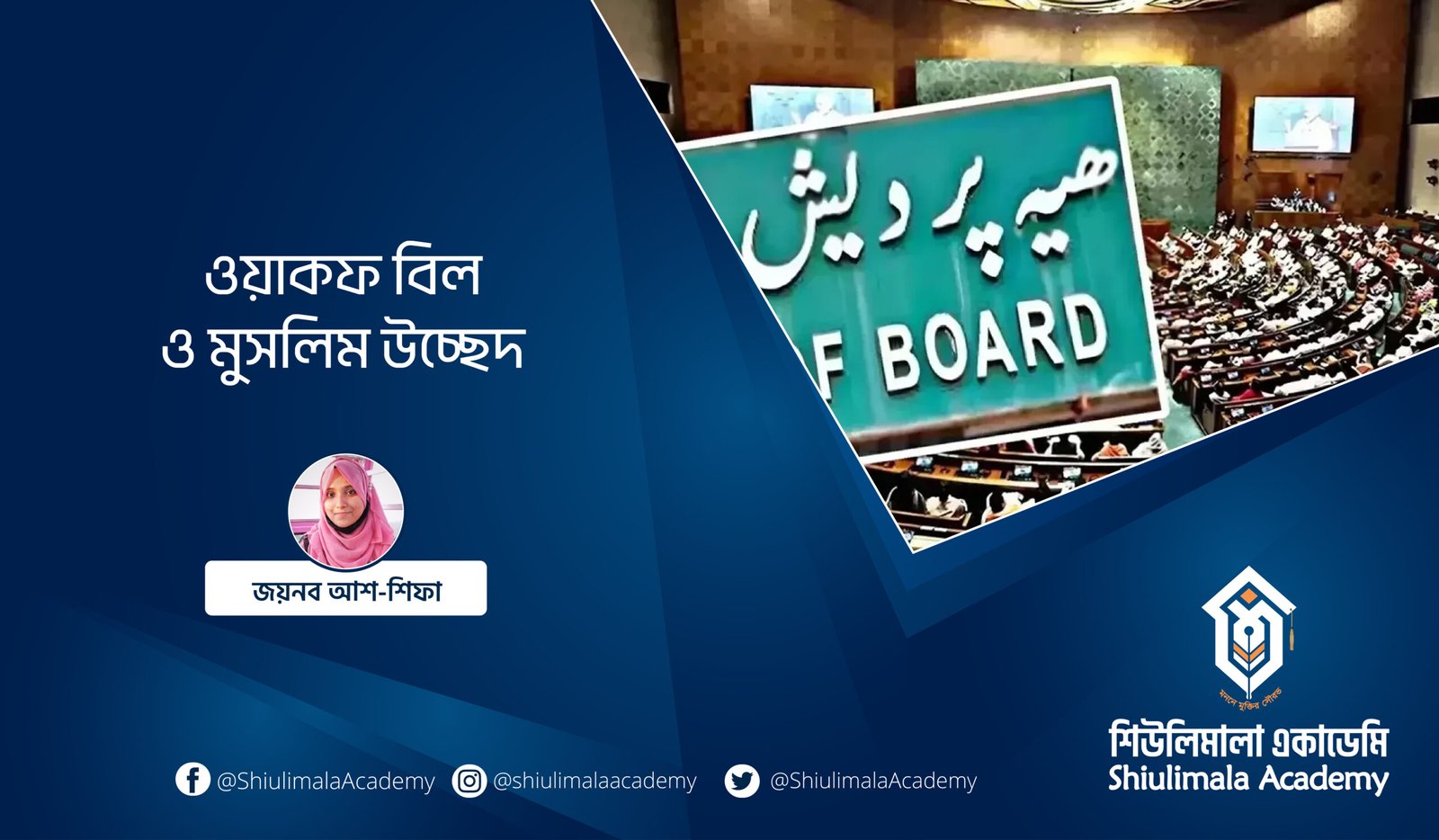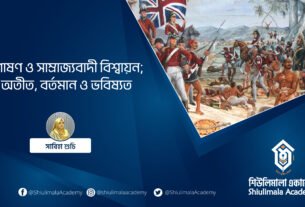জমি বা ভূখন্ডের কিছু অংশ, শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নয়; বরং এটি একটি জাতির আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অস্তিত্বের প্রতীক। ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, যে জাতি তার ভূমির উপর অধিকার হারায়, সে জাতি ধীরে ধীরে তার আত্মপরিচয়, স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ হারায়। জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেবল ফসল ফলানোর বা বাসস্থানের বিষয় নয়, এটি একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, নাগরিকের অধিকার এবং সমাজের শৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দু।
যেকোনো শাসকগোষ্ঠী যখন একটি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, প্রথম যে জিনিসটির ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে তা হলো—ভূমি। কারণ, ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ মানেই অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, জনগণের চলাফেরা ও বসবাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ, এমনকি মানুষের ধর্মীয় চর্চা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণও। জমি কে কীভাবে ব্যবহার করতে পারবে, কাদের মালিকানা থাকবে, কারা কর আদায় করবে—এসব নির্ধারণ করে সেই অঞ্চলের শাসন কাঠামো।
এই কারণে ভূমি আইন কোনো সাধারণ আইন নয়, এটি একটি গভীর রাজনৈতিক হাতিয়ার। এই আইনকে ব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী চাষিকে নিঃস্ব করতে পারে, একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান দখল করতে পারে, অথবা একটি গোটা জনগোষ্ঠীকে তাদেরই পূর্বপুরুষের ভূমি থেকে উৎখাত করতে পারে। ভূমির মালিকানা কার হাতে থাকবে, সেটিই নির্ধারণ করে কে আসল ক্ষমতার অধিকারী।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রিটিশরা উপমহাদেশে জমির আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে কেবল অর্থনৈতিক লুণ্ঠনই করেনি, বরং দীর্ঘমেয়াদে একটি দারিদ্র্যপীড়িত, বিভক্ত এবং নির্ভরশীল সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করেছে। একইভাবে, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি ভূমি আইন, কিংবা ভারতীয় ওয়াকফ বিল—সবই ভূমি দখলের মধ্য দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে ধ্বংস করার আধুনিক পন্থা।
অতএব, জমি মানে শুধু জমি নয়—জমি মানে নিয়ন্ত্রণ, জমি মানে আধিপত্য, জমি মানে শাসন, এবং শেষপর্যন্ত জমি মানেই ক্ষমতা।
ভূমি আইন কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ভূমি আইন (Land Law) হলো সেই আইনি কাঠামো যা নির্ধারণ করে একটি ভূখণ্ড বা অঞ্চলের জমি কার মালিক হবে, কে সেই জমি ব্যবহার করতে পারবে, কিভাবে ব্যবহার করতে পারবে, এবং সেই জমির উপর সরকারের বা ব্যক্তির কতটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এটি কোনো একটি নির্দিষ্ট জমির ব্যবহারবিধি নয় বরং একটি সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রশাসনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক উপাদান।
সহজভাবে বললে, ভূমি আইন বলে দেয়—
কে জমির মালিক,
কিভাবে মালিকানা স্থানান্তরিত হবে (উত্তরাধিকার, দান, বিক্রি),
জমি থেকে কর কীভাবে ও কতটা আদায় হবে,
ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জমির সীমারেখা কোথায়,
জমি নিয়ে বিরোধ হলে কীভাবে তার নিষ্পত্তি হবে,
সরকার বা রাষ্ট্র জরুরি প্রয়োজনে কিভাবে জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে,
এবং সমাজে জমি সংক্রান্ত ন্যায্যতা ও নিরাপত্তা কতটুকু বজায় থাকবে।
ভূমি আইন শুধু জমির উপরে নিয়ন্ত্রণের বিষয় নয়, এটি একটি অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মানদণ্ড। যে সমাজে ভূমি আইনের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা হয়, সেখানে স্থিতিশীলতা, সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা যায়। বিপরীতে, যে সমাজে ভূমি আইন হয় শাসকগোষ্ঠীর সুবিধা অনুযায়ী বা জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, সেখানে বৈষম্য, সহিংসতা ও নিঃস্বতার উদ্ভব ঘটে।
ভূমি আইনের গুরুত্ব এই কারণে অত্যন্ত বেশি—
অর্থনৈতিক দিক থেকে: কৃষিকাজ, শিল্প, বসতবাড়ি, অবকাঠামো—সব কিছুর ভিত্তি জমি। জমির উপর নিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ, ভূমি আইন প্রকারান্তরে একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে।
সামাজিক দিক থেকে: জমির মালিকানা, বণ্টন ও উত্তরাধিকার সমাজে শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন বা সমতা সৃষ্টি করতে পারে। ভূমি আইন যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তাহলে তা নারী, সংখ্যালঘু বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে।
রাজনৈতিক দিক থেকে: যে শাসক ভূমি আইনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে কার্যত জনগণের জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। জমির মালিকানা কে পাবে, তার সিদ্ধান্ত শাসকের ক্ষমতার সীমানা নির্ধারণ করে। এ কারণেই দখলদার শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই ভূমি আইন বদলে ফেলে—যেমনটি করেছে ব্রিটিশরা ভারতে, ইসরায়েল করেছে ফিলিস্তিনে, আর বর্তমানে ভারত করছে ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রেও।
এছাড়াও, ভূমি আইন মানুষের পরিচয়, বাসস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, ধর্মীয় অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার সাথে গভীরভাবে জড়িত। যে জমিতে মানুষের পূর্বপুরুষ শুয়ে আছে, যেখানে তার শিকড়, সেই জমি কেড়ে নেওয়া মানে শুধুই বাড়ি হারানো নয়—এটা তার অস্তিত্বের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া।
অতএব, ভূমি আইন কেবল একটি আইনি দলিল নয়—এটি একটি সমাজের চরিত্র, ক্ষমতার কাঠামো এবং ভবিষ্যতের নির্দেশক। এই কারণে এটি শাসক ও জনগণ উভয়ের জন্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়।
ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ ভূমি আইন ও তার ভয়াবহ প্রভাব
ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশদের শাসন কেবল রাজনৈতিক উপনিবেশ ছিল না; এটি ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্ব প্রতিষ্ঠার এক সুপরিকল্পিত প্রকল্প। এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিল ভূমি আইন। ব্রিটিশরা বুঝেছিল, একটি অঞ্চলের জনগণের জীবনের সঙ্গে জমির সম্পর্ক যত গভীর, সেই জমির উপর দখল স্থাপন করলেই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সবচেয়ে কার্যকরভাবে। ফলস্বরূপ, তারা একের পর এক ভূমি সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করে যার প্রতিটি ছিল উপমহাদেশীয় সমাজের ভিত্তিকে ধ্বংস করার হাতিয়ার।
১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)
ব্রিটিশরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মতো কৃষিনির্ভর অঞ্চলে এই ব্যবস্থা চালু করে। আগে যেখানে কৃষকই ছিল জমির প্রকৃত মালিক ও ভোগকারী, সেখানে এই ব্যবস্থায় জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় সরকারের অনুগত জমিদারদের কাছে। জমিদারের কাজ ছিল সরকারের জন্য চাষির কাছ থেকে নির্ধারিত কর আদায় করা, এবং তা ছিল নির্দয়ভাবে বাধ্যতামূলক। খরা, বন্যা, ফসলহানি—কোনো কিছুকেই কর মওকুফের কারণ হিসেবে গণ্য করা হতো না। কর দিতে ব্যর্থ হলে কৃষকের জমি নিলামে তুলে দেওয়া হতো।
এর ভয়াবহ পরিণতিতে ধীরে ধীরে একসময়ের সমৃদ্ধশালী অঞ্চলগুলোতে দেখা দেয় দারিদ্র্য, ঋণের জালে বন্দিত্ব, দুর্ভিক্ষ এবং কৃষক আত্মহত্যার মর্মান্তিক প্রবণতা। বাংলার মতো অঞ্চল, যা এক সময় বিশ্বের জিডিপির প্রায় ৮-১২% অবদান রাখত, তা হয়ে পড়ে দেউলিয়া, নিঃস্ব ও খাদ্য সংকটপীড়িত। এটি ছিল একটি অর্থনৈতিক গণহত্যা।
২. রায়তওয়ারি ব্যবস্থা
এই ব্যবস্থা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে চালু ছিল। এখানে জমির মালিকানা কাগজে-কলমে কৃষকের নামে থাকলেও আদায়যোগ্য কর নির্ধারিত হতো কৃষকের উৎপাদনের ওপর নয়, বরং সরকারের খরচ ও প্রয়োজন অনুযায়ী। অর্থাৎ, কৃষক যতই উৎপাদন করুক না কেন, তার হাতে থাকত না কোনো অর্থ বা খাদ্য—সবই চলে যেত কর হিসেবে সরকারের কাছে। এমন ব্যবস্থায় কৃষক ছিল তার নিজের জমিতেই এক প্রকার কর-দাস। এই ব্যবস্থাও ক্রমে কৃষকদেরকে নিঃস্ব করে তোলে এবং চিরন্তন ঋণের ফাঁদে ফেলে দেয়।
৩. মহালওয়ারি ব্যবস্থা ও ধর্মভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন
উত্তর ও মধ্য ভারতে চালু ছিল মহালওয়ারি ব্যবস্থা, যেখানে কর আরোপ হতো পুরো গ্রামের সম্মিলিত মালিকানার ভিত্তিতে। এতে একদিকে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা বিলুপ্ত হয়, অন্যদিকে কর প্রদানে গাফিলতির কারণে চাষিদের মধ্যে দোষারোপ ও বিবাদ বাড়ে। একই গ্রামের মানুষ একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়।
অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন সমাজে গভীর বিভাজন সৃষ্টি করে। হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক উত্তরাধিকার আইন চালু করায় সমাজে বিভ্রান্তি এবং বিদ্বেষ ছড়ায়। বিশেষত নারীরা এই আইনের মারপ্যাঁচে সবচেয়ে বেশি অধিকার বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সম্পত্তির কোনো অংশই পায় না।
এই আইনগুলো একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ ছিল, যার লক্ষ্য ছিল সমাজের ঐক্য ভাঙা, কৃষকদের জমিহীন করা, এবং সম্পদের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমে একদিকে কৃষকের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে তাদেরকে দুর্বল ও নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে।
এই ভূমি আইনগুলোর ফলাফলস্বরূপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা একটি কৃষিপ্রধান, সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার ভীত কেঁপে ওঠে। উপমহাদেশের জনগণ পরিণত হয় কর-দাসে, নিঃস্ব চাষিতে, বিভক্ত সমাজে—যার অভিঘাত আজও টিকে আছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাধ্যমে।
ফিলিস্তিনে ভূমি দখলের কৌশল: আইনকে অস্ত্র বানানোর নীরব যুদ্ধ
ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত শুধুই একটি ভূখণ্ডগত বিরোধ নয়, এটি একদিকে জাতিগত নির্মূলকরণ (ethnic cleansing), অন্যদিকে এক নির্মম আইনি যুদ্ধের দৃশ্যপট। ইসরায়েল শুরু থেকেই বুঝে নিয়েছে—একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে প্রথমেই তাকে ভূমিহীন করে দিতে হবে। আর এই ভূমি দখলের প্রক্রিয়াটি তারা শুধু অস্ত্রের জোরে নয়, বরং সুপরিকল্পিত আইনি কাঠামোর মধ্য দিয়ে, আন্তর্জাতিক নীতিমালার ফাঁকফোকর ব্যবহার করে সম্পন্ন করছে। একে বলা যায়, “আইনকে অস্ত্র বানিয়ে দখলদারিত্ব”।
১. Absentee Property Law (1950)
১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় প্রায় আট লক্ষ ফিলিস্তিনি নিজ ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইসরায়েল “Absentee Property Law” প্রণয়ন করে, যার আওতায় বলা হয়—যেসব ফিলিস্তিনি ১৯৪۷ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে গিয়েছে বা গমন করেছে শত্রু রাষ্ট্রে, তাদের সম্পত্তি তারা আর ফেরত পাবে না। তাদের ঘোষণা করা হয় “অনুপস্থিত মালিক” এবং সেই জমি ও স্থাপনা রাষ্ট্রীয় মালিকানা বলে ঘোষণা করা হয়।
এই একটি আইনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজভূমিতে পরবাসী বানানো হয়। আজও বহু ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে বসে রয়েছে, যাদের পূর্বপুরুষের জমি এখন ইসরায়েলি বসতিতে পরিণত হয়েছে।
২. সামরিক আদেশ (Military Orders) – পশ্চিম তীর ও গাজায় ভূমি বাজেয়াপ্ত
১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে পশ্চিম তীর ও গাজা দখলের পর, ইসরায়েল সেখানে একের পর এক সামরিক আদেশ জারি করে। এই আদেশগুলো আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকেও ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনি জমি বাজেয়াপ্ত করার লাইসেন্স দেয়। জমি অনেক সময় “সামরিক প্রয়োজন” দেখিয়ে নেওয়া হয়, আবার কোনো প্রকার নোটিশ ছাড়াই “সরকারি জমি” হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
ফলস্বরূপ, ফিলিস্তিনি কৃষক তাদের শতাব্দীপ্রাচীন জমির মালিকানার কোনো সুনির্দিষ্ট কাগজ দেখাতে না পারার কারণে সে জমি হারায়। তারপর সেই জমিতে বসতি গড়ে তোলে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা, যা আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ হলেও ইসরায়েল নিজস্ব আইনের ছত্রছায়ায় তা বৈধ করে তোলে।
৩. Land Registration Freeze – মালিকানার প্রমাণ রুদ্ধ করা
ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম তীরে ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। এতে করে বহু ফিলিস্তিনি তাদের পৈতৃক সম্পত্তির যথাযথ মালিকানার কাগজ তৈরি করতে পারেনি। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ পরে সেই জমিগুলোকে “কোনো মালিকানাহীন জমি” হিসেবে ঘোষণা করে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়।
এই পলিসি এমনভাবে গঠিত যেখানে, ফিলিস্তিনিরা আইনি পথে নিজের জমির প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়, আর সেটিকে ব্যবহার করে দখলের যুক্তি দাঁড় করায় ইসরায়েল।
৪. Zoning and Planning – নির্মাণের অধিকার কেড়ে নেওয়া
ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোকে বিভিন্ন জোনে বিভক্ত করে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি নির্মাণ বা সংস্কার কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শত শত আবেদন জমা পড়লেও, তাদের বেশিরভাগই বাতিল হয়। অপরদিকে, ইহুদি বসতির জন্য অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুতই অনুমোদিত হয়।
নির্মাণ অনুমোদন ছাড়া ঘর তৈরি করলে সেটিকে “অবৈধ” ঘোষণা দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি বহু স্কুল, হাসপাতাল, পানির কুয়া পর্যন্ত ধ্বংস করে দেওয়া হয় “অবৈধ স্থাপনা” নাম দিয়ে।
৫. সেফরোনিক উপায়: “Legal Annexation”
সম্প্রতি ইসরায়েল এমন কিছু আইন প্রণয়ন করেছে, যার মাধ্যমে পূর্ব জেরুজালেমসহ অনেক অঞ্চলকে “আইনি উপায়ে” ইসরায়েলের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। যদিও আন্তর্জাতিক মহল এই আইনগুলোকে অগ্রহণযোগ্য ও অবৈধ বলছে, তবুও ইসরায়েল তার প্রশাসনিক কাঠামো, পুলিশি শক্তি, শিক্ষা ব্যবস্থা, এমনকি ভাষা ব্যবস্থাও সেখানে চালু করছে—যা একটি স্পষ্ট দখলের ছাপ বহন করে।
৬. গণউচ্ছেদ ও বর্ণবাদী দেয়াল (Separation Wall)
ইসরায়েল একটি দৈত্যাকার দেয়াল নির্মাণ করেছে, যাকে তারা নিরাপত্তা দেওয়াল বললেও আসলে এটি বহু ফিলিস্তিনিকে নিজেদের ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অনেক সময় দেয়াল এমনভাবে কাটা হয়, যাতে ফিলিস্তিনিদের জলাধার, খামার, রাস্তাঘাট—সব কিছুই ইসরায়েলি অংশে পড়ে, আর তারা নিজের ভূমিতে যেতে হলে ঘুরে যেতে হয় বহু কিলোমিটার।
এই দেয়ালের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা হয়ে পড়েছে গৃহবন্দী, এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।
ইসরায়েলের ভূমি দখলের কৌশল কোনো হঠাৎ করে নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রকল্প, যেখানে আন্তর্জাতিক আইন, সামরিক শক্তি ও প্রশাসনিক কৌশল একত্রিত করে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রয়াস চলছে। যুদ্ধের মাঠে ট্যাংক ও গুলি যতটা ভয়ংকর, ভূমি আইন ও কাগজপত্রের মারপ্যাঁচ কখনও কখনও তার চেয়েও ভয়াবহ।
একটি জাতিকে নিঃস্ব করতে হলে তাকে অস্ত্র নয়—জমিহীন করলেই যথেষ্ট। আর ফিলিস্তিনে ঠিক সেটিই হচ্ছে—একটি জনগোষ্ঠীকে তার ইতিহাস, ভিটেমাটি, আত্মপরিচয় থেকে বঞ্চিত করে নির্মিত হচ্ছে এক জাতিগত নিধনের আধুনিক রূপ।
ওয়াকফ আইন কী?
আরবি ভাষায় ‘ওয়াকাফা’ শব্দটি থেকে এসেছে ‘ওয়াকফ’ – যার অর্থ হল সম্পত্তির হাতবদল। ভারতে যখন কোনও ব্যক্তি মুসলিম আইনের আওতায় ধর্মীয় বা দাতব্য কারণে তার সম্পত্তি দান করেন, তখন সেটাকেই বলে ওয়াকফ সম্পত্তি। এর মধ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, আশ্রয়কেন্দ্র বা শুধু জমি – সব কিছুই থাকতে পারে।
যে কাজের জন্য সেটি দান করা হয়েছে, সেটি ছাড়া অন্য কোনও কাজে ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহার করা যায় না, এবং এটি কাউকে বিক্রি বা হাতবদলও করা যায় না।
ওয়াকফে দান করা সম্পদ নির্দিষ্ট ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়, যাকে ওয়াকফ বোর্ড বলা হয়। যাঁরা সম্পত্তি দান করেন তাদের ওয়াকিফ বলা হয়। তথ্য বলছে, সবচেয়ে প্রাচীনতম ওয়াকফিয়ার নজির মেলে ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। সম্ভাব্য প্রাচীনতম পুরনো ওয়াকফিয়া প্যারিসের লুভের জাদুঘর দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে এর লিখিত কোনও তারিখ পাওয়া যায়নি। অনেক ইতিহাসবিদ এটিকে নবম শতকের মাঝামাঝি বলে মনে করেন।
ভারতের ইতিহাসে ওয়াকফের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দিল্লির সুলতানশাহির প্রথম দিকে। জামা মসজিদ কর্তৃপক্ষকে দু’টি গ্রাম উৎসর্গ করেছিলেন সুলতান মুইজুদ্দিন সাম ঘোর মুলতান। ওয়াকফ হিসেবে ওই গ্রাম দু’টি মসজিদের তৎকালীন প্রশাসন শাইখুল ইসলামের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটিই ভারতের প্রথম ওয়াকফ বলে মনে করা হয়।
ওয়াকফ মুসলমানদের দীন সুরক্ষা ও মানবসেবার এক চমৎকার ব্যবস্থাপনা, যা অন্য ধর্ম বা মতাদর্শীদের কাছে নেই। ওয়াকফ বলা হয় জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো মুসলমান তার ব্যক্তিগত স্থাবর অস্থাবর সম্পদ দান করে দেওয়া।
সম্পদকে ওয়াকফ করে দেওয়ার মাধ্যমে সেই সম্পদে ওয়াকফকারীর মালিকানা চিরতরে রহিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে কোনো সময় তার বংশধর তার ওপর মালিকানা দাবি করতে পারে না। এটা আল্লাহর মালিকানায় চলে যায়। ওয়াকফ সম্পদ একজন মোতাওয়াল্লি দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
সম্পদ ওয়াকফ করার ধারাবাহিকতা নবীজির যুগ থেকেই শুরু হয়। সর্বপ্রথম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী এবং মসজিদে কোবা ওয়াকফ করে দেন। আনসারি সাহাবিরা মুহাজির সাহাবিদের জন্য তাদের জমি খেজুর বাগান ইত্যাদিকে ওয়াকফ করেছিলেন। প্রিয় রাসুলের যুগে সাহাবায়ে কেরাম মদিনার বিভিন্ন কূপ কিনে সবার জন্য ওয়াকফ করেছেন এমন ইতিহাস পাওয়া যায়।
মুসলিম শাসনামলে ওয়াকফ বিস্তৃতি লাভ করে। ওয়াকফ সম্পদেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে মসজিদ ও দীনি প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে। আব্বাসি শাসনামলে ইমামদের যুগে ফিকহ রচিত হয়। এবং ওয়াকফসংক্রান্ত নীতিমালাগুলো লিপিবদ্ধ হয়।
আমরা দেখতে পাই ইসলামি শাসনামলে মসজিদ মাদরাসা দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াকফ সম্পত্তি দ্বারাই পরিচালিত হতো। এসব পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ওয়াকফ করা ছিল। মুসলমানদের সভ্যতা বিনির্মাণে দীন সংরক্ষণে ওয়াকফকৃত সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
রাষ্ট্র পরিচালনায় খলিফাদের বড় একটি শক্তি ছিল ওয়াকফের সম্পদ। ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে সামাজিক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা করা হতো। বিভিন্ন সরাইখানা রাবাত গড়ে উঠেছিল ওয়াকফের ওপর ভিত্তি করে। হাসপাতাল থেকে জনগণকে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হতো। রাবাত এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিধবা বৃদ্ধা অসহায় নারীদের আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। তাদের সকল খরচ ওয়াকফ আয় থেকে বহন করা হতো।
মুসলিম শাসনামলে ওয়াকফ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, এর ব্যবস্থাপনা মুসলিম উম্মাহর অনেক শ্রেষ্ঠ সন্তান ওয়াকফের জমিতে জন্ম নিয়েছে, ওয়াকফের ব্যবস্থাপনায় লেখাপড়া করেছে, ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছে। বৃদ্ধ বয়সে ওয়াকফ থেকে ভাতা পেয়েছে, মৃত্যুর পর ওয়াকফের জমিতেই তাদের কবর হয়েছে।
ইসলামি খেলাফত ধ্বংসের পর মুসলমানদের ওয়াকফের বিপুল পরিমাণ সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়। ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর আজ মসজিদ মাদরাসা ইমাম শিক্ষক শিক্ষার্থী অসহায় সামাজিকভাবে দুর্বল দরিদ্র শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। আজ মসজিদ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সমাজের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে হয়। অথচ সোনালি যুগে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুল পরিমাণ নিজস্ব আয় ছিল এবং এগুলো পরনির্ভরশীল ছিল না।
আমাদের উপমহাদেশে দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে ওয়াকফের বিস্তৃতি ঘটে। অসংখ্য মসজিদ মাদরাসা মাজার কবরস্থান এবং মুসলিম নিদর্শন স্থাপনা গড়ে ওঠে ওয়াকফের সম্পদে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিরা জনকল্যাণে এবং দীনি প্রতিষ্ঠানে তাদের সম্পদ দান করেন।
মুসলিম সুলতানদের পতনের পর দীর্ঘ ব্রিটিশ ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের শিকার হয় মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পদ। তারা বিভিন্ন আইন তৈরি করে বিভিন্ন অজুহাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদকে জাতীয়করণ করে।
ব্রিটিশদের বিদায়ের পর হিন্দুত্ববাদী ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা নানাভাবে আক্রান্ত এবং নির্যাতিত। মুসলমানদের ওয়াকফকৃত সম্পদে রাষ্ট্রীয় অন্যায় হস্তক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে চলছে। বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের হাতছাড়া।
সর্বশেষ ২০২৪ নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ওয়াকফ কৃত সম্পত্তির মালিকানা মুসলমানদের থেকে কেড়ে নেওয়ার সর্বশেষ আয়োজন সম্পন্ন হচ্ছে। এ নতুন সংশোধনীতে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জানা প্রয়োজন ওয়াকফ আইন নিয়ে ভারতে কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে I
স্বাধীনতার পর ভারতে প্রথম ১৯৫৪ সালে সংসদে ওয়াকফ বিল পাস হয়। এরপর ১৯৯৫ সালে সেই বিলে সংশোধন করা হয়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ছয় লাখের বেশি ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় আট লাখ একর জমির সমান। এর মধ্যে বহু মসজিদ, মাদরাসা, কবরস্থান ও ইসলামি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
ভারতের ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, ২০২৫ ও ভূমি দখলের আধুনিক নীতি
ভারতের ওয়াকফ (Amendment) Act, 2025 শুধু একটি আইন নয়—এটি ভূমি ও সম্পত্তি জুড়ে শাসনযন্ত্রের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যান্ত্রিক পরিকল্পনা। এটি পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, নিবন্ধন এবং আবেদন নিষ্পত্তিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রবলভাবে বৃদ্ধি করেছে—যা মুসলিম সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রিত ওয়াকফ সম্পত্তিগুলিকে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পথ সুগম করে।
১. রেজিস্ট্রেশন এবং ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ
আইনটি ৬ মাসের মধ্যে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি ডিজিটালভাবে নিবন্ধন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে, যদিও ইতিহাসজুড়ে (বিশেষত ওয়াকফ-বাই-ইউজার) অনেক সম্পত্তি লিখিত দলিল ছাড়া ছিল।
ফলে, যেসব সম্পত্তির অফিসিয়াল ডকুমেন্ট নেই, সেইগুলিকে “অবৈধ” বা “সরকারি” বলে চিহ্নিত করার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।
২. “ওয়াকফ‑by‑user” বিধান বাতিল
দীর্ঘকাল ধর্মীয় বা দানবাবে ব্যবহৃত হলেও দস্তাবেজবিহীন সম্পত্তিগুলিকে ‘waqf-by-user’ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অক্ষম করা হয়েছে ।
এর ফলে, প্রাচীন মসজিদ, কবরস্থান, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রথাগতভাবে দান করা হলেও, অনেকই আইনি স্বীকৃতি হারাতে পারে।
৩. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় প্রশাসনে
জেলা কালেক্টর ও কেন্দ্রীয় অপারেটিভদেরকে ওয়াকফ সম্পত্তির জরিপ, নিরীক্ষা ও পেশার জন্য নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ।
এছাড়া, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত আপিল প্রক্রিয়া নির্ধারিত হলেও, সরকারী আধিকারিকদের শক্তি বাড়ছে—ফলে স্থানীয় বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন ক্ষুন্ন হচ্ছে।
৪. বোর্ডে নানা সম্প্রদায় ও বেসরকারি নিয়োগ
ওয়াকফ বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে গঠনমূলক হিন্দু, শিয়া, বোহরা, আগাখানি প্রতিনিধি এবং অন-Muslim বিশেষজ্ঞ, যদিও সমালোচকরা বলছেন এটি ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে ।
৫. সীমাবদ্ধতা: আইন ও সংস্কার সাধনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব
সরকার বলছে যে, এই আইন যোগাযোগ, স্বচ্ছতা, নারী প্রতিনিধিত্ব, এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে—যেমন ঋণমুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মাইক্রো–ফাইন্যান্স, হাউজিং। কিন্তু সমালোচকরা এটিকে বিভাজন ও ক্ষয়ক্ষতির হাতিয়ার হিসেবেই দেখেন ।
ভূমির নতুন আদলে মালিকানা হরণ
প্রায় ৮৭২,০০০টিরও বেশি ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে প্রায় ৫৯ হাজার সম্পত্তি অনধিকারভুক্ত এবং ৪৩৬,০০০-এরও বেশি সম্পত্তির অধিকার স্পষ্ট নয়।
আইন অনুযায়ী Limitations Act, 1963 কার্যকর হওয়ায় ধারাবাহিক অবৈধ দখল লিগিটিমেট হতে পারে—এতে দীর্ঘদিন দখলকৃত সম্পত্তি নিয়ে ওয়াকফ বোর্ড আপত্তি করতে পারবে না ।
কিন্তু সমালোচক দেখছেন –
“Bill aims to seize historic religious properties lacking formal documentation… could be used to confiscate historic mosques”।
একাধিক শিখ, AIMPLB, রাজনৈতিক দলসমূহ ও মুসলিম সংগঠন আইনটি সংবিধানবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষতার নিন্দনীয় ভঙ্গকারী বলে অভিহিত করেছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে—মুর্শিদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, কোঝিকোড, কট্টর—জোরালো প্রতিবাদ হয়েছে; এর ফলে পুলিশের হস্তক্ষেপ, গ্রেফতার ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স মোতায়েনের প্রয়োজন হয়েছে।
সর্বোচ্চ আদালতে একাধিক মামলা চলমান, যেখানে তদন্ত চলছে—এই আইন কি ধর্মীয় সংস্থা চলাচলের স্বাধীনতা সংবিধান লঙ্ঘন করছে না? সরকার আপত্তি করে বলছে যতক্ষণ স্থগিতাদেশ নেই, ততক্ষণ সম্পত্তি স্বতঃসিদ্ধভাবে বহাল থাকবে ।
তবে আদালত ইতিমধ্যে জানিয়েছে—৪ এপ্রিল ২০২৫ থেকে কোনো সম্পত্তি ডিনোটিফাই বা বদল করা যাবে না, যতক্ষণ না মামলা নিষ্পত্তি হয়।
ভারতের ওয়াকফ (Amendment) Act, 2025 প্রকৃতপক্ষে ভূমি আইনকে আধুনিক দখলের অস্ত্রে রূপান্তরিত করার ক্রিয়া। যেমন ব্রিটিশ বা ইসরায়েল ভূমি আইনগুলো ব্যবহার করে সম্পত্তি দখল করেছিল—ঠিক তেমনিভাবে এই আইনও ডকুমেন্টেশন ও নিবন্ধনের ছক প্রয়োগ করে হাজার হাজার বছরের মুসলিম ওয়াকফ ও সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় অধিকার আরোপ করছে।
এটি একটি আইনি–অপরাধ, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক টুল হিসেবে কাজ করছে, যেখানে অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি বহু মুসলিম ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা আমলাতান্ত্রিক বোর্ডের হাতে চলে যেতে পারে।
ফলশ্রুতি একটা গোষ্ঠীর সম্পত্তি, ইতিহাস, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রাজনৈতিক ও শাসনীয় ‘আইনি’ কাঠামোর ফলে আজ হুমকির মুখে।
এই আইনের পেছনে বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যগুলো হলো:
১. ‘এক জাতি, এক আইন’ (Uniform Civil Code) চাপিয়ে দেওয়া।
বিজেপি সরকারের বহুদিনের এজেন্ডা হলো “One Nation, One Law”। এটি মুসলিম পারিবারিক আইনসহ ধর্মীয় বৈচিত্র্য ধ্বংসের একটি পদক্ষেপ।
২. মুসলিমদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করা।
ওয়াক্ফ সম্পত্তি শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়, মুসলিমদের শিক্ষা, সমাজসেবা, স্বাস্থ্যসেবাসব বিভিন্নরকম দাতব্য কাজেও ব্যবহৃত হয়। এই সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলে অসংখ্য সামাজিক দাতব্য সেবা সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবে।
৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব মুছে ফেলা।
সেবা সংস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদরাসা, কবরস্থান ইত্যাদি সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাস, স্থাপত্য এবং সংস্কৃতি ধ্বংস করার সুযোগ তৈরি হবে। এর মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে মুসলিমদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে মুছে ফেলা যাবে।
৪. ওয়াক্ফ জমি নিজ দলের লুটেরার হাতে তুলে দেওয়া।
যেসব জমির ওয়াকফ করার ডকুমেন্টস না পাওয়া যাবে, তা সরকার ‘খাস জমি’ হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে।
ওয়াক্ফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ শুধু একটি আইন নয়, এটি মুসলিমদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত অস্তিত্ব ধ্বংসের একটি কাঠামোগত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত ও দূরদর্শী হতে হবে।
নতজানু নীতি এই অবস্থা থেকে এই জাতিকে কোনো মুক্তি এনে দেবে না। আজকের পৃথিবীর আন্তর্জাতিক আইন তাদের গণতন্ত্রের বুলি তাদের মানবাধিকার এগুলো মুসলমানদের জন্য না। এটা আমরা ফিলিস্তিনে দেখেছি ইরাকে দেখেছি আফগানিস্তানে দেখেছি। তাদের আইন আদালত মুসলমানদের মুসলমানদের সম্পদের সুরক্ষা দিবে না। ভারতের বাবরি মসজিদ তার চাক্ষুষ প্রমাণ।