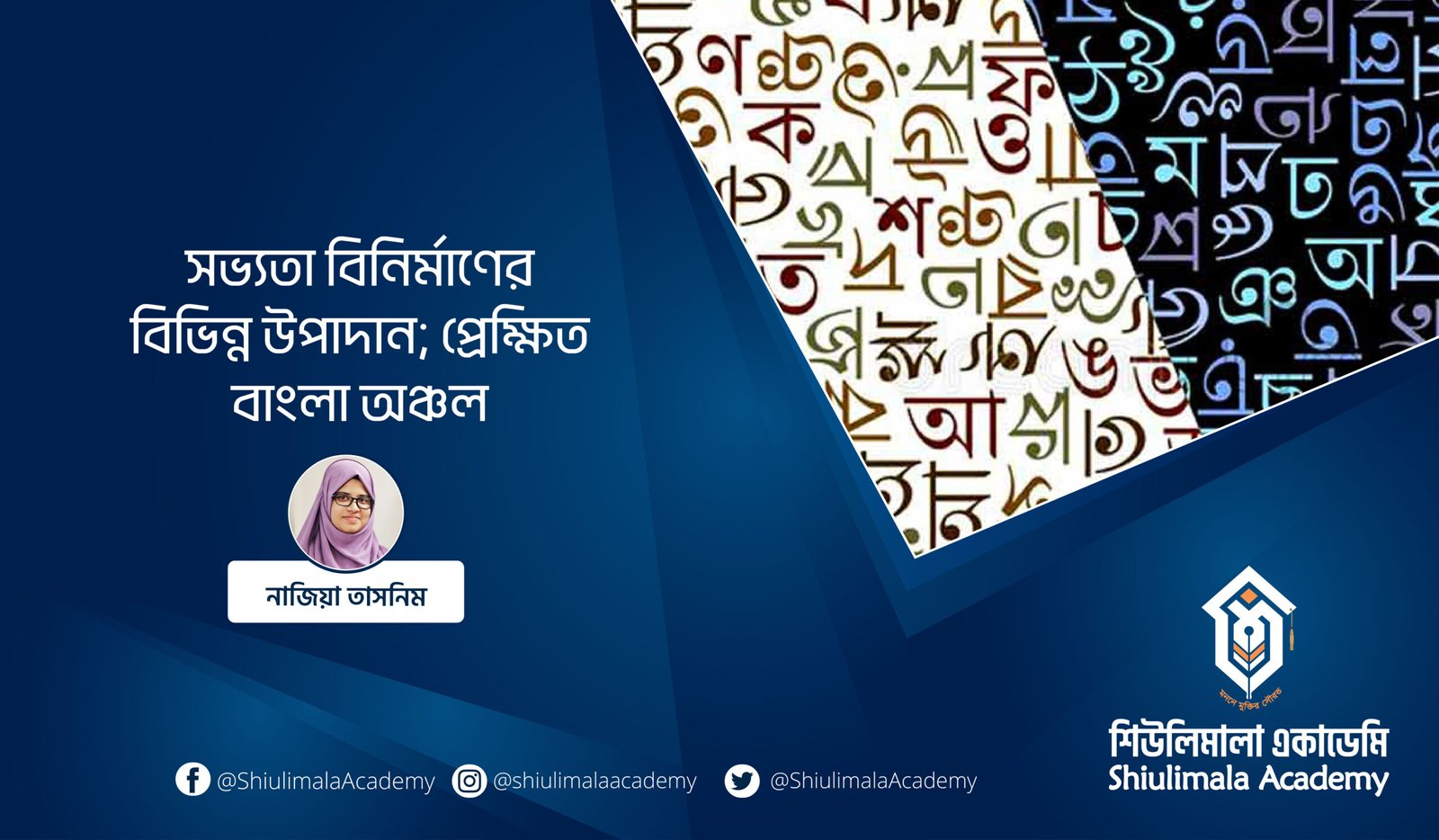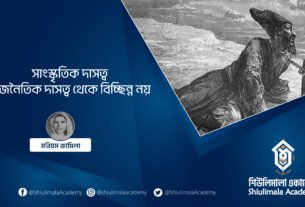সভ্যতা এমন একটি মৌলিক পরিভাষা, যা মানুষের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সভ্যতা কোনো ক্ষণস্থায়ী বা সাম্প্রতিককালের বিষয় নয় যে, আমরা শুধু আজকের দিনে এসে তা নিয়ে আলোচনা করছি। বরং, সভ্যতা মানুষের অগ্রযাত্রা, মানবজীবনের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিকশিত একটি ধারণা। আধুনিক সময়ের সবচেয়ে বড় সভ্যতা-বিশারদ মালিক বিন নবির ভাষায়—“মানুষ সংক্রান্ত যেকোন আলোচনাই আমাদের সভ্যতার দিকে ধাবিত করে।”
মানবতার ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি— প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর জীবনের সংগ্রাম, অগ্রযাত্রা ও মিশনের মধ্য দিয়েই সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাঁর সংগ্রামী জীবনের ভিশনও ছিল মানুষের জন্য একটি সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ একটি সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করা। এরপর ইতিহাসের ক্রমধারায় বিভিন্ন সময়ে আমরা অসংখ্য সভ্যতার উত্থান-পতন লক্ষ্য করি; গ্রিক সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা, আবার নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আগত ইসলামী সভ্যতা। অর্থাৎ, সভ্যতা সব সময়ই বিদ্যমান ছিল এবং মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সভ্যতার প্রয়োজন ছিল, আছে এবং থাকবে।
পশু-পাখিদের কোনো সভ্যতার প্রয়োজন হয় না, কারণ তারা কিছু নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে জীবনের চক্র শেষ করে ফেলে। কিন্তু মানুষ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, সবই মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত। মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক বিশেষ সৃষ্টি; মানুষের যোগ্যতা, সক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্য অন্য সব প্রাণীর চেয়ে আলাদা। একইসাথে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল একটি সৃষ্টি—যে মানুষ জন্মের পর নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। সেই মানুষই আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সবচেয়ে শক্তিশালী সৃষ্টিও। কেননা, মানুষের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতা আছে, যা অন্য কোন প্রাণীর নেই। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী, আবার একই সাথে আবেগ, অনুভূতি এবং বিবেকসম্পন্ন প্রাণী। মানুষ একে অন্যের সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে। মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তাই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য শুধু জৈবিক চাহিদাগুলোই যথেষ্ট নয়; তার প্রয়োজন পরিবেশ, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের যথাযথ ভিত্তি। মানুষ কখনো একা বেঁচে থাকতে পারেনা। অত্যন্ত নাজুক এবং দুর্বল একটি শিশু থেকে সামর্থ্যবান একজন মানুষে পরিণত হওয়া পর্যন্ত জীবনের যে গতিপথ, এ যাত্রাপথে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষকে পারিপার্শ্বিক অনেক মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে অনেক ধরণের সম্পর্কে মানুষকে জড়াতে হয়। আর সম্পর্কগুলো চালিয়ে নিতে বিভিন্ন ধরণের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ তাকে মানতে হয়। এই সমস্ত কারণে মানুষ সব সময়ই সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে। ইবনে মিশকারের ভাষায়, “মানুষ একত্রিত হওয়ার বিষয়টা তাদের পারস্পরিক সংঘবদ্ধ করে একটা শক্তিশালী সমাজে রূপান্তরিত করে।” ইবনে সিনার মতে, “মানুষের প্রকৃতিগত ফিতরাত হল যে, তার পক্ষে একাকী বসবাস করা সম্ভব নয়।” বিখ্যাত আখলাকতত্ত্ববিদ আলী চেলেবি’র মতে, “মানুষ যদি একটা সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সমাজবদ্ধ হতে হবে। সমাজবদ্ধ হওয়া ছাড়া কখনো একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।” তার মতে, “সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে সমাজ, এমনকি সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতার মাধ্যমে একটা সভ্যতার উৎপত্তি হয়ে থাকে।” ইসমাইল রাজী আল ফারুকী এই চিন্তাকে আরও বিকশিত করে বলেন, “মানুষের একসাথে বসবাস করাটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় বা আবশ্যক। তাছাড়া মানুষের পক্ষে (একাকী) ব্যতিক্রমধারায় পরিচালিত হয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।” অর্থাৎ, তারা সবাই সমাজবদ্ধ জীবন বা সভ্যতার সূচনাকে মানুষের একটি ফেতরাতী চাহিদা হিসেবে তুলে ধরেছেন। যদিও পাশ্চাত্য এক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তা লালন করে। যেমন পশ্চিমা দার্শনিক দুর্খেইমের মতে, “মানুষ ফিতরাতগতভাবে নয়, বরং সময়ের প্রয়োজনে একজন আরেকজনকে অনুভব করা শুরু করেছে, পাশাপাশি একজন আরেকজনের প্রয়োজনীয়তা এটাও আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে বলে তারা একত্রে বসবাস শুরু করেছে।”
শিরোনামের দ্বিতীয় শব্দটি হলো বিনির্মাণ। বিনির্মাণও একটি মৌলিক ধারণা। এর আরবি পরিভাষা হলো ইমারত। এটি এতটাই মৌলিক একটি পরিভাষা, যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথেই সম্পর্কিত। কারণ মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে—এটি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলোর একটি। এই মৌলিক প্রশ্নের যেসব উত্তরের কথা কুরআনে উল্লেখ আছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ইমারাতুল আরদ, অর্থাৎ পৃথিবীকে বিনির্মাণের দায়িত্ব পালন। এই বিনির্মাণের ধারণা মানুষের প্রতিটি কাজ ও সমস্ত আয়োজনকে অর্থবহ করে তোলে। আমি কেন পড়াশোনা করছি, কেন চাকরি করছি, কেন একজন ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং নির্মাণ করে, কেন একজন স্থপতি নকশা করে, কেন একজন শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করে— সবকিছুকেই এই ইমারতের বা বিনির্মাণের ধারণাটি অর্থবহ করে তোলে। কারণ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে এই দায়িত্ব নিয়েই।
এখন দেখা যাক সভ্যতা বিনির্মাণের উপাদানগুলো কী কী? এক্ষেত্রে, বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। মালিক বিন নবির মতে, সভ্যতা তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:
- মানুষ
- মাটি
- সময়
এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষ। মানুষই সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। মানুষের জন্যই সভ্যতা, মানুষের মাধ্যমেই সভ্যতার উত্থান।
আজকের যে পাশ্চাত্য সভ্যতা, এর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এটি মানুষকে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে পরিধিতে স্থান দিয়েছে। একারণে এ সভ্যতা মানুষকে প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার সামগ্রিক পরিবেশ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সভ্যতা গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং তা কেবল তাদেরই সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করছে। এটি আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের যে মর্যাদা, তাকে প্রচণ্ডভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছে। একজন মানুষ যেদিন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সেদিন থেকেই সে সম্মানিত। এই পৃথিবীতে তার প্রতিটি মৌলিক অধিকার তার জন্মগত অধিকার। সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকাও তার অধিকার। সে যে পরিবার, ধর্ম, বর্ণ বা যে ভূমির সন্তানই হোক না কেন। অথচ আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা এই অধিকার ও সম্মানকে বিভাজিত করেছে। কারণ এই সভ্যতা নির্দিষ্ট স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সভ্যতা people-এর সংজ্ঞায় সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। ফলে এই সভ্যতা ঠিক সভ্যতা হয়ে উঠেনি। সভ্যতাকে যদি গাছের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলতে হয় আগাছা।
তারপর আসি সময় এবং স্থান। মূলত, সময় ও স্থান মানুষের সাথে সম্পর্কিত হয়ে সভ্যতা গঠন করে। যে সভ্যতাই হোক— গ্রিক, ভারতীয়, বৌদ্ধ কিংবা ইসলামী; প্রতিটি সভ্যতাই তার সময় ও ভৌগোলিক পরিসরে বসবাসকারী মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রতিটি সভ্যতা তার সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আজকের সভ্যতার সাথে অতীতের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা একটি সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। সে অর্থে, সভ্যতা হলো অতীত ও বর্তমানের মিলনবন্ধন। একইসাথে এটি মানুষের সাথে তার মাটি ও সময়ের মেলবন্ধন। একইসাথে সভ্যতা ভৌত বাস্তবতার পাশাপাশি মানুষের আধ্যাত্মিক ও মেটাফিজিক্যাল বিষয়গুলোকেও পরিগ্রহ করে থাকে।
এ কারণেই সভ্যতার আলাপ আদম (আ.)-এর সময় থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত অব্যাহত, এবং প্রতিটি যুগে সময় ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।
বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী স্কলার থিওম্যান দুরালি বলেছেন—“সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য দুটি স্তম্ভ প্রয়োজন: তার একটি হলো দ্বীন এবং অন্যটি হলো ভাষা। সভ্যতার যে উপাদানগুলো—মানুষ, মাটি, সময়—এগুলোকে একটি সুতায় বেঁধে দেয় মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও আদর্শ। এগুলো একটি সভ্যতার ভিশন নির্ধারণ করে। যেমন—
- গ্রিক সভ্যতা ছিল দেবতাকেন্দ্রিক।
- বৌদ্ধ সভ্যতা ছিল একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক ধ্যানধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।
- ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের মৌলিক স্পিরিটের ভিত্তিতে, যা আজও প্রাসঙ্গিক।
তবে, ইসলামী সভ্যতার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর অভিযোজনক্ষমতা, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা। এটি একই সাথে বিশ্বজনীনতা ও আঞ্চলিকতাকে পরিগ্রহ করে। এজন্য ইসলামী সভ্যতা যুগে যুগে এবং যেকোন অঞ্চলেই প্রাসঙ্গিক থেকেছে। তাছাড়া, ইসলামের অন্যতম স্পিরিট হলো সভ্যতায়ন। ইসলাম এমন একটি দ্বীন, যার মধ্যে সভ্যতার চেতনা নিহিত। ইসলাম শুধু ইবাদতের ধর্ম নয়; বরং এটি মানুষের সামগ্রিক জীবন, সমাজ ও সভ্যতাকে পরিগ্রহ করে। ইসলাম মানুষকে একটি সুনির্দিষ্ট ভিশন দেয় এবং সে ভিশন হলো মানুষের জন্য বসবাসযোগ্য দুনিয়া বিনির্মাণ। রাসুলে কারিম (সা.)-এর জীবনে আমরা দেখি সারাজীবন মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোকে রক্ষা করতে পারবে এমন একটি সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। অন্য কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে এটি সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ইসলাম এভাবে সভ্যতাকে ধারণ করেছে এবং মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে একীভূত করেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ইসলামী সভ্যতা কেবল মুসলমানের জন্য নয়; এ সভ্যতা মানুষের জন্য, মানবতার জন্য। কেননা এই সভ্যতার স্পিরিট হলো মানুষের জন্য বসবাসযোগ্য একটি দুনিয়া বিনির্মাণের সংগ্রাম। এখানে মানুষ বলতে পৃথিবীর আলো-বাতাসে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষ। এই মানুষের কোনো গুপ্ত শ্রেণিবিভাজন নেই। এই কারণেই আমরা নিজেদেরকে ইসলামী সভ্যতার সন্তান বলে থাকি। বিশেষত বাংলা অঞ্চলে, যখন আমরা একটি নতুন সভ্যতার কথা বলি কিংবা বাংলাদেশে যখন সভ্যতার পুনর্জাগরণের কথা বলি, তখন ইসলাম আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এখানে এটি কোনো জোরপূর্বক আরোপিত ধারণা নয়, বরং আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় ইসলাম কাজ করেছে এবং করছে।
সভ্যতা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। যেমন একটি পুরনো বৃক্ষকে এক স্থান থেকে তুলে অন্য স্থানে বসিয়ে দিলে সেটি টিকে থাকে না, সভ্যতাও তেমনিভাবে আরোপিত হতে পারে না। সভ্যতা অবশ্যই সেই মাটিতেই বিকশিত হয়, যেখানে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, আদর্শ, হাজার বছরের সংস্কৃতি এবং নিজস্ব ভাষার সাথে এর সঙ্গতি থাকে। সভ্যতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো ভাষা।
সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে ভাষা হলো প্রথমে ভাবের বাহন, এরপর চিন্তার আদান-প্রদানের মাধ্যম এবং সর্বোপরি জ্ঞানচর্চার বাহন। তবে ভাষা নিজেই সভ্যতার একটি শক্তিশালী অনুষঙ্গ। প্রখ্যাত দার্শনিক নোয়াম চামস্কির মতে, “একটি ভাষা কেবলমাত্র কিছু শব্দের সমষ্টি নয়; বরং একইসাথে এটি একটি সংস্কৃতি, একটি ঐতিহ্য, একটি সমাজের একত্রিত রূপ, সে সমাজের দ্বারা তৈরীকৃত সমগ্র ইতিহাস।”
ফলে ভাষা কেবল সংস্কৃতির অংশ নয়, বরং সভ্যতা বিনির্মাণের অন্যতম প্রধান উপাদান। আল মাওয়ার্দী সভ্যতার যে উপাদানগুলোর কথা বলেছেন তার মধ্যেও ভাষা একটি।
ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ভাষা যেমন সভ্যতা নির্মাতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্যও আগ্রাসনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো ভাষা। ব্রিটিশরা যখন প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে আসে, তখন এখানে প্রায় ১৮০টিরও বেশি ভাষা এবং প্রায় সাড়ে পাঁচশ উপভাষা বিদ্যমান ছিল। এখানে অসংখ্য জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল, অনেক আলেম ও চিন্তাবিদ ছিলেন।
কিন্তু উপনিবেশবাদীরা সেই ভাষাগুলোকে দমিয়ে দিয়ে ইংরেজিকে এখানকার মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। জ্ঞানের কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করে, স্কলারদের হত্যা করে। ফলস্বরূপ রাতারাতি মানুষ মূর্খতার এক অন্ধকার গহ্বরে পতিত হয়। মানুষ হঠাৎ করেই ভাষাহীন হয়ে পড়ে, তাদের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত প্রবাহ ব্যাহত হয়। মূলত, ভাষাকে দমন করা মানেই একটি জাতিকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা। আমাদের জাতীয় অগ্রযাত্রা এবং ইতিহাসকে পিছিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ভাষাগত আগ্রাসন যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আর কোন অস্ত্রই এতটা ফলপ্রসূভাবে ব্যবহৃত হয়নি। ভাষাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেই কুরআন, হাদিস থেকে শুরু করে ইতিহাস, দর্শন সবকিছুর ব্যখ্যা ও বয়ান পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।
এই কারণেই উপমহাদেশে বারবার ভাষা নিয়ে সংগ্রাম হয়েছে, রক্ত ঝরেছে। অথচ ভাষা তো যুদ্ধের বিষয় নয়, এটি তো নদীর মতো নিরন্তর প্রবাহমান, গতিপথে নানা জলধারার সাথে মিশে, নতুন নতুন শব্দকে নিজের মধ্যে ধারণ করে সমৃদ্ধ হয়, সামনের দিকে এগিয়ে যায়।
সে জায়গা থেকে বাংলা ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ একটি ভাষা। এ ভাষার রয়েছে গৌরবদীপ্ত অতীত, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সুগভীর ভিত্তিমূল। বৌদ্ধ যুগ থেকে শুরু করে ইসলামী সভ্যতার সময় পর্যন্ত এর ধারাবাহিক বিকাশ হয়েছে। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ভাষা সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে। আলাউলের পদাবলী, রামায়ণ, মহাভারতসহ অসংখ্য কালজয়ী গ্রন্থ যার জ্বলজ্বলে দৃষ্টান্ত। গুলেস্তা ও বোস্তা, ইউসুফ জুলেখা, জঙ্গনামা’র মত অসাধারণ অনুবাদ সাহিত্যও সমৃদ্ধ করেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শত শত বছর আগে লেখা সেই সাহিত্য আজও আমরা সহজেই বুঝতে পারি। শুধু সাহিত্যই নয়, এই ভাষায় তৎকালে অধিকাংশ জ্ঞানের মৌলিক সোর্সও বিদ্যমান ছিলো।
কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা ভাষা থেকে অনেক শব্দ ও পরিভাষা বাদ দিয়ে এ ভাষাকে সংকীর্ণ করার চেষ্টা হয়েছে। একসময় বলা হলো এর উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে, অথচ সংস্কৃত এসেছে অনেক পরে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এর বৈচিত্র্যময় বিকাশকে সংকুচিত করা হলো। ভাষাকে সংকীর্ণ করা মানে সভ্যতার বিকাশকেও সংকীর্ণ করা।
যেমন—আখলাক শব্দটি। এটি শত শত বছর ধরে আমাদের সমাজে ব্যবহৃত হয়েছে বিস্তৃত অর্থবোধক একটি পরিভাষা হিসেবে। বাংলা ভাষা ও পরিভাষাকে গ্রহণ করে আপন করে নিয়েছে। কিন্তু যখন এটি ইংরেজিতে Ethics হিসেবে অনুবাদ করা হলো, তখন তার বিস্তৃত সমুদ্রসদৃশ অর্থ একটি ছোট্ট পুকুরে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। ভাষার এই সীমাবদ্ধতা আমাদের সামাজিক আখলাককেও সংকুচিত করেছে। সেটি আমাদের সভ্যতাকেও প্রভাবিত করেছে।
আমাদের আরেকটি মৌলিক পরিভাষা হলো আমানত। আজকের দিনে আমরা আমানত বলতে সাধারণত বুঝি—কারো কাছে টাকা জমা রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা ফেরত পাওয়া। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমানতের ধারণা অনেক বিস্তৃত। আল্লাহ তাআলা মানুষের সাথে মহাবিশ্বের যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তার ভিত্তি হলো আমানত। অর্থাৎ এই দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ের সাথে, প্রাকৃতিক হোক বা কৃত্রিম, মানুষ একটি আমানতের বন্ধনে আবদ্ধ।
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই পরিভাষাটিও আজ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে মানুষ ভুলে গেছে যে পৃথিবীকে বিনির্মাণ করা, সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়া এবং মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা ছিল মানুষের ওপর ন্যস্ত একটি দায়িত্ব—একটি আমানত। এই দায়িত্ব বিস্মৃত হওয়ার কারণে আমরা আজ সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।
সুতরাং, ভাষা সভ্যতার বিনির্মাণের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি শুধু ভাব ও জ্ঞানের বাহন নয়, বরং মানুষের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যম।
ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের সভ্যতার ইতিহাসও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই ভূমি বৌদ্ধ সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা এবং দীর্ঘকালব্যাপী ইসলামী সভ্যতার সাক্ষী হয়েছে। ইসলামী সভ্যতা এই অঞ্চলে প্রায় ৫০০ বছর ধরে বিকশিত হয়েছে, এবং একটি সভ্যতা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদানকে এখানে সমুন্নত করেছে—নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, জ্ঞানের ধারা, বিশ্ববিদ্যালয়, নিজস্ব চিন্তাভাবনা। বাংলা ভাষা নিজস্ব ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ ইতিহাস বহন করে। এটি বহুভাষার শব্দভাণ্ডারকে ধারণ করে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়েছে। ফলে উপমহাদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানুষের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।
কিন্তু যখন বাইরের কোনো ভাষা বা সংস্কৃতি জোর করে আমদানি করা হয়, তখন সভ্যতার বিকাশ ব্যহত হয়, বরং পিছিয়ে যায়। আমরা ঔপনিবেশিক সময়ে এটি ভালোভাবে অবলোকন করেছি। উপনিবেশবাদ আমাদের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে দেয়নি; বরং পিছিয়ে দিয়েছে। কারণ তারা আমাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দমন করে বাইরের ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে আমাদের সভ্যতার বিকাশ স্থবির হয়ে পড়েছিল।
মানব ইতিহাসে সভ্যতার উত্থান যেমন ঘটেছে, তেমনি পতনও ঘটেছে। সভ্যতা বিনির্মাণের যে উপাদানগুলো, সেগুলো যখন কোনো সভ্যতায় দুর্বল হতে শুরু করেছে, তখন সেই সভ্যতার পতন হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি সময়েই মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সভ্যতা অপরিহার্য ছিল এবং থাকবে।
তাই আজ যখন আমরা আবার সভ্যতার আলাপ করি, সভ্যতার পুনর্জাগরণের কথা বলি, তখন অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। একইসাথে আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া মীরাস, আমাদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস এবং আমাদের দ্বীন—এসব কিছুকে এ আলাপের আওতাভুক্ত করতে হবে। সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আজকের সময়ের বাস্তবতাকেও স্বীকার করে নতুন এক সভ্যতা বিনির্মাণ করতে হবে।
বাংলা অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে, আমাদের নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিকশিত করা এবং ইসলামী সভ্যতার মৌলিক চেতনা, আখলাক ও মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। সেইসাথে আজকের দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং এই সময়ের চাহিদা পূরণে সক্ষম— এমন এক সভ্যতা বিনির্মাণের দিকে আমাদের ধাবিত হতে হবে।
কৃতজ্ঞতা:
- ইসলাম ও সভ্যতা- হেবা রউফ ইযযেত
- জাতির মূল স্তম্ভ দ্বীন ও ভাষা; বাংলাদেশে আমাদের জাতিসত্তার ইশতেহার- হাসান আল ফেরদৌস
- বাংলা ভাষা ও জাতীয় জাগরণে নজরুল- আব্দুল হাই শিকদার
- সভ্যতা বিনির্মানে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ভূমিকা; মালিক বিন নবীর বয়ান- আব্দুল আযিয বারগৌত
- ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর কোর্সসমূহ
- TheSocio-Intellectual Foundations of MALEK BENNABI’S APPROACH to CIVILIZATION-Badrane Benlahcene