সাহিত্যের গোড়ার কথা
ইসলামের নবী কেবল আরব দেশে আসেননি, দুনিয়ার সব দেশেই এসেছেন। আল্লাহর পাঠানো সবই ছিলেন ইসলামের নবী। সাহিত্যের আলোচনায় প্রথমেই নবী প্রসংগে এলাম কেন? কারণ নবীরাই মানুষের প্রথম শিক্ষক । নবীরাই সমাজ সংগঠক।নবীদের যোগ মানুষের সাথে তৃণমূল পর্যায় থেকেই। মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য নবীদের ভূমিকা ছাড়া কল্পনাই করা যেতে পারে না। নবীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের সন্ধান এনেছেন এবং সে পথ মানুষকে দেখাননি এমনটি হতে পারে না। সাহিত্য মানুষের জীবনের একটা প্রয়োজনীয় অংশ আর নবীরা এ অংশে কোনা অবদান রাখেননি একথা কেমন করে ভাবা যেতে পারে? নবীরা যেসব সহিফা ও কিতাব এনেছেন সেগুলোও সাহিত্যরস সমৃদ্ধ। নিছক কাটখোট্টা আলোচনা কোনো কিতাবেই নেই। জীবনকে উপলব্ধি করে আলোচনাগুলো জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে জীবনরস সমৃদ্ধ করে। তবেই তা মানুষের কাছে আকর্ষনীয় মনে হয়েছে। মানুষ তার সাহায্যে উন্নতি করে উন্নত জীবন সমাজ সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে এবং তার ভিত্তিতে মানুষ করেছে সাহিত্য সাধনা। এটাই হচ্ছে মানুষের সমিতা সাবনার গোড়ার কথা।
আজ যেন সাহিত্য বলতে নব্বুওয়াতী খাতের ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত একটা স্রোত বুঝায়। এটা মানুষের জীবনের অন্যান্য খাতে ভুলের মতো একটা ভুল। ‘রাধাকৃষ্ণের লীলা’ এই ভুলেরই একটা ফসল। সাহিত্যকেও নবুওয়াতী ধারায় সম্পৃক্ত হতে হবে। নয়তো তা মানুষের জন্য উপাদেয় ও উপযোগী হতে পারে না। সাহিত্য রস ও সাহিত্যের আস্বাদ মানুষের জীবন গঠনে সাহায়তা না করে যদি ক্ষতি সাধন করে তাহলে কে এমন মানুষ আছে যে তা গ্রহণ করবে? শেষ নবীর কিতাব আল কুরআনে জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে : ‘দুনিয়ার জীবনটা তো খেলা-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং অর্থ সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হলো, বৃষ্টি হয়ে গেলো এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারপর সে ফসল পেকে গেলো এবং তোমরা দেখতে পেলে তা হলুদ বর্ণ ধারণ করছে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আখেরাত এমন স্থান যেখানে রয়েছে আজাব এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থির জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।’(আল হাদীদ : ২০)
এ জীবনকে আমরা গ্রহণ করেছি এবং জীবনকে উৎকর্ষিত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জীবনের প্রতারণার জালে জড়িয়ে আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলতে পারি না। আমাদের সামনে রয়েছে আখেরাতের জীবনের কামিয়াবী। এই আখেরাতের জীবনের জন্য দুনিয়ার জীবন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।দুনিয়াকে বলা হয়েছে আখেরাতের কৃষিক্ষেত (হাদীস)। এখানে যেমন পরিশ্রম করা ও যত্ন নেওয়া হবে তেমনি আখেরাতে তার ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতারণার জালে যদি আমরা ফেঁসে যাই, দুনিয়ার আসল কাজে জড়িত না হয়ে যদি প্রতারণামূলক খেলা-তামাশায় মেতে উঠি এবং দুনিয়ার সম্পদ আহরণ ও ভোগ বিলাসে লিপ্ত হই, তাহলে আমাদের আখেরাতের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়া আমাদের সামনে আছে এবং আখেরাত সামনে নেই। তবে আখেরাত আমাদের কল্পনা জগতের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের সকল বাস্তবতার সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। কাজেই তাকে আমার জীবন কর্ম ও জীবন চিন্তা থেকে আলাদা করতে পারি না।
জীবনকে খেলা তামাশা বলা হয়েছে কোন অর্থে? স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের অর্থে। একশো বছরের জীবনের বাস্তব কঠিন কর্মক্ষেত্রে খেলা তামাশা মাত্র কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার আনন্দ বিনোদন। এই স্বল্পস্থায়ী ক্ষণটুকুর পর আবার বাস্তব কঠোর কঠীন জীবন শুরু। ঠিক তেমনি এই স্বল্পস্থায়ী জীবনটা খেলা তামাশা এবং আখেরাতটাই বাস্তব ও অনন্তকালীন জীবন। কাজেই আমাদের যা কিছু কাজ চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য। জীবনটা শুধু দুমুঠো খাদ্য গ্রহণ, শরীর ঢাকার জন্য বস্ত্র আহরণ এবং শারীরিক, জৈব ও যৌন চাহিদা পুরণ করার নাম নয়। বরং এই স্বল্পকালীন দুনিয়ার জীবনকে অনন্তকালীন আখেরাতের জীবনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই
জীবনটাকে আমাদের বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে।
জীবনের সাথে সাহিত্য, জীবনকে পরিশীলিত ও বিকশিত করার জন্য সাহিত্য। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নয়। জীবনকে বিকৃত করেও সাহিত্য নয়। সাহিত্য আমাদের জীবনেরই নির্যাস।
সাহিতা আমাদের সুন্দর করবে। আমাদের পরিশীলিত ও পরিশ্রুত করবে। আমাদের জীবনকে ক্লেদমুক্ত অপাপবিদ্ধ করবে। সাহিত্য আমাদের সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী করবে। জীবনের ঘটনাবলী থেকে আমরা সত্য ও ন্যায়ার বাছাই করে নিতে পারবো। জীবন সংগ্রামে সংহিতা কেবলমাত্র একজন দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। বরং একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক ও দক্ষ সমালোচকের দৃষ্টি হবে সাহিত্যের দৃষ্টি। এই স্বল্পকালীন পৃথিবীর জীবনে মানুষকে তার যথাযথ ভূমিকা পালনে অর্থাৎ মানুষ কিভবে যথার্থ মানবতার আধারে পরিণত হতে পারে এবং নিজের নফসের ও জীব-জড়ের কৃত্রিম শক্তির অনুগত না হয়ে বিশ্ব জাহান ও বিশ্ব প্রাকৃতিত্ব মালিক একমাত্র আল্লাহর অনুগত হতে পারে, তাই হবে সাহিত্যের সাধনা।
গাংগেয় বদ্বীপে ইসলামের ভিত
বাংলাদেশে ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবার পরই ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি। ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকালেই খ্রিষ্টীয় সপ্তম ইসলামের দাওয়াত বাংলাদেশে প্রবেশ করে। প্রাকৃতিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে এখানকার পরিবেশ ছিল অনুকূল। এই অনুকূল পরিবেশে ইসলামের দাওয়ার সহজে বিস্তার লাভ করে। উপমহাদেশের কেন্দ্র দিল্লী থেকে বহু দুরে থাকায় বিদেশী আক্রমণকারীদের দৃষ্টি কমই এদিকে পড়েছে এবং অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরাও এখানে কম সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া সবুজ শ্যামল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত ও প্রাকৃতিক বন জংগলাকীর্ণ সমতলভূমি এমন এক ধরনের নৈসর্গিক গুরু গম্ভীর পরিবেশ তৈরি করেছিল যা নিরিবিলি নিশ্চিন্তে সত্য দীনের দাওয়াত ছড়াবার পথে সহায়ক হয়েছিল। ফলে স্থানীয় বৌদ্ধ, জৈন ও আর্য ধর্ম প্রভাবিত জনগোষ্ঠী ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সংগে আর একটি বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার মতো। কয়েক হাজার বছর থেকে এ এলাকায় বিপুল সেমেটিক জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল তৌহীদবাদী। কালের আবর্তনে তাতে মরচে পড়ে গিয়েছিল। আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বৌদ্ধবাদী ও জৈনবাদী ধর্মীয় সংস্কার যেভাবে এ এলাকায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল ঠিক একই ধারায় ইসলামী তৌহীদবাদ সমগ্র বাংলার অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়েছিল অতি অল্প সময়েই। যেন এটা ছিল তাদের প্রাণের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ। সকালে হারিয়ে গিয়েছিল আবার সন্ধ্যায় তাকে ফিরে পেয়েছিল, এভাবে তারা এটাকে গ্রহণ করেছিল। তাই হিন্দুস্তানের অতি প্রাচীন মুশরিকী আবাসভূমির মধ্যে গড়ে উঠতে পেরেছিল একটি বিশাল তৌহীদবাদী জনগোষ্ঠী।
আলেম উলামা ও কাজীদের জ্ঞানচর্চা
মুললিম বিজেতাদের পূর্বে সমুদ্র ও নদীপথে আরব বণিকদের সাহায্যে বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে ইসলামের প্রথম যুগেই। এরপর ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটতে থাকে। মুসলিম বিজেতাদের ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ ধারা বলিষ্ঠতা অর্জন করে। এ সময় এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম আইনঙ্গ তথা ফকীহ ও কাজীদের আগমন ঘটতে থাকে। তারা ছিলেন ইসলামি শাস্ত্রে সুদক্ষ ও পারদর্শী। মুসলিম বিশ্বে যে বিপুল জ্ঞান চর্চা হচ্ছিল তার ঢেউ এখানেও এসে পড়ে। ফলে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকেই এখানে গৌড়, পান্ডুয়া,মাহিসুন (মাহিসন্তোষ), সোনারগাঁও ইত্যাদি এলাকায় বড় বড় ইলমী তথা ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এখানকার মাদরাসাগুলোতে ইসলামী জ্ঞান আহরণ করার জন্য সমগ্র হিন্দুস্তান থেকে ছাত্রদের আগমন ঘটতো। শায়খ তাকিউদ্দীন আরাবী, শায়খ শরফুউদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী, শায়খ আলাউল হক, হযরত শায়খ নুর কুতবুল আলম ইত্যাদি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্ঞানসাধকগণ এসময় এসব জ্ঞানকেন্দ্র আলোকিত করেছিলেন। তাই বলা যায়, ইসলামি শাসনের প্রথম যুগেই বাংলাদেশ ইসলামী জ্ঞানচর্চার পীঠস্থানে পরিণয় হয়। এখানে এর পরিবেশও ছিল। তখন জ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল আরবী ও ফারসী । ফলে বিদেশাগত মুসলমান এবং এদেশীয় শিক্ষিত, জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে মূলত এ জ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের মূল কেন্দ্র দিল্লীতে শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর জ্ঞান সাধনার এই কেন্দ্র বাংলা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।
সাধারণ মুসলমানের ভাষা ছিল বাংলা। ইতিপূর্বে পাল যুগে বৌদ্ধ শাসনামলে সাহিত্যের ও রাজভাষা সংস্কৃত থাকলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চা যা একটু আধটু হয়েছিল সেনযুগে হিন্দু শাসনামলে এসে তা সম্পূর্ণরণে রহিত হয়ে যায়। সংস্কৃতের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা ও রাজকার্য চলতে থাকে। এজন্য একটা দরবারী জগাখিচুড়ি মার্কা সংস্কৃত ভাষাও গড়ে ওঠে। মুসলিম সুলতানদের শাসনামলে মূলত বাংলা ভাষার পুনরজন্ম হয়। মুসলিম শাসকগণ তাঁদের দরবারী ও রাজভাষা ফারসী এবং ইলমী ভাষা আরবী রাখলেও মুসলিম এবং এদেশটার জনসাধারণের ভাষা বাংলার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করার জন্য রাজকোষ অর্থ বরাদ্দ করেন। ফলে ধীরে ধীরে বাংলা ইলমী ভাষায় রুপান্তরিত হবার পথ প্রশস্ত হতে থাকে।
সুফী সাধকদের ইসলাম প্রচার
মুসলমানদের মধ্যে দিনরাত আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল একটি দল গড়ে উঠেছিল। তাঁরা ছিলেন সুফী নামে খ্যাত। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের য্যোগী, সন্ন্যাসী ও রাহেবদের মতো তাঁরা সংসার বিরাগী ছিলেন না। তাঁরা সংসার,ধর্ম, জ্ঞানচর্চা এবং এমনকি জিহাদ চর্চাও করেছেন। এই সংগে আল্লাহর ইবাদত ও মানবতার সেবাই ছিল তাঁদের ব্রত। বাংলায় ইসলাম প্রচারে এই সুফিদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই বাংলার মুসলিম সমাজে সুফীদের জীবন চর্চার প্রভাব বেশী অনুভুত হয়েছে। কিন্তুু সুফীগণ ইসলামী শরীয়তের বাইরে কোনো অভিনব ও কৃত্রিম জীবন যাপন করতেন না।তারা ছিলেন আদর্শ মুসলিম এবং আদর্শ ইসলামী চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন কুরআনের সুরা আল কাসাসের ৭৭ নং আয়াতে ‘আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কারা,তবে সেই সংগে দুনিয়ায় তোমার প্রাপ্য অংশ ভুলো না।’ মর্মবাণীর যথার্থ আধার। তাঁরা সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করেননি।খিলাফয়ে রাশেদার চার পাঁচশো বছর পরে সৈরতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক শাসকদের সাথে কোথাও তাঁরা কোনো আপোশ করেন নি। বরং কবি ও দার্শনিল ইকবালের ভাষায় অনেক জায়গায় ‘সিকান্দাররা কালিন্দরদের কথায় ওঠাবসা করতেন। দিল্লীর খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী র., হযরত বু আলী কলন্দর র. আজমীরের হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী র. এবং গৌড়ের হযরত শাহ নূর কুতুবুল আলম র. এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সুফীরা কখনো কোনো অন্যায়, জুলুম ও শোষণের সাথে আপোশ করেননি। তাঁরা ব্যাপক হারে জনগণকে ইসলামের তালিম ও তরবীয়ত দিয়েছেন এবং তাদের ইসলামী জীবন যাপানে সাহায্য করেছেন।
এই সুফীদের হাতে এক সাথে এত বেশী সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে যে, তাদের ইসলামী তালিম ও তরবিয়ত দেয়া এবং তাদের ইসলামী চরিত্র গঠন করা এই সীমিত সংখ্যক সুফীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যদি পনের শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সুফী হযরত মীর সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানীর একটি পত্র থেকে জানা যায় ‘মোটকথা বাংলার বড় শহরের কথা বাদ দিলেও এমন কোনো ছোট শহর বা গ্রাম নেই যেখানে খোদাভীরু সুফীগণ আগমন ও বসতি স্থাপন করেননি’। তারপরও বলা যায় কুরআন ও সুন্নাহ চর্চার অবর্তমানে বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারেনি। যার ফলে মুশরিকী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বেড়া টপকে তারা ইসলামী মিল্লাতের আওতাভুক্ত হলেও ওদিক থেকে আসার সময় নিজেদের বহিরংগে মুশরিকী সভ্যতা সংস্কৃতির অনেক কিছু সাথে করে নিয়ে আসে। কালক্রমে এগুলো মুসলিম জীবন ধারায় জেঁকে বসে।
মুলত ইসলাম এমন একটা জীবন ব্যবস্থা ও জীবনাদর্শ যা মোটেই অনুষ্ঠান নির্ভর নয়। বরং কতিপয় বিশ্বাস ও বিশ্বাসভিত্তিক কর্মের ওপরই তা নির্ভরশীল। ইসলামের উৎস হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল। তৃতীয় কোনো সত্তার সাথে ইসলাম সরাসরি জড়িত নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে সুফী দরবেশ বা উলামায়ে কেরামের যারাই জড়িত থাক না কেন সেক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ চর্চার যতটুকুন কমতি থেকে গেছে তা ইসলামী ভিত্তির দুর্বলতা হিসাবেই চিহ্নিত হবে।
স্থানীয় কুফরী উপাদান
বাংলায় মুসলমানদের আগমন এবং ইসলামী আদর্শবাদের প্রসারের পূর্বে যেসব ধর্মমত বিস্তার লাভ করেছিল সেগুলির পেছনে কোনো পরিচিত ও পরীক্ষিত আসমানী কিতাবের সমর্থন ছিল না। বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদ ও আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদেরই এখানে প্রচলন ছিল বেশী। এই তিন বৃহৎ ধর্মমতের বাইরে কাল্পনিক দেবদেবীর পূজারও একটা ধারা প্রচলিত ছিল। মূলত সবগুলো ধর্মমতই ঈশ্বর আরাধনার নামে প্রকৃতি পূজা ও পুতুল পুজায় পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মমত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদিকে অভ্রান্ত মনে করতো। কিন্তু এর পেছনে কোনো শক্তিশালী ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারতো না। ফলে সেগুলো প্রায় গালগল্প, পুরাতন কাহিনী, নিছক নীতিকথা এবং দার্শনিক আলোচনার কচকচি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আল্লাহর অস্তিত্বে বিভিন্ন জীব ও জড়কে শরীক করা এবং এতদসংক্রান্ত ব্যাপক কুসংস্কারই ছিল ধর্ম। ফলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে নানান বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রকৃত সত্যকে মেনে নেবার মতো মানসিকতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।
আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতি বর্ণবাদের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করে ফেলেছিল। মানুষ সরাসরি মানুষের দাসে পরিণত হয়েছিল। বরং একদল মানুষ সমাজে অন্ত্যজ ও মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। বিরোধী ধর্ম মত জৈন ও বৌদ্ধবাদও ধীরে ধীরে বর্ণভেদ প্রথার হাতে নিজেদের সোপর্দ করে দিয়েছিল। অথবা কোথাও আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করে সহজিয়া ও তান্ত্রিক ইত্যাদি মতবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিল। অর্থাৎ ধর্মের নামে সমগ্র বাংলাদেশে ধর্মীয় অনাচার কুসংস্কার ও চারিত্রিক নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। এই ছিল তখনকার বাংলা সাহিত্য চর্চার পটভূমি বা পরিবেশ।
মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা
বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েকশো বছর পূর্ব থেকে ইসলাম প্রচারকদের এদেশে আগমন শুরু হয়। ইসলামের খালেস তৌহিদবাদ ও সামাজিক সাম্য বাংলার পৌত্তলিক সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সামাজিক অবিচার, জুলুম, নিপীড়ন এবং প্রশাসনিক শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী পরিবেশ হয়ে ওঠে। সর্বোপরি নিরাকার সর্বশক্তিমান একক স্রষ্টার আরাধনার ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকালে চতুরদিকে যখন ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বেড়ে চলছিল তখনকার সমাজে ইসলামের শক্তির একটা অস্পষ্ট প্রভাব সমসাময়িক একটি কবিতায় ফুটে উঠেছে। অজ্ঞতাবশত কদি রামাই পণ্ডিত তের শতকের শেষের দিকে লিখিত তাঁর এ কবিতায় ইসলামী আদর্শ ও সদ্যগঠিত মুসলিম সমাজের চিত্র সঠিক রূপে আঁকতে না পারলেও ইসলামের অসাধারণ ও যাদুকরী প্রভাব এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতাটির নাম নিরঞ্জনের রুষ্মা । এ কবিতায় মধ্যযুগীয় ইউরোপের পোপ ও যাজকদের ক্ষমতার মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু পুরোহিতদের ক্ষমতার কিছু আভাস পাওয়া যায়। জাজপুর তথা ওড়িষার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সদ্ধর্মীদের নিকট কর আদায় করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠী গলার পৈতা কানে বেড় দিয়ে বৌদ্ধ জনসাধারণকে শাপ শাপান্ত করে তাদের বাড়ি-ঘর আগুন জালিয়ে ছারখার করে দেয়। তাদের এ জুলুম উৎপীড়ন দেখে ধর্মদেবতা বৈকুন্ঠে বসে এর প্রতিবিধানে মনোনিবেশ করলেন। ধর্মরূপী মুসলমানরা জাজপুরে প্রবেশ করলো এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। তারা দেউল ও দেব বিগ্রহ ভেঙে পুতুল পুজার অবসান ঘটিয়ে ব্রাহ্মণদের বিনাশ করলো। কবির কল্পনায় বিষয়টা এভাবে ধরা দিয়েছে:
ধর্ম হইল জবন রূপী
মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হত্র
ত্রিভুবনে লাগে ভ-এ
খোদায়ে বলিআ এক নাম।।
(নিরঞ্জন নিরাকার
হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলএ দম্বদার।।
জথেক দেবতাগণ
সভে হৈয়্যা একমুন
আনন্দেতে পরিলা ইজার।।)
ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ
বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপানি।
গনেশ হইলা গাজী
কার্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা জথ মুনি।।
তেজিয়া আপন ভেক,
নারদ হইলা শেক,
পুরন্দর হইলা মলনা।
চন্দ্র, সূর্য আদি দেবে
পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলে বাজাএ বাজনী।।
আপনি চণ্ডিকা দেবী,
তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর।
জথেক দেবতাগণ,
সভে হয়া একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর।।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে,
ক্যাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পাএ,
রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল।।
শব্দার্থ: দম্বদার – দম-ই-মদার, বদরুদ্দীন মওলানা শাহ-ই মাদার, পনের শতকের লোক, এ অংশটি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত। আদম্ফ – আদম। পাখাড়-পাকড়াও। কবির বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে: ধর্মদেবতা মাথায় কালো টুপি পরে ত্রিকচ অর্থাৎ
তীরকাশ তথা তীরধারী কামান নিয়ে উন্নত জাতের অশ্বে আরোহন করে ত্রিভূবনে ভীতি সঞ্চারকারী ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনি তুলে জবন তথা মুসলিম রুপ ধারণ করলেন। (নিরঞ্জন নিরাকার বেহেশতের অবতার হয়ে মুখে দম-ই-মাদার বলতে লাগলেন। সমস্ত দেবতা একমত হয়ে আনন্দে ইজার পরে নিলেন অর্থাৎ সবাই মুসলমান রূপ ধারণ করলেন।) ব্রহ্ম মুহাম্মাদ হলেন, বিষ্ণু হলেন পয়গম্বর এবং মহাদেব হলেন আদম। পনেশ গাজী, কার্তিক কাজী এবং যত মুনি ঋষি ফকির দরবেশ সাজলেন। আপন বেশভূষা পরিত্যাগ করে নারদ শেখ ও পুরন্দর মওলানা সাজলেন। চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি আদি দেব পদাতিক হয়ে বাজনা বাজিয়ে তাদের সেবা করতে লাগলেন। চণ্ডিকা দেবী স্বয়ং হাওয়া বিবি হলেন আর পদ্মাবতী হলেন বিবি নূর, যত দেবতা ছিলেন সবাই এভাবে মুসলমান সেজে এক সাথে জাজপুরে প্রবেশ করলেন। তারা দেবালয় ও দেবগৃহ ভাঙলেন, মনের আনন্দে লুটতরাজ করে খেতে লাগলেন এবং সংগে সংগে অপরাধীদের ‘পাকড়াও পাকড়াও’ ধধ্বনি তুললেন। এই দারুণ গণ্ডগোল দেখে রামাই পণ্ডিত ধর্মের পায়ে লুটিয়ে পড়লো এবং গান গাইলো। এতে বুঝা যাচ্ছে দেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে এবং ইসলামের ন্যায়ের দন্ড তথাকথিত বর্ণবাদী সমাজের জুলুম, অবিচার ও উৎপীড়ন নির্মূল করে সমাজে শান্তি, সমতা ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনছে। মানুষ ইসলামের হক ও সাম্যের আহবান গ্রহণ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে।
বাংলায় তুর্কীদের হাতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তুর্কীরা পাঠান ও মোগলদের তুলনায় বেশি ইসলামী ভাবাপন্ন ছিলেন। ফলে বাংলায় আরব দেশের মতো না হলেও তাদের সাথে সামঞ্চস্যশীল একটা ন্যায় ইনসাফ ও সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলায় মুসলমানদের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সমাজে একটা ইসলামী পরিবেশ ও ইসলামী দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি হচ্ছিল। সেটা ছিল : মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই এক আদমের সন্তান। এক আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক। একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আরাধনা করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। সবাই তাঁর অনুগত। বাংলার বিশাল ভূখন্ডে (অর্থাৎ বাংলা বিহার, ওড়িষা ও বৃহত্তর আসাম) এই তৌহিদী পরিবেশ দানা বেঁধে উঠছিল। কিন্তু যেহেতু বাংলা ভাষা তখনো স্থিতিশীলতা লাভ করেনি, তখনো সৃজ্যমান ছিল (কয়েকশো বছর আগের চর্যাপদের ভাষা দেখলে তা বোঝা যাবে) আর সৃজ্যমান ভাষায় বড় ও সৃষ্টিশীল কোনো কিছুর আশা করা যায় না, তাই এসময়কার সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থাকলেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবির রচনার সাক্ষাত পাওয়া যায় না। পনের শতক থেকে আমরা মুসলিম কবিদের একটা ‘ধারাবাহিকতা লক্ষ করি। শাহ মুহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন, মুজাম্মিল তাদের অন্যতম। শাহ মুহাম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্য ‘য়ুসুফ-জলিখা’ রচনা করেন গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪১০)। কবি জৈনুদ্দীন ছিলেন গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে (১৪৭৪-১৪৮১) সভাকবি। কবি মুজাম্মিল পনের শতকের মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পনের শতক থেকে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত যে অসংখ্য মুসলিম কবির সন্ধান পাই তাদের অন্যতম হচ্ছেন : সৈয়দ সুলতান, (১৫৫০-১৬৪৮) শেখ ফয়জুল্লাহ, শুকুর মাহমুদ, (১৬৮০-১৭৫০) সাবিরিদ খান, দোনাগাজী, বাহরাম খান, আফজাল আলী, মুহম্মদ কবীর, মুহম্মদ খান, (১৫৮০-১৬৫০) দৌলত কাজী, (১৬০০-১৬৩৮) আলাওল, (১৬০৭-১৬৮০) শেখ পরান (১৫৫০-১৬১৫) আবদুল হাকীম (১৬২০-১৬৯০) শাহ গরীবুল্লাহ, মুহম্মদ ইয়াকুব, হায়াত মাহমুদ, মুহম্মদ মুকীম (১৭০০-১৭৭৫), সায়্যিদ হামজা (১৭৫৫-১৮১৫) প্রমুখ।
মুসলিম শাসনের অবসানের পর বিশেষ করে এদেশের অমুসলিম সমাজের সহযোগিতায় বিদেশী খৃস্টান বণিক ইংরেজরা দেশের শাসন যন্ত্র দখল করে। ফলে উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বসে বাংলা ভাষার নিত্য ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দগুলো দুই হাতে বাদ দিয়ে মৃত সংস্কৃত ভাষার অপ্রচলিত ও অপরিচিত কঠিন শব্দসম্ভারে ভারাক্রান্ত করে একটা নতুন বাংলা গদ্য তৈরি করা হয়। অতপর এ ভাষায় গদ্য ও পদ্য লেখার কাজ চলে। ইংরেজের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থাকার কারণে মুসলমানরা প্রথমে এ বিষয়ে উদাসীন থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাদের এক ধাপ পিছিয়ে আসতে হয়। ইংরেজের সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্দীপিত হিন্দু মনীষার কারণে হিন্দু ঐতিহ্য এই সাহিত্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। তবুও এই উনিশ শতকে যেসকল মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের জন্ম হয়েছে তারা এর মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী স্বতন্ত্র পথটি তৈরি করার প্রচেষ্টা চালান। এদের মধ্য থেকে কয়েকজন শ্রেষ্ট কবি সাহিত্যিকের নাম এখানে উল্লেখ করছি – এরা হচ্ছে ঔপন্যাসিক প্রবন্ধকার মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) প্রবন্ধকার শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১), কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), প্রবন্ধকার ও সংবাদিক মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), কবি প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক সৈয়্যদ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), প্রবন্ধকার ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৯৯-১৯৩৬), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), কথাশিল্পী এস, ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ঔপন্যাসিক নজীবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), কবি শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬), ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কবি কথাশিল্পী ও প্রবন্ধকার বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), কবি ও ঔপন্যাসিক শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫)।
মুসলিম সাহিত্যের উপাদান
মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা যখনই সাহিত্য ময়দানে পদার্পণ করেছেন তাদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র ও সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। তাদের একটা বিশিষ্ট অংশ নিজেদেরকে নিছক কবি সাহিত্যিক মনে করেননি। তাঁরা মনে করেছেন বাংলার এই কুফরী সমাজে যেমন তাদের একক তৌহিদবাদী হিসাবে টিকে থাকতে হবে তেমনি এখানে কুফরীর গলদ চিহ্নিত করাও তাদের দায়িত্ব। এজন্য তারা একই সংগে ভাষার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। যে ভাষায় ইসলামী আদর্শ ও আচরণ প্রকাশ এবং তার বিকাশ সাধন করা যায় সে ভাষা প্রয়োগ করার কথা তারা চিন্তা করেছেন। যেমন :
দেশেত আলিম থাকি যদি ন জানায়।
সে আলিম নরকেত যাইব সর্বথায়।।
নর সবে পাপ কৈলে আলিমের ধরি।
আল্লাহর সাক্ষাতে মারিবেস্ত দণ্ড বেড়ি।।
তোম্মারা সবের মেলে মোর উৎপন।
তেকারনে কহি আমি শাস্ত্রের বচন।।
আল্লায় বলিব তোরা আলিম আছিলা।
মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ ন কৈলা।।
আছুক আপনা পাপ আলিমে খণ্ডাইব।
পরের পাপের লাগি লাঘব পাইব।।
(শব-ই-মিরাজ: সৈয়্যদ সুলতান)
কবি সৈয়্যদ সুলতান যেমন হিন্দু ধর্ম কাহিনী ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইসলামী কাহিনী ও প্রস্তাব বাংলায় লিখে প্রচার করেছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর শাগরিদ কবি মুহম্মদ খান পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘মকতুল হুসৈন’ এও এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। এ গ্রন্থটি রচিত হয় ১৬৪৫ খৃস্টাব্দে। এতে বলা হয়:
হিন্দুস্থানে লোকে সবে ন বুঝে কিতাব।
ন বুঝি শুনি নিত্যি করে মহাপাপ।।
তেকাজে সংক্ষেপ করি পঞ্চালী রচিলুং।
ভাল মন্দ পাপ পূণ্য কিছু ন জানিলুং।।
পঞ্চালী পড়িতে সবে মনে ভয় পাই।
অবশ্য কিতাব কথা শুনিবেক যাই।।
কিতাবে আল্লার আজ্ঞা শুনিবেন্ত যবে।
দান ধর্ম পূণ্য কর্ম করিবেন্ত তবে।।
অবশ্য মোহোরে সবে দিবে আশীর্বাদ।
মহাজন আশীর্বাদ খণ্ডিবে প্রমাদ ॥
বিশেষ পীরের আজ্ঞা ন যায় লঙ্ঘন
রচিলুং পাঞ্চালিকা তাহার কারম।।
শেখ মুত্তালিব (১৫৯৫-১৬৬০) লিখছেন:
আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারনে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ।।
মুছলমানী শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু।।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়া মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমিন দোয়া করিব আমারে।।
মুমীনের আশীর্বাদে পূণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক।।
এসব জানিয়া যদি করয়ে রক্ষণ
তবে সে মোহোরে পাপ হইবে মোচন ॥
(কিফায়িতুল মুসল্লীন)
মধ্যযুগের মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা তাদের জীবন ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা তাদের সাহিত্যে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত ব্যপক। কেবলমাত্র মানব মানবীর প্রেমোপাখ্যান লিখেই তারা নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেননি। এইসংগে তারা ইসলামী শরীয়ত, হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর মোকাবিলায় মুসলিম পৌরাণিক কাহিনী, হিন্দুদের পৌরাণিক ও আজগুবি সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনায় সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ ইসলামী সৃষ্টিতত্ব, ইসলামী দর্শন ও সুফীতত্ব, মুসলিম ঐতিহাসিক কাব্য, রূপক সাহিত্য তথা একপ্রকার রূপকের মাধ্যমে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা, মর্সিয়া সাহিত্য, মারফতী ইত্যাদি ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন গান রচনা করেন। তাদের এতদসম্পর্কিত কিছু গ্রন্থের নামোল্লেখ করলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা আরো একটু সুস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে মনে হয়। যেমন:
শরীয়ত নামা- নসরুল্লাহ খান
নসীহত নামা-শেখ পরান
কিফায়িতু-ল-মুসল্লীন-শেখ মুত্তলিব
হিদায়িতু-ল-ইসলাম-নজরুল্লাহ খান
নামাজ মাহাত্ম্য- মুহাম্মদ জান
শিহাবুদ্দীন নামা-আবদুল হাকীম
হিতজ্ঞান বাণী- হায়াত মাহমুদ
নবী বংশ-সৈয়্যদ সুলতান
রসূল বিজয়-ঐ
শব-ই-মিরাজ- ঐ
ওফাৎ-ই-রসূল- ঐ
ইবলিস নামা ঐ
আম্বিয়া বাণী- হায়াত মাহমুদ
কিয়ামত নামা -মুহম্মদ খান
নূর নামা (সৃষ্টিতত্ব)- শেখ পরান
নূর নামা (সৃষ্টিতত্ব)- আবদুল হাকীম
জ্ঞান প্রদীপ (সূফীতত্ব) সৈয়্যদ সুলতান
কারবালা (মর্সিয়া সাহিত্য)-আবদুল হাকীম
জঙ্গনামা- গরীবুল্লাহ ও ইয়াকুব
সায়াৎনামা -(জ্যোতিষ শাস্ত্র) মীর মুহাম্মদ শফী
এ ধরনের ইসলামী জ্ঞান ও মুসলিম জীবন সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ তারা রচনা করেন। তাদের লেখনীর সাহায্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার একটা সাগর সৃষ্টি হয়।
তবে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, মুসলিম কবিদের এই ইসলাম চর্চার সাথে খালেস তৌহীদের সম্পর্ক যতটুকু তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পর্ক সুফীতাত্বিক মরমীবাদের। বাংলার কবিদের কাব্যচর্চার ওপর ইরানের প্রভাব ব্যাপকতর। সে তুলনায় আরবীয় প্রভাব অতি সামান্যই। আর ইরানী প্রভাব মানেই হচ্ছে ইরানী সাহিত্যে যে মাশশায়ী, ইশরাকী ও ইরফানী ইত্যাদি এরিস্টটলীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিবাদী দর্শন এবং তাসাউফের গৃঢ় রহস্যভিত্তিক মরমীবাদের প্রসার ঘটে তারই প্রভাব বাংলার কবিদের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে।
আব্বাসীয় আমলে হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে গ্রীক দর্শনের আলোচনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী ও ফখরুদ্দীন রাযীর আক্রমণাত্মক ভূমিকার ফলে মাশশায়ী দর্শন ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে ফেললে ইশরাকী ও ইরফান তাসাউফ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইশরাকী তাসাউফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খ শিহাবদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে হাবস ইবনে আমীরাক সোহরাওয়দী (৫৪৯হি:- ৫৮৭হি:)। রেই, হামেদান, কাযভীন ইত্যাদি ইরানের বিভিন্ন শহরে তাসাউফের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা গড়ে ওঠে। ফারসী সাহিত্য মূলত তাসাউফের এই ভাবধারাগুলির মধ্যেই বিকশিত হয়। পনের শতকের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর থেকে শুরু করে উনিশ শতকের বাংলার কবিদের মধ্যে এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইরানী কবিদের সাথে তারা গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন ‘ইউসুফ জুলিখা’সহ ইরানী কবিদের অনেকগুলি কাব্য তারা বাংলায় অনুবাদ করেন। এমনকি অনেকে তাদের আদলে কাব্য ও কবিতা চর্চা করেন। এখানে পীরের নির্দেশে গ্রন্থরচনার কথা অনেক কবিই বলেছেন। পনের শতকের কবি লিখেছেন:
শাহা বদরুদ্দীন পীর কৃপাকুল হরি।
শতমুখে সে বাখান কহিতে ন পারি।।
তাহান আদেশ-মালা শিরেতে ধরিয়া।
রচিলেন্ত মুজাম্মিলে মনে আকলিয়া।।
(সায়াৎনামা)
পীর শাহ দৌলার আদেশে কবি শেখ চান্দ লিখছেন:
ফতে মোহাম্মদ সুত শেখ চান্দ নাম।
গুরুর আজ্ঞায় পঞ্চালী রচে অনুপাম।।
কাছাছুল আম্বিয়া এক বিতাবেত শুনি।
পঞ্চালী বাঁধিয়া তাকে পুস্তকেত ভনি।।
মুলত মধ্যযুগের বাংলা কবিতা তাসাউফের চত্বরে ঘোরাফেরা করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় খৃষ্টান কবিরা যখন বাইবেলের মধ্যে ডুব দেয়, বাইবেল চর্চা করে এবং বাইবেল থেকে পথ নির্দেশনা নেবার চেষ্টা করে তখন এশিয়ার মুসলিম কবিরা ডুব দেয় তাসাউফের মধ্যে। তাসাউফের মধ্যে জীবন দর্শনের চিত্র অংকন করে। তাসাউফকে কুরআনের নির্যাস বিবেচনা করে। ফলে কুরআন থেকে পথ নির্দেশনা দেবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। বাংলা মধ্যযুগের কবিরা কুরআন ও ইসলামের নামে যা কিছু বলেছেন তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের চিন্তা থেকে নয়। বরং ইরানী সাহিত্যের মধ্যস্থতায় তাসাউফের জারক রসে সিঞ্চিত করে বলেছেন। এই প্রসংগে বলা যায় মওলানা রুমীর মসনবীকে বলা হয়েছে-
‘হত কুরআ দর যবানে পাহলভী’
মসনবী-ই-মানবী-ই মৌলভী
অর্থাৎ ‘পাহলবী তথা ফারসী ভাষায় মওলানা রুমীর মসনবীই হচ্ছে কুরআন মজীদ।’
অথচ অন্যদিকে ইমাম গাজ্জালী র. মওলানা রুমীর এই মসনবীর চিন্তা উদ্বৃত (সামা) গান ও নাচের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ কোনো গ্রন্থই কুরআনের সমান্তরাল হতে পারে না।
তাসাউফের চিন্তার জটিলতার কারণে পনের ষোল শতকের বাংলার কিছু মুসলিম কবি শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেন। তারা এটাকে শির্ক মিশ্রিত এবং মুসলিম জীবন ধারা থেকে বিভিন্ন মনে করতে পারেননি। আল্লাহ যে খালেস তৌহীদের কথা কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, শিরক ছাড়া অন্য সমস্ত গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন, সেই শিরক থেকে আমাদের জীবনকে যেমন মুক্ত রাখতে হবে তেমনি সাহিত্যও হবে তা থেকে মুক্ত।
আধুনিক পরিবেশ ও আধুনিক সাহিত্য
উনিশ শতক থেকে এদেশের সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। এ আধুনিকতার সম্পর্ক ইংরেজী সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় চিন্তার সাথে কবিতার আংগিকে কাঠামোয় এবং চিন্তায় যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি নতুন গদ্যভংগী রচিত হয়। উপন্যাস, প্রহসন, নাটক ইত্যাদি কথাসাহিত্যের একটি ধারা সৃষ্টি হয়। সমগ্র সাহিত্য জগতে যেন নতুন জোয়ার আসে। মুসলিম সমাজ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় মুসলিম সাহিত্যিকরা প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা ভাষার ওপর থেকে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রভাব ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে তাদের নিজেদের পৌরাণিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় বড় বড় প্রতিভার জন্ম হয়। যথার্থই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির উচ্চ সোপান অতিক্রম করতে থাকে।
এসময় মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে এগিয়ে আসেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। তিনি নতুন ভাষার ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে প্রথম মুসলিম সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর পরে শক্তিশালী লেখক হিসাবে এগিয়ে আসেন মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯ – ১৯৩১), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার সৈয়্যদ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ঔপন্যাসিক নজীবুর রহমান সাহিত্যরত্ব (১৮৭৮-১৯২৩), প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কবি শাহাদত হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কবি ও প্রবন্ধকার গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪), ইত্যাদি অসংখ্য শক্তিশী সাহিত্যিকবৃন্দ। তাঁরা সবাই নিজেদের সময় ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিকভাবে প্রবল। তাই সাহিত্য জগতে তাঁরা প্রতিবেশীদের তুলনামূলক উন্নতমানের সাথে সহাবস্থান করেও মুসলমানদের জন্য একটা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন।
এই সময় আগমন হয় বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬)। ভাষার ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক প্লাটফর্মের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি মুসলিম ঐতিহ্যে ফিরে যাবার সকল প্রচেষ্টা শুরু করেন। তাঁর প্রতিভা প্রতিপক্ষ প্রতিবেশীদের হৃদয়ও স্পর্শ করে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করে তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেন। বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংগীত তাঁর অমর কীর্তি। নজরুলের পরে কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৩) তাঁর সাহিত্যধারাকে আরো পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ফররুখ ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যকে পূর্ণরূপে বিকাশিত করেন।
১৯১৭ সালে বাশিয়ায় লেনিনবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লব হবার পর এর প্রভাব সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ শতকের জার্মান চিন্তাবিদ কার্লমার্কস ও ফেড্রারিক এঙ্গেলস ছিলেন এই বিপ্লবী চিন্তাধারার উদগাতা। তাঁরা অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবের ডাক দেন। আসলে কমিউনিস্ট ভাবধারা একটা অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম। একে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত করেন। একদল সাহিত্যিকের মাথায় শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তা এবং এই সংগে নিরীশ্বরবাদিতা ও ধর্ম আফিমের ন্যায় এই ধারণা বন্ধমূল করে দেন। এরই ভিত্তিতে তারা দুনিয়াব্যাপী একটি সাহিত্যের আবহ তৈরিতে মেতে ওঠেন। মাত্র সত্তর বছরের মধ্যে তারা বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও ব্যর্থ হয়ে যান। মার্কসবাদ একটা অলীক কল্পনায় পরিণত হয়। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যকে তারা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এখন কয়েক প্রজন্ম ধরে। তারা সাহিত্য থেকে আল্লাহকে বিদায় দিয়েছেন। সাহিত্যের পরতে পরতে শ্রেণী সংগ্রাম প্রবেশ করিয়ে একটা হিংসাত্মক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা মানবতাবাদের কথা বলেন। কিন্তু তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে সবচেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে মানবতা। তারা মানুষকে কোনো এক পর্যায়ে নিয়ে স্থিতিশীল করতে পারেননি। মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে কার কাছে আশ্রয় নেবে? এক আল্লাহকে ত্যাগ করলে অসংখ্য আল্লাহ এসে যায়। দেশ এক আল্লাহ, পাটি এক আল্লাহ, প্রেসিডিয়াম এক আল্লাহ- এভাবে ক্ষমতাধর প্রত্যেকেই এক এক আল্লাহ। এই স্বৈরাচারী আল্লাহদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা মার্কসবাদী সাহিত্যের নেই।
বিগত শতকের শেষার্ধব্যাপী এই মার্কসবাদী সাহিত্যের দাপাদাপি বাংলার মুসলিম সাহিত্য অংগণে অশনি সম্পাতের মতো অনুভুত হচ্ছিল। মুসলিম ঘরানার বহু সাহিত্যিক ইসলামী আদর্শবাদ ত্যাগ করে এদিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। মার্কসবাদের পতনের পর তাদের পালে আর হাওয়া বইছে না। তবুও তারা মার্কসবাদের মূল ভিত্তি সেক্যুলাবাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। অনেকে ইসলামী আদর্শবাদের আওতায় ফিরে আসছেন।
তবে ইসলামী আদর্শবাদও বিশ্বাসের নতুন বলয় সৃষ্টি করে ময়দানে নতুন করে জেগে উঠছে। আমাদের পূর্বসূরীদের বিগত ছ’সাতশো বছরের প্রচেষ্টা ও কর্মপ্রবাহ এ বলয়কে শক্তিশালী ভিত্তিদান করেছে। কুরআন ও হাদীস অবিকৃত থাকার এবং তাদের সাথে আমাদের আবেগগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ গড়ে ওঠার কারণে আজ সেখান থেকে পথনির্দেশ লাভ করা আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। ইসলামী সমাজ চিন্তা যেমন নতুন করে নব উদ্যমে বলীয়ান হচ্ছে তেমনি ইসলামী সাহিত্য চিন্তাও তার সাথে সমান তালে এগিয়ে যাবে।

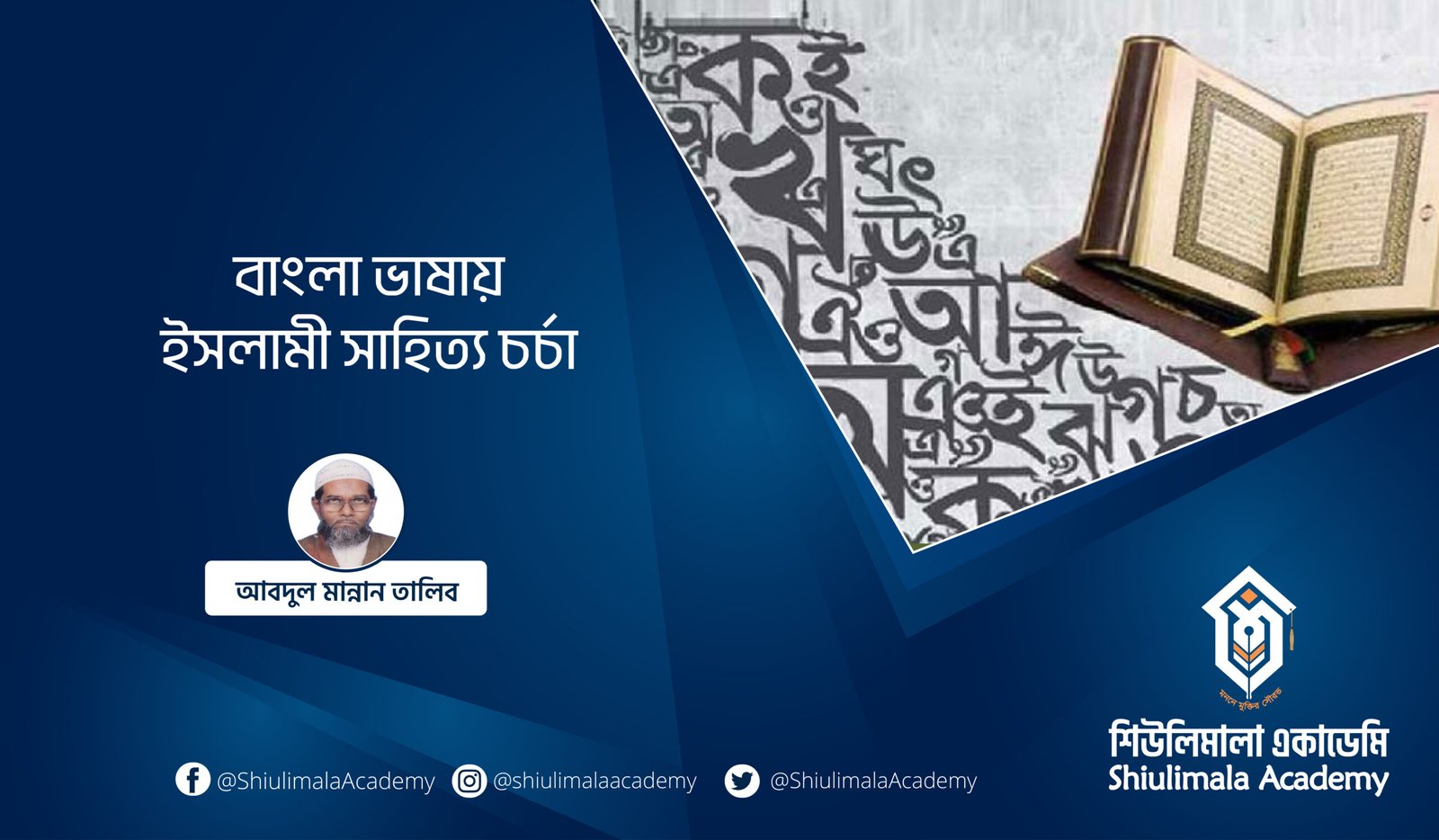

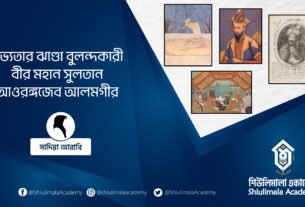
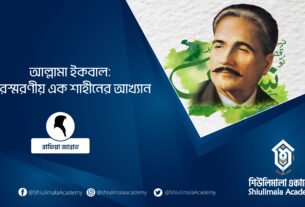

সাহিত্য ও ভাষা একটি জাতির জন্য ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা শরীরের জন্য রূহ। এত চমৎকার আয়োজনের জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা।