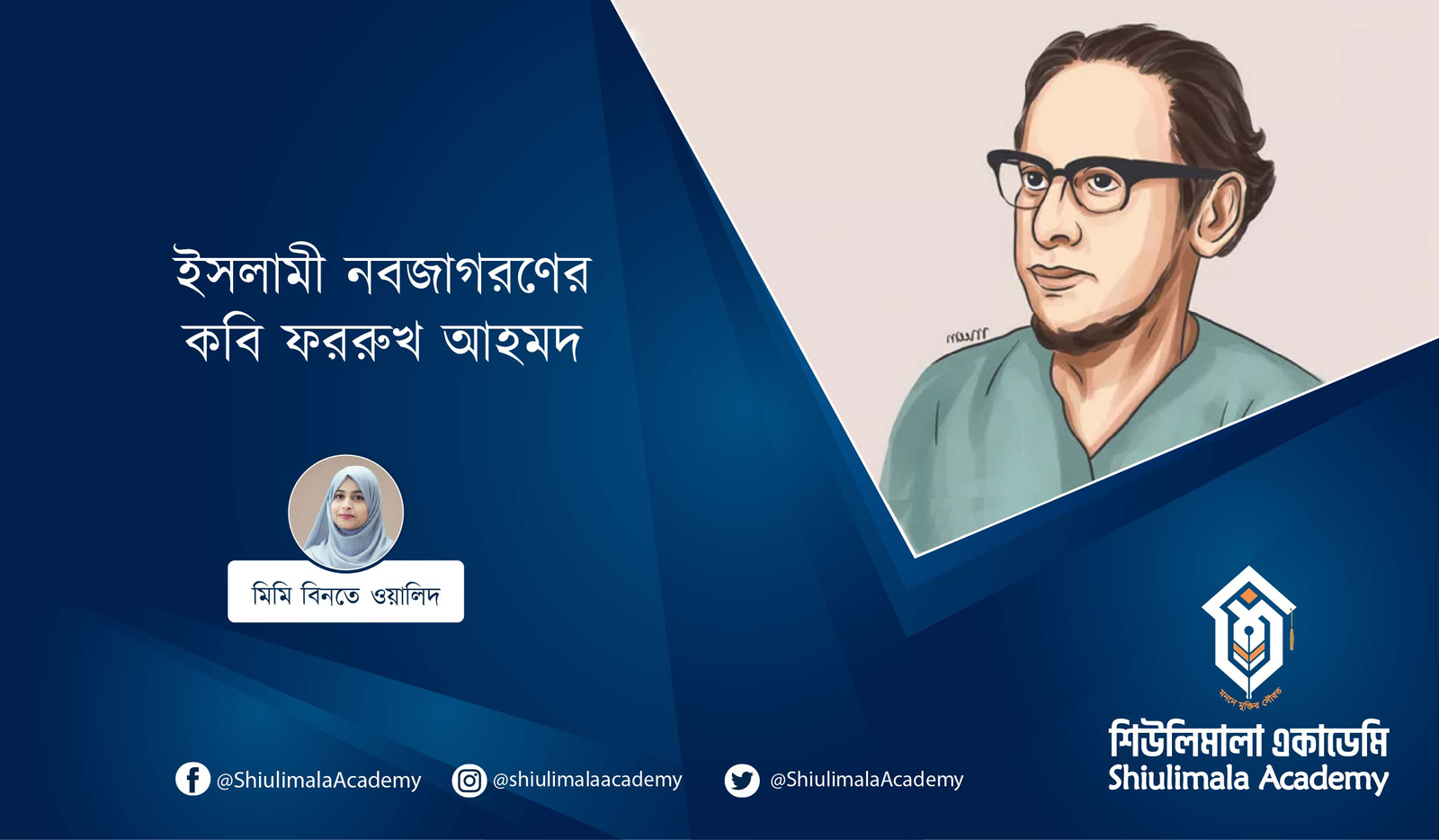কবি ফররুখ আহমদ ( ১৯১৮-১৯৭৪) যে সময় কলম ধরেছেন সে সময়ের একটি আলাদা তাৎপর্য আছে এবং কবি তাঁর সময়ের অন্যসব কবি, সাহিত্যিকদের থেকে দলছুট হয়ে যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে নতুন রঙ ও রসের সংযোজন করেছে আর কবিকে সম্ভাষণ করেছে, ‘মুসলিম রেনেসাঁর কবি’ অভিধায়।
কবি ফররুখ আহমদ তাঁর সমস্ত লেখা জুড়ে হক্বের তালাশ করেছেন। হক্ব হচ্ছে তাঁর মঞ্জিল। কবি এই সত্যে পৌঁছানোর জন্যই পাড়ি দিয়েছেন উত্তাল বা’র দরিয়া, দুর্গম গিরি, শুষ্ক মরু, মেঘাচ্ছন্ন নভ। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে হক্বের মঞ্জিল আলিঙ্গন করতে কবি নিজেই সজ্জিত হয়েছেন নাবিকদের পথপ্রদর্শক সিন্দবাদের ভূমিকায়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যটি কবির ছাব্বিশ বছর বয়সের টগবগে যৌবন উচ্ছ্বাসে প্রাণোচ্ছ্বল। ব্যক্তিগত পিছুটান থেকে বৈশ্বিক— তাবৎ শৃঙ্খলের উৎকট ঝঙ্কার পাশ কাটিয়ে কবি কান খাড়া করেছেন, কূলে প্রতীক্ষারত জুলুম জর্জরিত মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠে, যারা ইনসাফের আশায় পাড়ে জড় হয়েছেন।
কবি ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে যে বিশ্বব্যবস্থা প্রণীত হচ্ছিলো তাতেই ইসলামী সভ্যতা পতনের সমস্ত আয়োজন মহা বর্বরতায় সম্পন্ন হচ্ছিলো। কবি মনে-প্রাণে ইসলামী আদর্শকে ইনসাফ লাভের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে আকাঙ্ক্ষা করছিলেন কিন্তু বিশ্বব্যবস্থা অগ্রসর হচ্ছিলো সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী কায়দায়। ফলে কবি মুখোমুখি হয়েছেন সময় ও পারিপার্শ্বিকতার দ্বন্দ্বে। পুঁজিবাদী ভাগ-বাঁটোয়ারায় সমগ্র বিশ্বের সবুজ ক্ষেত্র যখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে রক্তিম হয়ে উঠেছে সেই সময়ই কবি পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যদিও সে বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় তবু যুদ্ধবিদ্ধস্ত আবহাওয়াতেই কেটেছে কবির শৈশব। বিশ্ব মোড়লরা পুঁজিবাদকে সুশৃঙ্খলভাবে অর্থাৎ নিরব ঘাতক হিসেবে পরিচালনা করার কায়দাকানুন তখনো রপ্ত করতে পারেনি বলে তৎকালে পুঁজিবাদের বিভৎস শরীর ছিল একেবারেই নগ্ন এবং কর্কশ কণ্ঠস্বর ছিল সরব। ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাংলা অঞ্চলের মানুষ যাদের যুদ্ধের সাথে দূরদূরান্তরের কোনো সম্পৃক্ততা নেই তারা স্রেফ মোড়লদের ইবলিশি হঠকারিতায় বলির পাঠা হয়েছে। ত্রিশ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের ছুতায় ইন্তেকাল করেছেন। কবি মূলত পুঁজিবাদী আগ্রাসনকে অনুভব করেছেন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, তত্ত্বজ্ঞানে লব্ধ বিশ্বদর্শনে। যা তাঁর ধারণকৃত আদর্শের সাথে প্রকাণ্ড সংঘাত সৃষ্টি করেছে।
উনিশটি কবিতায় নবজাগরণের ভাব ও ভাষার মিতালিতে কবি তাঁর ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেন। অখণ্ড ভারত অধিবাসী তখন ঔপনিবেশিক কারাভোগের প্রায় শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছে। সমগ্র কাব্য পরিভ্রমণ করে কবির মনোভাবের তিনটি রূপ উদ্ধার করা যায় :
প্রথমত, ঘৃণা এবং ক্রোধ। কবি তাঁর পারিপার্শ্বিক শোষণের সমস্ত চেহারাকে ঘৃণা করছেন। শোষণের জাঁতাকলের দিকে কবি অগ্নিবিস্ফোরক দৃষ্টিতে চোখ রেখেছেন। শোষণমূলক সভ্যতার কেবল গুটিকয়েক উপাদানকে কবি শয়তানের খামখেয়ালি বলছেন না বরং তিনি সমগ্র সভ্যতাকেই শয়তান হিসেবে আখ্যায়িত করছেন এবং বর্জন করছেন।
“ মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে আত্মদান,
তারি শোধ তুলে নাও হে জড়-সভ্যতা শয়তান!
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে করিতেছ পান,
ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ অম্লান, ”
(লাশ: সাত সাগরের মাঝি)
লাসের স্তুপে বিগলিত অভিশপ্ত নিখিলের ধ্বংস প্রার্থনা করেছেন।
দ্বিতীয়ত, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। শোষণের তীব্রতার মাঝেও কবি আশাবাদী হয়ে উঠছেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব কবি চিত্তে আশার সঞ্চার করেছে। উপনিবেশের বিদায় ঘণ্টাও কবি শুনতে পাচ্ছেন তখন। ইসলামী আদর্শে গঠিত পাকিস্তানি প্রজাতন্ত্রের আভাস কবির মঞ্জিল স্পর্শের গতিকে বেগবান করছে। কবি সমস্ত বাঁধা পদদলিত করে তাঁর আদর্শিক বন্দোবস্তের দিকে ছুটছেন। কবির এই অপ্রতিরোধ্য আশাবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে ‘ঈমান’। কবি বিশ্বাস করছেন, এ মঞ্জিলমুখী যাত্রায় আল্লাহ যাত্রীদের সাথেই আছেন। কবির এই ঈমান কেবল তাঁর সাহিত্যিক উপাদান নয় বরং তাঁর আত্মার অকৃত্রিম প্রেরণা।
“এবার যদি এ তাজী হয় বানচাল
তক্তায় ভেসে পাড়ি দেব কালাপানি,
হাজার জীবন হয় যদি পয়মাল
মানবনা পরাজয়!
ধরো অচপল আবার হালের মুঠি;
শেষ ঠেউয়ে আর ক’রব না সংশয়।”
(বা’র দরিয়ায়: সাত সাগরের মাঝি)
তৃতীয়ত, কবি প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সম্বোধন করেছেন। নবজাগরণ কবির কাছে মোহ নয়, ইউটোপিয়া নয়। পুনর্জাগরণের বাঁধাসমূহকে কবি স্বীকার করছেন, মানব স্বভাবের হেতুতে কবি কাবুও হচ্ছেন। কিন্তু কবিকে একেবারে পর্যুদস্ত করা যাচ্ছে না, কবি তাঁর পদক্ষেপকে আরো বেশি দ্রুতগামী করছেন। মোদ্দা কথা কবি, বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে নয় বরং বাস্তবতাকে মোকাবিলা করে করে অগ্রসর হয়েছেন।
“আজ নির্ভিক মাল্লার দল ছোটে দরিয়ার টানে,
পান করি সিয়া সুতীব্র জ্বালা কলুষিত বিয়াবনে;
হারামি মওত ঢাকে সারা মন, দেহ,
গলিজ-শহরতলীতে আবার জেগে ওঠে সন্দেহ;”
(সিন্দবাদ: সাত সাগরের মাঝি)
কবি উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হয়েছেন, শঙ্কিত হয়েছেন আবার নির্ভিক উৎচ্ছ্বাসে পাহাড় সমান ঢেউ পাড়ি দিয়েছেন। কারণ কবির মঞ্জিল আছে। এই মঞ্জিল হচ্ছে ‘হেরার রাজ-তোরণ’। ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ— যে জাগরণ নিপীড়িত বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মাঝে ইনসাফের সুখবর বয়ে আনবে।
“ এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠেছে দু’চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ…”
(সাত সাগরের মাঝি: সাত সাগরের মাঝি)
কবি তাঁর এই তিন মনোভাবকে আশ্রয় করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তাকে তাজা করে তুলেছেন।
একজন কবি হিসেবে, ইসলামী নবজাগরণের কবি ফররুখ আহমদ নবজাগরণের চেতনাকে বিষয় ও আঙ্গিক, দুই ভাবেই ধারণ করেছেন। বিষয়ের ক্ষেত্রে আবার ইসলামের প্রাথমিক যুগের নির্ভেজাল ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। প্রেরণা পুরুষদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।
১৯৫২ সালে প্রকাশিত ‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যগ্রন্থে কবি, রাসুল সা. এর বিপ্লবী জীবনের সবর, কুরবানী, ইস্তিকামাত প্রভৃতি গুণাবলি ছন্দবদ্ধ বাক্যে রূপায়িত করেছেন। চার খলিফাকে ভিন্ন-ভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপন করেছেন। হযরত আবু বকর রা. মধ্য দিয়ে একজন প্রকৃত বন্ধু এবং সহকর্মীর চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন। আবু বকর রা. ‘সওর’ পর্বতে বিষাক্ত সাপের ছোবলের তলে নিজের শরীর বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঘুমন্ত রাসুল সা. এর ঘুম যেন কোনভাবেই না ভাঙে সেজন্য দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা হজম করেছিলেন।
হযরত উমর রা. মধ্য দিয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রজা সাধারণের সাথে সাধারণ হয়ে মিশে যাওয়ার বৈশিষ্ট্যে আলোকপাত করেছেন। ওসমান রা. কে তাঁর দানশীলতা এবং পবিত্র কোরআনের সংকলক হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং হযরত আলী রা. কে বীর যোদ্ধা এবং জ্ঞানের দরজা হিসেবে হাজির করেছেন।
এছাড়া তাঁর কাব্যে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যক্তি ও ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে ভৌগোলিক নৈকট্যকে স্মরণ করিয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে বিশেষভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালিয়েছেন। গাউসুল আজম, মুজাদ্দেদ আলফেসানিকে পেশ করেছেন কবিতার ভাষায়।
মধ্যযুগে মুসলমানদের রচিত সাহিত্যের উল্লেখ তাঁর কাব্যের বিভিন্ন চরণে মেলে। তিনি কখনো হাজির করেছেন কবিকে, কখনো কাব্যকে, কখনো কাব্যের চরিত্র-পাত্রকে, কখনো আবার ঘটনাকে।
আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও কবি নবজাগরণের চেতনাকে সমুন্নত রেখেছেন। কাব্যে আরবী-ফার্সি শব্দের বিপুল সমারোহ ঘটিয়েছেন। এমনকি বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত, এমন অনেক শব্দকেও সসম্মানে ঠাঁই দিয়েছেন কবিতার শরীরে। প্রতীক হিসেবে নৌপথে সিন্দবাদ, আকাশ পথে স্বর্ণ ঈগলকে নিয়ে এসেছেন। আবার নবজাগরণকে বাংলা অঞ্চলের সাথে ঘনিষ্ঠ করতে কবি ‘মাঝি’ ব্যবহার করছেন। কারণ এ শব্দের সাথে আমাদের কুটুম্বিতা শাশ্বত কালের।