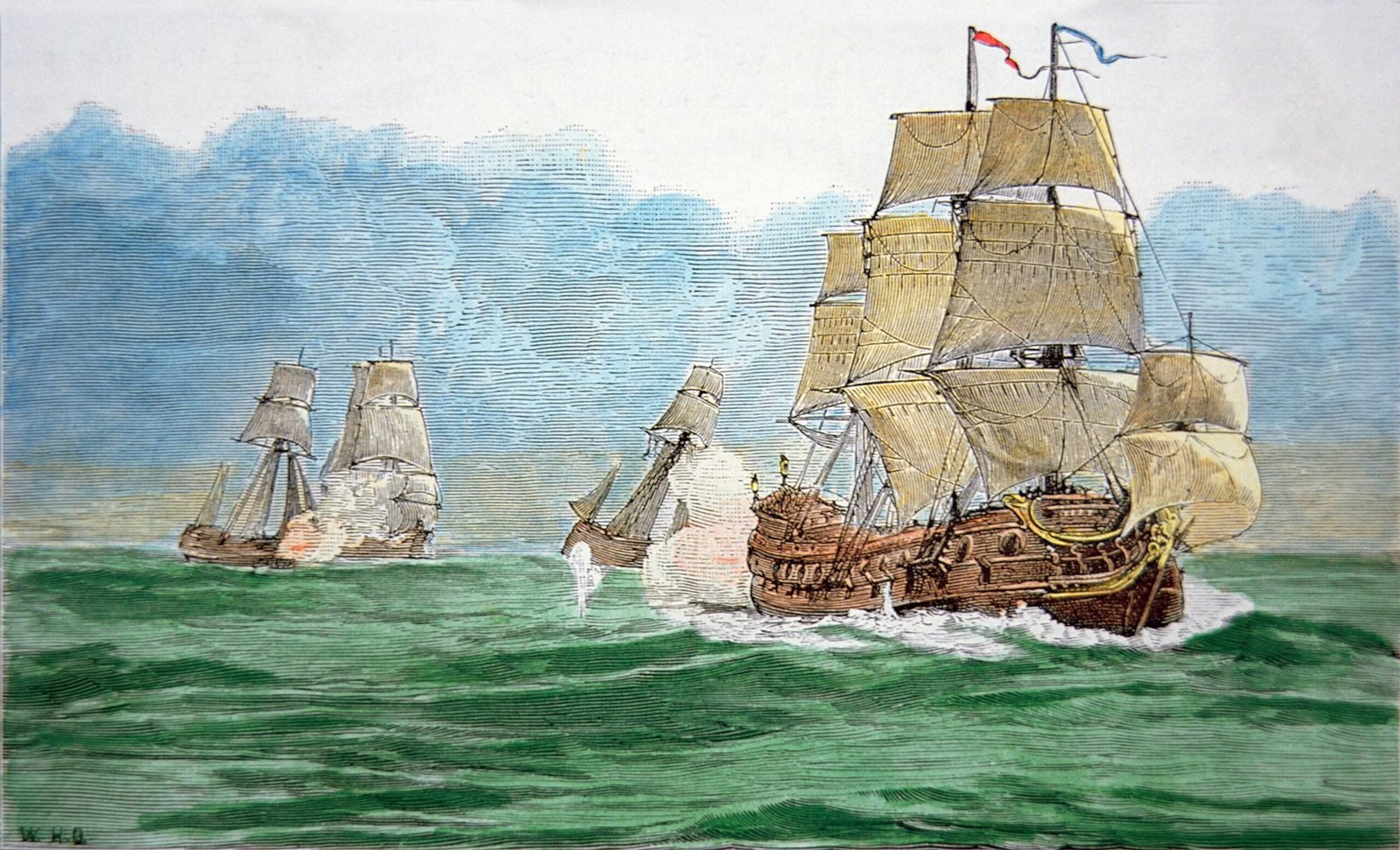নদী-সমুদ্র ও জলপথ—এই তিনের মিলনেই বহু জাতির ভাগ্য গঠিত হয়েছে, বহু সাম্রাজ্যের উঠানামা ঘটেছে। মানুষের রাজনীতি যত বদলেছে, জলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ততবারই ইতিহাসের চালচক্র ঘুরিয়েছে। ৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বে আলেকজান্ডার যখন এশিয়া মাইনরের পথে ১২০ জাহাজ আর প্রায় ৩৮ হাজার নৌ-সেনা নিয়ে যাত্রা করেন, তখন থেকেই স্পষ্ট হয়েছিল— সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ মানেই শক্তি নিয়ন্ত্রণ। আবার ১৫৮৮ সালে ইংরেজদের কাছে স্প্যানিশ আর্মাডার পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা যে আত্মবিশ্বাস পেল, তার ছায়া পড়ে দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলে। বেনিয়ার বেশে তাদের আগমন শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশকে ২০০ বছরের আধিপত্যের দিকে ঠেলে দেয়। ১৪৯২ সালের পর থেকে নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের নামে আরো বহু জাতি একই পরিণতির স্বীকার হয়েছে। এখনও অনেকে দাঁড়ানোর শক্তি ফিরে পায়নি। এই দীর্ঘ প্রেক্ষাপটের মধ্যেই বোঝা যায়, বাংলায় মোঘল নৌ-বাহিনীর উত্থান-পতন কীভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের টিকে থাকা বা ভেঙে পড়ার ছন্দ ঠিক করে দেয়। বিশেষ করে ১৫৭৬–১৭০৭ সালে জলপথে মোঘলরা যে সামরিক দক্ষতা দেখায়, আর ১৭০৭–১৭৫৭ সালে তা ক্ষয় হতে থাকলে গোটা কাঠামো কীভাবে নড়িয়ে যায়—সেই গল্পই এই আলোচনার মূল সুর। বাংলার পতনের পেছনে নৌ-শক্তির দুর্বলতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক; একে প্রধান কারণ বলা না গেলেও উপেক্ষার সুযোগ নেই।
বাংলায় নৌ-বাহিনীর আদি রূপরেখা
বাংলার ভৌগোলিক রূপই তাকে নিজস্ব জল-সমর কৌশল গড়ে তুলতে বাধ্য করেছে। নদীবহুল অঞ্চল হওয়ায় কেন্দ্রীয় দিল্লি সালতানাতের নিয়ন্ত্রণ এখানে সবসময় দুরূহ ছিল। তাই গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১২–১২২৭) স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, গঙ্গার তীর ঘেঁষে নৌবাহিনী সাজান এবং ইলতুতমীশের অভিযানে জলপথ দিয়ে বাধা দেন। বাংলায় নৌ-সামরিক ব্যবস্থার প্রথম উদাহরণ এটিই। ইওয়াজ খলজি শুধু নৌবাহিনীর পথিকৃত নন, সমগ্র খলজি শাসকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে সফল ও দীর্ঘস্থায়ী শাসক।
মোঘল প্রশাসনে নৌ-বিভাগের অবস্থান
মোঘল প্রশাসনিক কাঠামোয় নৌ-সামরিক ব্যবস্থার জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় দপ্তরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কারণ সাম্রাজ্যের রাজস্বভিত্তিক নীতি ছিল মূলত ভূমির ওপর নির্ভরশীল। তাই সামরিক শক্তির কেন্দ্রে ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক—স্থলবাহিনীই ছিল মোঘল সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি। স্পেন ও উসমানীয়রা যেখানে গভীর সমুদ্রনীতি গড়ছিল, মোঘলরা সেখানে ভূমিভিত্তিক সামরিক প্রযুক্তি উন্নত করছিল। তবে প্রাদেশিক প্রশাসনে ‘নাওয়ারা’ নামে নৌবিভাগ ছিল, আর এর প্রধানকে বলা হতো ‘মীরবহর।’
এই দুর্বল নৌ-শক্তির সীমাবদ্ধতা আকবর বাংলায় অভিযান চালাতে গিয়েই উপলব্ধি করেন। তাই তিনি বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেন—হাতি বহনকারী নৌযান নির্মাণ, দক্ষ মাঝি নিয়োগ, নদীপথের নিরাপত্তা, শুল্ক সংগৃহীত করা, সেতু ও বন্দর নির্মাণ ইত্যাদি।
বাংলার নৌ-সামরিক প্রয়োজন ছিল প্রধানত দুটি অঞ্চলে—গুজরাট-সিন্ধু এবং পূর্বের জলাভূমিপূর্ণ বাংলা। জানা যায় আকবরের আমলে স্থানীয় নৌযানের পাশাপাশি মোঘল নৌ-বহরে প্রায় ৩০০০ রণতরি ছিল।
মোঘল আমলে বাংলার নৌবাহিনী
ইতিহাসের সব চেয়ে অবহেলিত জায়গা হলো মোঘল নৌবাহিনী। যত ইতিহাস ঘটবেন না কেনো, বাংলার পালতোলা নৌকা নিয়ে যত ইতিহাস লেখা হয়েছে তত ইতিহাস যুদ্ধবহর গুলার জন্য লেখা হয়নি। সব জায়গায় মোঘল নৌবাহিনীকে দুর্বল বলা হয়েছে।
মোঘল আমলে বাংলা, গুজরাট ও কেরেলায় ছিল বিশাল সমুদ্র বন্দর। আর এইসব গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গুলোতেই মূলত যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করা হতো। অন্য বন্দর গুলোতে জাহাজ নির্মাণে ব্যবহার হতো ‘সেগুন’ গাছ। তবে বাংলা ইস্তেমাল করা হতো ‘সুন্দরী’ গাছের কাঠ। যার ফলে জাহাজগুলো লালচে রঙের হতো। ‘সুন্দরী’ কাঠের সাথে ইউরোপের ‘ওক’ বা ‘পাইন’ গাছের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে অন্যান্য কাঠের তুলনায় ‘সুন্দরী’ গাছের কাঠ ৪ গুনেরও বেশি সময় স্থায়ী হতো। জাহাজের কাঠের বন্ধন জোড়া লাগাতে ইউরোপীয়রা ব্যবহার করত ‘হাড়-কঙ্কালের’ আঠা। তবে বাংলায় ব্যবহার হতো শামুক গলিয়ে তৈরি করা আঠা। এতে জাহাজ নমনীয় থাকত, স্থিতিস্থাপক ছিল ও ক্ষয় রোধ করতে পারতো। লোহার উপরে তামার প্রলেপ লাগাতো যার ফলে মরিচা ও বার্নাকল (শেওলা) হতে জাহাজ হেফাজত থাকতো। বাঙ্গালা নদী মাতৃক হওয়ার দরুন তারা বংশক্রমিক জাহাজ বানাতে শিখে গিয়েছিলো। যার ফলে অন্যান্য ‘সুবাহ’র তুলনায় ‘বাংলা সুবাহ’য় সব চেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। বাংলায় অনেক ধরণের যুদ্ধবহর নির্মাণ করা হতো। সেগুলোকে মোট ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ
১. খেলনা (𝐅𝐮𝐬𝐭𝐚)
বৈঠা চালিত ছোট জাহাজ। মাঝে মাঝে পাল ব্যবহার করা হতো। জাহাজের দুইপাশে ১০-৩০ জন বৈঠা নিয়ে নৌকা বাইচ এর মতো বহর চালাতো। এই ফুস্তার প্রধান কাজ ছিল দ্রুত বার্তা পৌঁছানো আর রেকি দেওয়া।
২. সারেঙ্গ (𝐂𝐚𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥)
বাংলার নৌ বাহিনীর ছোট ও কার্যকারী যুদ্ধ জাহাজ। এগুলা ছোট পালতোলাবাহী জাহাজ (নৌকা নয়)। পাল ও বৈঠা উভয় ব্যবহার করা হতো। সারেঙ্গ (সারেং, সারেঙ), ঘুরাব (গুরাব), নাও, গড়াল ইত্যাদি নানা ধরণের বহর ছিল। জাহাজের সামনে এক-দুইটা বড় কামান থাকতো। আর থাকতো অসংখ্য তিরন্দাজ। যারা আগুনের তীর ছুড়তো আর পাল এ আগুন লাগিয়ে দিতো।
৩. কোসা (𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐲)
বাংলার সবচেয়ে কার্যকরী বড় যুদ্ধবহর। পাল ও বৈঠা সমন্বয়ে চলিত জাহাজে থাকতো ৩০-৯০ টি কামান। মুঘল আমলে ‘জালবাজ (জালবা)’ ও ‘জালিয়া’ নামক গ্যালি বহরের কথা পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০-৭০০ ফুট। প্রায় ৬০-৮০ জন লস্কর (ক্রু) বহন করতো। আরেক ধরণের বহরের নাম হলো ‘কোসা’। ছোট কোসা জাহাজে ৪০ জন লস্কর থাকতো, তবে বড় কোসা জাহাজে ১০০+ লস্করের জায়গা হতো। আঁকার হতো প্রায় ১০০০-১৫০০ ফুট লম্বা।
৪. গঞ্জ (𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐨𝐧)
মোঘল আমলে সব চেয়ে বড় যুদ্ধ জাহাজ। ৯৪-১২৪ টার মতো কামান বিশিষ্ট বহর, যা মূলত ইরোপিয়ান গ্যালিয়নের মতোই। বাংলায় একে বলা হতো ‘গন্জ’ বা ‘গন্জিনাত’। ৩০০-১০০০ মানুষের জায়গা হতো। ১৫০-২৫০ এর মতো লস্করের সাহায্যে চালানো হতো জাহাজটি। এইরকম জাহাজ মূলত রপ্তানি করা হতো। উসমানীদের (অটোম্যান) পরে ইংরেজরা এই জাহাজ কিনে নিয়ে যেত। শাহী বাণিজ্য, শাহী এনাম (উপঢৌকন) ও হজ যাত্রীদের জন্যও এই জাহাজ ব্যবহৃত হতো।
বাংলার নৌবাহিনীর পদবি
বাংলা নৌবাহিনীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে পদবীর (rank) ইতিহাস জানা খুবই কঠিন ও দুর্লভ। মুঘল নৌবাহিনীদের কোন শৃঙ্খলা ছিল না। বাংলায় হালকা শৃঙ্খলা থাকলেও প্রশাসনের ব্যাপক অভাব ছিল। তবুও শায়েস্তা খাঁ’য়ের আরাকান অভিযান আর ব্রিটিশদের সূত্র ধরে কিছু পদবির সম্পর্কে জানা যায়। যেমনঃ
• আমির-আল-বহর (আমিরাল>অ্যাডমিরাল)
আরবিতে আমির-আল-বহর মানে হল বহর গুলার শাসক। মোঘল আমলে আমিরের জায়গায় মীর যুক্ত হয়ে বলা হতো মীর-ই-বহর। ইউরোপে আমির-আল-বহর থেকে বহর কেটে নাম দেয় আমিরাল (পরে ডি যুক্ত হয়ে অ্যাডমিরাল)। মোঘল বাংলায় আরাকান আক্রমণের সময় মীর-ই-বহর ছিল ইবনে হুসাইন ও আবুল হাসান।
• দরিয়াসালার
এই পদবির অস্তিত্ব নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। এক দুই জায়গায় আমির-আল-বহর ইবনে হুসাইনকে দরিয়াসালার বলা হয়েছিল। কেউ বলে, সিপাহ-সালার মানে সেনাপতি যে মীর বখস’এর নিচে কাজ করে। তেমনি দরিয়াসালার মানে মীর বহরের নিচে কাজ করে। আবার আরেক দল বলে, শায়েস্তা খাঁ আরাকান আগ্রাসনের সময় এক বছরে ৩০০ জাহাজ তৈরী করে ছিল। এরমানে জাহাজ যেহুতু নেই তাই দরিয়াসালার মতো পদবি থাকার সম্ভাবনা থাকে না।
• দরিয়াদার/সারেংদার/সরদার
যে কেবলমাত্র একটা জাহাজের নেতৃত্ব দেয় তাকে ক্যাপ্টেন বলে। উসমানী আমলে ক্যাপ্টেনকে বলা হতো ‘কাপুতাঘ পাশা’। ফার্সিতে বলা হতো কাপুতান। ব্রিটিশ আমলে বাংলায় বলা হতো ‘কাপ্তান’। ঐতিহাসিক ভাবে কাপ্তান এর নাম পাওয়া দুস্কর। বর্তমান ইরানি নৌবাহিনীতে দরিয়াদার (দরিয়া = সমুদ্র) পদবি আছে দেখে অনেকে মতবাদ দিয়েছে। আবার, সরদার যেহুতু নেতার সমর্থক তাই অনেকে এটাও ব্যবহার করেছে। তবে ‘সারেংদার’ অনেকটা যৌক্তিক। কারণ উচ্চপদস্থ নাবিকদের বলা হতো সারেং। তাদের নেতা সারেংদার এটাই স্বাভাবিক। আবার বাংলায় সবচেয়ে কার্যকরী বহর ছিল সারঙ্গ। তাই ধারণা করা হয় সারেংদার হলো কাপ্তানের সমমানের পদবি। তবে ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত নয়।
• সারেং ও লস্কর
সারেং হলো উচ্চপদস্থ নাবিক। এদের কাজ খুঁটিনাটি দেখাশোনা করা। কেউ পালতোলা, কেউ বৈঠা, কেউ কামান, কেউ খাদ্য-রশন, কেউ নেভিগেশন ইত্যাদি কাজ তদারকি করে। আর সারেংদের নিচে ৫-২০ জনের লস্কর দল থাকে। কামান চালানো, তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপায়ে পড়া, জাহাজ পরিষ্কার করা, মেরামত সব এরাই করতো।
আগের যুগে, যে একটা জাহাজ পরিচালনা করতো তাকে সারেংদার (কাপ্তান) বলা হতো। একের অধিক হলে বলতো দরিয়াসালার (কমোডর)। আর যার নিয়ন্ত্রণে ২০-১০০ মতন জাহাজ থাকতো তাকে আমির-আল-বহর-বহর ডাকা হতো।
আরাকান বহরযুদ্ধে আমিরাল (আমির-আল-বহর-বহর) ছিল ২ জন। আমিরাল ইবনে হুসাইন আর আমিরাল আবুল হাসান। আমিরাল আবুল হাসানের নেতৃত্বে ছিল ১৪১ টি বহর আর দেড় হাজার সিপাহী।
মুঘল বাংলায় নৌবন্দর
মোঘল বাংলায় বড়-ছোট অনেক বন্দর ছিল। বড় বন্দর গুলার মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম আর সন্দ্বীপ ছিল অন্যতম। আর ছোট নৌবন্দর গুলো হলোঃ
হাতিয়া, শাহবাজপুর, সংগ্রামগড়, অংগরখালি, নারিকেল জিঞ্জিরা, দেয়াঙ, আলমদিয়া, যুগিদিয়া, হুগলি, ধুমঘাট, সোনারগাঁও, শ্রীপুর, ভাওয়ালগড় ইত্যাদি।
এখন প্রশ্ন হলো, বাংলায় শৃঙ্খল নৌবাহিনী থাকতেও মোঘল নৌবাহিনীকে দুর্বল বলা হতো কেন?
মুঘল আমলে সেনাবাহিনী এতোই শক্তিশালী ছিল যে তারা ভাবতেই পারেনি সমুদ্র থেকে কেউ এসে ভারত দখল করে নিবে। তবে যখনি মোঘল সতর্ক হয়ে যেত তখন নৌবাহিনী ব্যাপক শক্তিশালী করা হতো। উল্লেখ্য যে আরাকান যুদ্ধের সময় (১৬৬৬) বাংলার মতো সামান্য প্রদেশে নৌবহর ছিল ৩০০টি। আর সেই সময় (১৬৯৪) পুরা ব্রিটিশ সম্রাজ্যের রয়েল নেভিতে নৌবহর ছিল ৩০৩ টি। অতএব এটা বলার প্রশ্নই আসে না যে মুঘল নৌবাহিনী দুর্বল ছিল। তবে সঠিক যে প্রশাসনের অভাবে বাংলায় খুব কম নৌযোদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে এই ইতিহাস চাপানোর কারণে আমাদের মনে হয় মুঘল নৌশক্তি দুর্বল ছিল।
আকবরের বাংলায় জলযুদ্ধ
রাজমহলের যুদ্ধে ১৫৭৬ সালে আফগান আধিপত্য ছিন্ন হলেও ভাটির বিস্তীর্ণ জলাভূমি—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেটের নিম্নাঞ্চল—মোঘলদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। বারো ভূঁইয়া এবং আফগান বিদ্রোহীদের সংগঠিত প্রতিরোধে আকবরের পাঠানো সুবাদাররা একের পর এক ব্যর্থ হন। মুজাফফর খান নিহত হন, কুতুবুদ্দীন কোকা ও দুর্জন সিং যুদ্ধে মারা যান, কেউ কেউ ভয় ও হতাশায় বাংলা ছাড়েন।
এই দীর্ঘ প্রতিরোধের মুখে বাংলার ভাটি পরিণত হয় এক ধরনের Crescent of Fire-এ। আকবরের আমলে ঢাকায় টোডরমলের অধীনে ৭৬৮টি যুদ্ধজাহাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায়—নৌ-সামরিক শক্তি দুর্বল হলেও আয়োজন ছোট ছিল না। তবুও ঈসা খান ও তার ভূইয়া-বাহিনী, যাদের নৌ-বাহিনী ছিল প্রায় ৭০০-এর মতো, মোঘলদের বারবার রুখে দেয়। ব্রহ্মপুত্রের তীরে এগারো সিন্ধুর যুদ্ধে দুর্জন সিংয়ের ভীষণ পরাজয় তার প্রমাণ।
ঈসা খান ছিলেন সরাইলের জমিদার থেকে উঠে আসা এক অসাধারণ সংগঠক। তার রাজধানী ছিল কতরাব (বর্তমান রূপগঞ্জ) এবং সোনারগাঁও। বারো ভূঁইয়া নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ ইতিহাসবিদের ধারণা—এরা সংখ্যায় ১২-ই ছিলেন এবং মূলত ভাটিতেই সক্রিয় ছিলেন।
জাহাঙ্গীর—আর পরিকল্পিত নৌ-অভিযানের যুগ
বাংলার ইতিহাসে নৌ-শক্তির সবচেয়ে রূপান্তরমূলক অধ্যায় শুরু হয় ১৬০৮ সালে ইসলাম খান চিশতীর হাতে। তিনি বুঝেছিলেন, বাংলায় স্থলযুদ্ধ নয়—জয় সম্ভব জলের ওপর আধিপত্য স্থাপন করে। তাই তিনটি কৌশল নেন—
১) শক্তিশালী নৌ-বহর গঠন
২) পরাজিত ভূঁইয়াদের নৌযান ও সৈন্যকে মোঘল বাহিনীতে একীভূত করা
৩) রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে এনে ভাটিতে দ্রুত অভিযান পরিচালনা করা
ইহতিমাম খান ও তার পুত্র মির্জা নাথন এই যুদ্ধে মুখ্য ভূমিকা রাখেন। নথন ছিলেন প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ বাহরিস্তান-ই-গায়বী–এর লেখক। তাদের নেতৃত্বে ডাকচড়া, যাত্রাপুর, খিজিরপুর, কদমরসুল, কতরাব—সব দুর্গ একে একে পতন ঘটায় মোঘল নৌ-সেনারা। নথন সাত দিনে নতুন খাল খনন করে নৌযান সরিয়ে এনে অতর্কিত আক্রমণের যে কৌশল নেন, তা তখনকার সামরিক প্রযুক্তিতে অনন্য।
ঢাকা পৌঁছানোর পরে বুড়িগঙ্গার চাঁদনীঘাট হয়ে ওঠে মোঘলদের নৌঘাঁটি। পরে মুসা খান আত্মসমর্পণ করলে তার নৌকা পর্যন্ত মোঘল বাহিনীতে যুক্ত হয়। খাজা উসমানের বুকাইনগর দুর্গের পতনেও ব্যবহৃত হয়েছিল এই যৌথ নৌ-বহর। ত্রিপুরা অভিযানও নৌ-স্থল সম্মিলিত কৌশলের সাফল্যের ভালো উদাহরণ।
আওরঙ্গজেবের আমলে জলযুদ্ধের শিখর
শাহজাহানের সময় সীমান্ত রাজ্যগুলোতে বড় সাফল্য না এলেও মীর জুমলার যুগে পরিবর্তন আসে। কোচবিহার ও আসাম দখলে তিনি ৩২৩টি নৌযান নিয়ে অভিযান চালান—যেখানে ছিল কোশা, জলবা, গুরব, পারিন্দা, বজরা, পালিলা প্রভৃতি নানা ধরনের যুদ্ধনৌকা। গুরব নৌকা ছিল ভাসমান কামানবাহী যুদ্ধযান, যা চারটি কোশা নৌকা দিয়ে টেনে নেওয়া হতো।
আসামে শত্রুর ৬০০ নৌকা মোঘলদের আক্রমণ করলে পাল্টা প্রতিরোধে ৩০০ নৌযান ধ্বংস হয়। পরে প্রতাপ সিং চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মীর জুমলার নৌ-বিভাগের বার্ষিক ব্যয় ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ রুপি—যা তিনি ইউরোপীয় বণিকদের ওপর কর আরোপ করে তুলতেন।
মীর জুমলার পর বাংলার নৌশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেন শায়েস্তা খান। আরাকান-মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের তাণ্ডব থামাতে তিনি প্রথমে সন্দ্বীপ জয় করেন, তারপর কূটনীতি ও সামরিক শক্তি মিশিয়ে চট্টগ্রামকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করেন। তার পরিকল্পনায় ছিল—নৌবহর পুনর্গঠন, পর্তুগিজদের সঙ্গে সন্ধি, সন্দ্বীপ দখল, ডাচদের নিরপেক্ষ রাখা। ৩০০ নতুন জাহাজ নির্মাণ, পর্তুগিজদের ৫০টি জলবা সংগ্রহ, আর ডাচদের কৌশলে দূরে রাখা—সব মিলিয়ে ১৬৬৬ সালের কর্ণফুলী নদীর যুদ্ধে আরাকানিদের ১৩৫ নৌকা দখল হয়।
চট্টগ্রাম জয় ছিল মোঘল নৌ-শক্তির শেষ বড় সাফল্য।
১৭০৭–১৭৫৭: পতনের ছায়ায় বাংলার জলপথ
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নৌবাহিনী ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি হারাতে থাকে। যদিও ঢাকা নিয়াবতের অধীনে নাওয়ারা জায়গির ও ৭৬৮ রণতরির উল্লেখ পাওয়া যায়, কার্যকারিতা ছিল ক্ষীণ। পর্তুগিজ নাবিকদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা নৌবাহিনীকে মোঘলদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। ইংরেজ ও ডাচরা হুগলী ও বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াতে থাকে—বাংলার নবাবেরা সময়মতো এর প্রতিক্রিয়া করেননি। তাই ক্লাইভ-ওয়াটসনের ক্ষুদ্র নৌবহর সহজেই হুগলী দখল করতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।
তথ্যসূত্র :
১. বাঙলানামা ১ম সংখ্যা :
মোঘল আমলে বাংলার নৌ-শক্তি – আব্দুল্লাহ আল মামুন