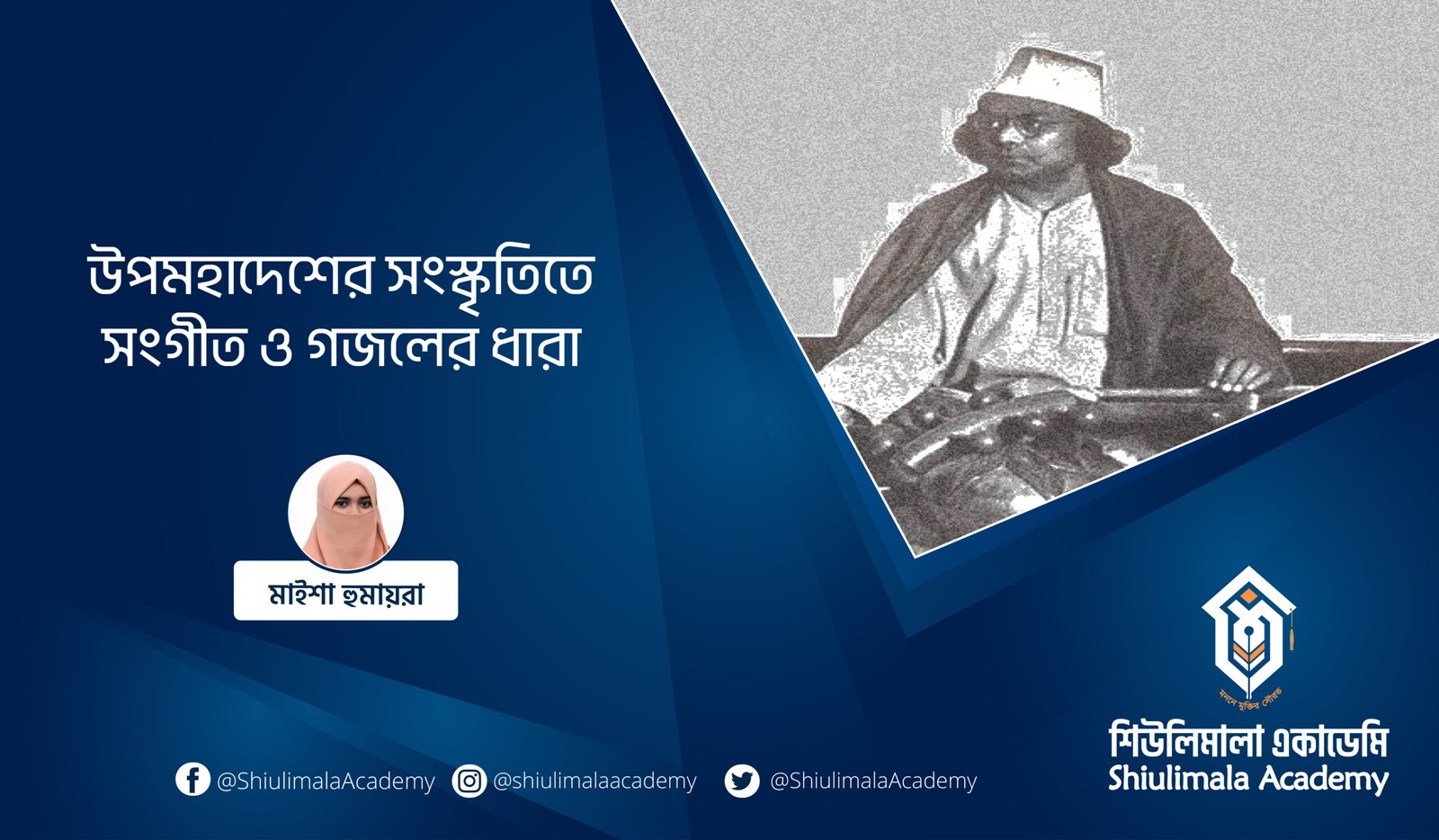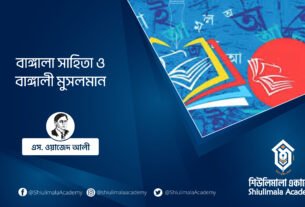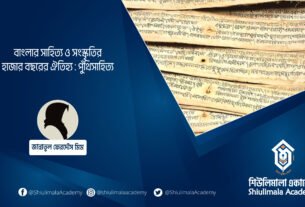সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির রূহের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্য মানবজীবনের ভাবনা, অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটায় ভাষার মাধ্যমে। অন্যদিকে, সংস্কৃতি হলো কোনো সমাজের জীবনযাপন পদ্ধতি, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপ। এটি একটি জাতির পরিচয় বহন করে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে একটি জাতির মানসিকতা, সামাজিক ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ। তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতি শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং একটি জাতিকে সচেতন, উদার ও মানবিক করে গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার।
সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক হলো “গজল”। গজল তার জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে ১৫ শতকের বেশি সময় ধরে। গজলের কথা বলতেই তার সাথে প্রাসঙ্গিক যে শব্দটা মাথায় আসে তা হলো গান। তবে গান ও গজল নিয়ে অনেকের মধ্যেই মতভেদ আছে। গান ও গজলকে অনেকেই একই মনে করে থাকেন। কিন্তু গান ও গজল এক নয়। মূলত সংগীতের এক একটি ধারা একেক ধরনের গান। আর সংগীত দ্বারা গীত, বাদ্যের সমাবেশকে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে, গজল আরবি সাহিত্যে উৎপত্তিপ্রাপ্ত কবিতার একটি রুপ এবং এটি ফারসি, উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। এখন জানা যাক, গান ও গজলের মধ্যে মূল পার্থক্য কী ? গান ও গজলের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, “প্রতিটি গজলকে গান হিসেবে গাওয়া যায় কিন্তু প্রতিটি গানকে গজল হিসেবে গাওয়া যায় না বা করা যায় না ”।
সাহিত্যসম্পদ
সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্যভিত্তিক রাজনীতির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন পাক ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশে অতীত থেকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অরক্ষিত নয়। বাংলা সাহিত্যের কোনো না কোনো পর্যায়ে পূর্বসূরিতা আরবি, ফারসি ও উর্দু সাহিত্য বনাম হিন্দি সংস্কৃত সাহিত্য প্রভাব ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়। ধর্ম,দর্শন ও ধর্মীয় সংস্কৃতি সূত্রে আরবি, ফারসি আমাদের স্বগোত্রীয়। পাশাপাশি উপমহাদেশ অর্থাৎ পাক ভারত ও ইরান এবং আরবের চিন্তাধারা আমাদের ভাব ও সংস্কৃতিতে অপূর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। মোঘল, পাঠানের পর এ দেশে আসে ইংরেজ। ইংরেজরা আমাদেরকে করেছে পাশ্চাত্যমুখী । ধীরে ধীরে এশিয়া বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যমুখী সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে আমরা ইউরোপ আমেরিকার সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ি। ফারসি ইতিহাস বলে, বিশ শতকের শুরুতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে ফারসি সাহিত্য ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। এরপর আমরা সম্মুখীন হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইরানের কবিতায় নতুন ধারা শুরু হয়। কতিপয় আধুনিক কবি নিমা ইউশিজের কবিতার আদর্শে পুরোনো ঐতিহ্য ভাঙতে শুরু করেন। এসব আধুনিক কবিরা অন্তমিলবিহীন ও ছন্দহীন কবিতা লেখা শুরু করেন। এ সময় মালাকাম খান এবং সাদি নাট্যকার পশ্চিমা ধারার নাটক লেখা শুরু করেন। আফগানিস্তানের বালখে, ১৩ শতকে, আবির্ভাব ঘটে জগদ্বিখ্যাত ফারসি কবি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমির। তারপর রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কারণে ২০ শতকের শুরুতে কাব্য সাহিত্য এবং পরবর্তী সময়ে গদ্যের বিকাশ ঘটে। কুর্দি কবি আহমেদ ই হানি রচিত ‘মেম ও জিন’ রোমান্টিক মহাকাব্য। উল্লেখ্য, আরবি, ফারসি ও কুর্দি সব সাহিত্যই সেসব জাতির সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে। এ সময় ফারসি ছিল ভারতীয় রাজভাষা। ফলে ফারসি শিল্পকর্ম সাহিত্য বিশেষত ‘গজল’ তথা রোমান্টিক কবিতা উর্দু হিন্দিসহ ভারতীয় সাহিত্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছিল।
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইসলামি সাহিত্যের প্রভাব বেশি। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মাধ্যেমে বঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে। এ ধারার সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম ‘আরব্য রজনীর গল্প’। গল্পগুলো মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রেম গল্পের কৌশল ব্যবহার করে রচিত। আরব্য রজনীর গল্পগুলো ১৮ শতকে পশ্চিমা সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ ফরাসি অনুবাদক আ্যান্টোইন গ্যালান্ড গল্পগুলো অনুবাদ করেছিলেন। তন্মধ্যে ‘আলাদীনের জাদুর প্রদীপ’, ‘আলিবাবা’ ও ‘চল্লিশ চোর’ এবং ‘নাবিক সিন্দাবাদ’ বিশ্বজুড়ে পাঠকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। এরপর ১৯ শতক পর্যন্ত তুর্কি সাহিত্য ফারসি ইসলামি ঐতিহ্যে পরিপুষ্টি লাভ করলেও দেওয়ানি সাহিত্য ছিল উচ্চতর সাহিত্য। যা উসমানীয় দরবারের চারপাশে বিকাশ লাভ করে। তবে এ শতকে তানযিমাত যুগের সঙ্গে তুর্কি সাহিত্যের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। ফলে পশ্চিমা ফরাসি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব শুরু হয়ে যায়। এছাড়াও বিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিম কবি লেখকদের সাহিত্যচর্চা উল্লেখযোগ্য। গোলাম মোস্তফা রচিত ‘বিশ্বনবি’ শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থগুলোর অন্যতম। তারপর আমরা দেখতে পাই, ইসলামি কবিতা ও গান গজল রচনায় কাজী নজরুল ইসলামের চিরস্মরণীয় অবদান।
পারস্যে গজলের জনপ্রিয়তা
সাহিত্যের বাকি সব ফর্মের তুলনায় গজলের বিবর্তন ও বিস্তারের কাহিনী অনেকটাই আলাদা। কারণ গজল যখন প্রথম আরব উপদ্বীপের বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন তা সমাদরের সঙ্গে ঠাঁই করে নিয়েছিল মধ্যযুগের স্পেনে, যেখানে গজল লেখা হতো একই সঙ্গে আরবি ও হিব্রু ভাষায়। অন্যদিকে ঐ সময়ে পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচলিত নানা ভাষায়ও গজল রচিত হচ্ছিল; যেমন হাউসা ও ফুলফুলদে। সেই সাথে এটাও মনে রাখার বিষয়, স্পেন ও পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলে রচিত গজল নিজস্বতা বা স্বকীয়তা ধারণ করার পরও শেষ অবধি আরবীয় মডেলের দিকেই ঝুঁকে ছিল। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পারস্যে গজলের প্রচলন ঘটে। সেখানে গজলের একটি স্বতন্ত্র তথা পারসিক ধারার সৃষ্টি হয়। তা হলো “রাদিফ “। রাদিফ হলো একটি গজলের প্রতিটি শেরের দ্বিতীয় পঙিক্তর শেষ শব্দটি একই রাখা, যা পুনরাবৃত্তিপূর্ণ অথচ দারুণ মনোমুগ্ধকর রীতি। উল্লেখ্য, প্রত্যেক গজলের দৈর্ঘ্য ০৭ থেকে ১৫ শেরে আবদ্ধ রাখার রীতিটিও পারস্যে প্রথম প্রচলিত হয়। পারস্য গজলের সুনির্দিষ্ট চারিত্র্য অর্জন ( গজলের প্রথম শের বা দ্বিপদীর মধ্যে এক ধরনের নিজস্বতার চকমকে পালিশ দেয়ার মাধ্যমে) হয়।
প্রথম ও প্রধানতম পারসিক গজল রচয়িতা হলেন আবদুল্লাহ জাফর রুদাকি। ৯ম শতাব্দীর শেষ দিকে তার আবির্ভাব ঘটে। তারপর অবশ্য আরো অনেক কিংবদন্তিতুল্য মহান গজল রচয়িতার আবির্ভাব ঘটে যেমন বারো শতকে সানাই গজনভি, ফরিদউদ্দিন আত্তার; তেরো শতকে সাদি শিরাজী ও জালালউদ্দিন রুমি; চৌদ্দ শতকে হাফিজ শিরাজী প্রমুখ। ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, পারস্যের গজল মূলত তার দুটি জোরালো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্ববাসীর কাছে একটি আলাদা আসনে ঠাঁই পেয়েছে। ঐ দুটি বৈশিষ্ট্য হলো :
১. বাণীর মধ্যে বিরাজমান তীব্র আধ্যাত্মিক নিমগ্নতা।
২. তীক্ষ দার্শনিক চিন্তা।
মূলত, ফারসি ভাষায় রচিত গজল মধ্য এশিয়া ও ভারত ভূখণ্ডেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। কেননা ঐ দুই এলাকায় তখন ফারসি ছিল শাসকদের ভাষা। ফলে শক্তপোক্তভাবেই গজল প্রাচ্যবাসীর কাব্যিক অভিব্যক্তি প্রকাশের এক আদি ও অকৃত্রিম রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় । এমনকি অন্যান্য ভাষায় যেসব ভিনদেশী কবি তখন লিখতেন, তারাও একটি পরিপূর্ণ কাব্যিক প্রকরণের সন্ধান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে ছিলেন পারস্যের গজলের দিকে।
গজলের ভারত জয়
গজলের জন্মস্থান আরবভূমি এবং যে ভূখণ্ডে এসে তা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল সেই পারস্য অঞ্চল হলেও গজল অসামান্য স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশেই। সেখানে বেশির ভাগ গজলই রচিত হয়েছে উর্দু ভাষায়। যদিও আমির খসরু তেরো শতকেই গজল লিখেছেন বলে তার রচনাবলি ঘাঁটলে প্রমাণ মেলে; প্রকৃতপক্ষে উর্দু গজলের আদিপর্বের রচয়িতা হিসেবে ষোলো শতকের শেষার্ধে গোলকণ্ডার কুতুব শাহি বংশের সুলতান মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ ও দাক্ষিণ্যাতের সতেরো শতকের কবি ওয়ালি আওরঙ্গাবাদিকেই ইতিহাসবিদরা চিহ্নিত করেছেন। ভারতে গজল রচনার ধারা ধর্ম, ভাষা ও বিষয়ের দিক থেকে বেশ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে এ অবধি বিবর্তিত হতে হতে এসেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে দক্ষিণাত্যে গজল রচনা প্রথম শুরু হলেও তা ক্রমে ক্রমে ভারতের নানা দিকে দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন গজল রচনা করাটা চটজলদি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি শহরগুলোর কবিদের মধ্যে গজল লেখা নিয়ে প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হয় রীতিমতো। ধীরে ধীরে পুরো ভারত ভূখণ্ডের চারদিকেই গজল ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারতের নানা প্রান্তে অনেক কবিই তখন গজল লিখেছেন ধুমসে, যা কিনা এখানকার গজলকে এক বৃহৎ পরিসরের দিশা দেখিয়েছিল এবং বহুবিস্তৃত বিষয়কে ধারণ করার শক্তি জুগিয়েছিল। আদতে মির্জা গালিব, মির তকি মির বা জওকের মতো কবিরা যেমন, তেমনি ওয়াজিদ আলী শাহ বা বাহদুর শাহ জাফরের মতো নিজভূমে পরবাসী নির্বাসিত রাজপুরুষেরাও উপমহাদেশে গজল রচনার ঐতিহ্যকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতীয় গজলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো বিভিন্ন ভাষার এবং একাধিক ধর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কবিরা একই সঙ্গে একই সময়ে গজল লিখেছেন, লিখে চলেছেন। এখন এটা বেশ স্পষ্ট যে বিভিন্ন ধারার কবিরা একত্র হওয়ায় গজলের পরিসীমা ভারতীয় উপমহাদেশে এসে বিষয়গত ও শৈলীগত—এ দুদিক থেকেই অনেকটা প্রশস্ত হয়েছে। আকারে-প্রকারে বেড়েছে, যা কিনা আরব বা পারস্য ভূখণ্ডে এতটা ব্যাপকরূপে ঘটা কঠিন ছিল। পারস্যে যেমন আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক কথকতাই ছিল গজলের মুখ্য বিষয়, প্রেমিকমনের বয়ানও সেখানে শেষ বিচারে আধ্যাত্মচেতনায় সমর্পিত—ভারতীয় উপমহাদেশের গজলের বিষয় ঠিক অতখানি গুরুতর বিষয়াবলিতে বন্দি থাকেনি। প্রেমিকের মনের হাহাকার থেকে শুরু করে রাজ্য হারানো রাজার দুঃখগাঁথা—উর্দু গজলের বৈচিত্র্য এমনই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবাহিত। এ কারণে গজল যেমন উপনিবেশপূর্ব ভারতীয় কবিদের মধ্যে কাব্যচর্চার ফর্ম হিসেবে জনপ্রিয় হচ্ছিল, তেমনি সংগীতের বাণীরূপেও এর জনপ্রিয়তা রাজদরবার কি অভিজাতগৃহ থেকে সংগীতপ্রেমী জনসাধারণের মাঝেও গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করেছিল। আবির্ভাবের পর থেকেই গজল এ উপমহাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের নানা ধাপ পেরিয়ে এখন অনন্যভাবে স্থায়ী এক ফর্ম হিসেবে গণ্য হচ্ছে।
পশ্চিমা কবিদের গজলপ্রীতির আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য দুনিয়ার কোনো সাহিত্যে গজল বা গজলের সঙ্গে তুলনীয় কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্যিক ফর্ম না থাকা সত্ত্বেও তা দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্যের একাধিক ভাষার কবিদের আকর্ষণের সামগ্রী বলে গণ্য হচ্ছে। অনেকেই পারস্যের গজলকে অনুকরণ করেন। অগস্ট গ্রাফ ভন প্লাতেন নামের এক জার্মান বহুভাষাবিদ আবার অনুকরণের পথে না গিয়ে পারসিক গজলের ছন্দ ও অন্ত্যমিল রীতিমতো মেনে গজল লেখার চেষ্টা করেছিলেন। তার লেখা দুটি গজলের সংকলন প্রকাশও পেয়েছিল। বিশ শতকে এসে স্পেনীয় কবি ফ্রেদরিকো গার্সিয়া লোরকা একাধিক গজল লিখেছিলেন gecelos শিরোনামের অধীনে। পরে সেগুলো তার কাব্যগ্রন্থ দিওয়ান ডেল তামারিত-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু জার্মানই অবশ্য নয়, অন্যান্য পশ্চিমা ভাষায়ও গজল রচনা ও অনুবাদের ঝোঁক দেখা গিয়েছে যেমন ইতালিয়ান, ইংরেজি ও ফরাসি। এসব ভাষায় গজলের অনুবাদ ও ভাবানুকরণের পাশাপাশি মৌলিক গজল লেখার একটি প্রবণতাও নজরে পড়ে। বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে ইংরেজিভাষী পরিমণ্ডলে গজল বড় রকমের গ্রহণযোগ্যতার দেখা পায়। বহু তরুণ কবিই তখন গজলের ফর্মে কবিতা লেখার চেষ্টা করছিলেন। মার্কিন মুলুকে আড্রিয়ান রিচ, জন হল্যান্ডার ও রবার্ট ব্লাই; কানাডায় জিম হ্যারিসন, ফিলিস ওয়েব ও ডগলাস বার্বার এবং অস্ট্রেলিয়ায় জুডিথ রাইটের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (তবে আরো অনেকের নামই বাদ পড়ে গেল)। তারা মূলত গজলচর্চা করছিলেন কাব্যসাহিত্যের ধারায় ভিন্ন রকম কিছু যোগ করার মাধ্যমে। আড্রিয়ান রিচের কথাই ধরা যাক; ১৯৬৯ সালে মির্জা গালিবের মৃত্যুশতবার্ষিকীর সময় তিনি প্রথম গালিবের গজলের সঙ্গে পরিচিত হন। তখন গালিবের গজল অনুবাদ করতে গিয়ে দ্রুতই তিনি এর প্রেমে মশগুল হয়ে পড়েন। পরে তিনি ‘গালিবের প্রতি শ্রদ্ধালেখন’ শিরোনামে ১৭টি গজল (নির্দিষ্ট গড়ন ও আঙ্গিকের বাইরে গিয়ে) লিখে আলাদা আলাদা লিফলেট আকারে ছাপিয়েছিলেন।
গজল রচনায় সফল একজন ব্যক্তি হলেন কাশ্মীরি বংশোদ্ভূত মার্কিন কবি আগা শহিদ আলি। তিনি মৌলিক গজলই লিখেছিলেন, অনুবাদ-ভাবানুবাদের পথে হাঁটেননি। কিন্তু গজল লেখার প্রচলিত ছন্দ ও বিন্যাসকে তিনি পরিত্যাগ করেননি। তার গজলের অনুভব নতুন, কিন্তু কাঠামোটি চিরায়ত। যারা গজলের নামে ‘ফ্রি ভার্স’ কবিতা লিখতে চেয়েছেন, তাদের সম্পর্কে তিনি হতাশা ব্যক্ত করে গেছেন। আগা শহিদ আলি মনে করতেন, কেউ যদি ‘প্রকৃত’ গজল লিখতে চায়, তবে এমনটা করা নেহাতই স্ববিরোধী কর্মকাণ্ড। আগা শহিদ আলি তাই নিজের গজল সংকলন Call Me Ishmael Tonight ও সম্পাদিত গ্রন্থ Ravishing Disunities: Real Ghazals in English-এ বেশকিছু ‘আদর্শ’ গজলের নমুনা উপস্থাপন করে গিয়েছিলেন।
কাওয়ালির জনক ও তবলার আবিষ্কার
“হযরত আমির খসরু” তার নাম আমরা কম বেশি সকলেই শুনেছি। মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন হযরত আমির খসরু। তবে তিনি শুধু সঙ্গীতজ্ঞই ছিলেন না, একাধারে ছিলেন কবি, গায়ক, সুফি, দার্শনিক ও যোদ্ধা। তিনি আমির খসরু হিসেবে পরিচিত হলেও তার মূল নাম ছিল আবুল হাসান ইয়ামিন আল-দিন মাহমুদ । আমির খসরুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি তাকে ‘আমির খসরু’ উপাধি প্রদান করেন। জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি মারা গেলে আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সময় আমির খসরু শিল্প-সাহিত্যে তার প্রতিভা পুরোপুরি বিকশিত করার সুযোগ পান। এ সময় তিনি সুলতানের বীরত্বগাঁথা নিয়ে ‘খাজিনাউল ফুতুহ’ নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি প্রধানত ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় গান ও কবিতা লিখতেন। অসাধারণ গান ও কবিতার মাধ্যমে তিনি ভক্তদের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন ‘তুত-ই-হিন্দ’ বা ‘ভারতের তোতা পাখি’ হিসেবে। তিনি ভারতীয়, ইরানী ও আরবি সঙ্গীতের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় করেছেন যে, তা গানের জগতে উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিসেবে খ্যাতি পায়। তার হাত ধরেই ভারতীয় উপমহাদেশে গজল সঙ্গীত ও কাব্যের প্রচার-প্রসার শুরু হয়। শুধু তাই- ই নয়, আমির খসরুকে “সেতার” ও “তবলা” বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কারক বলা হয়।
এছাড়াও বহুল জনপ্রিয় কাওয়ালি সংগীত আমির খসরুর নিজের উদ্ভাবিত সংগীত ধারা। ফলে তাকে ‘কাওয়ালির জনক’ বলা হয়। এটি ছিল দুই ভাষায় রচিত সংগীত, যেমন- ফার্সি ও হিন্দি। মূলত কাওল সংগীত গাওয়া হতো সুফি দরবেশদের মাহফিলে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার দরবারে আমির খসরু সাধারণত কাওয়ালি গজল গাইতেন যা ছিল সহজ, বোধগম্য ও জনপ্রিয়। কাওয়ালি শব্দটি এসেছে আরবি ‘কাওল’ বা ‘কাওলুন’ শব্দ থেকে, যার অর্থ কথা, বাক্য। বহুবচনে শব্দটি হয় ‘কাওয়ালি’। ভারতীয় উপমহাদেশে কাওয়ালি এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। ‘তারানা’ সংগীত, সংগীতের আরেকটি জনপ্রিয় ধারা যা আমির খসরুর নিজস্ব আবিস্কার। এটি হলো একপ্রকার শ্রুতিমধুর এবং দ্রুতগতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এর শব্দ তরঙ্গ শ্রোতাকে গম্ভীরভাবে আকর্ষণ করে- যদিও শব্দগুলো প্রায় অর্থহীন হয়। আমির খসরু পারস্য এবং ভারতীয় সংমিশ্রণে কয়েকটি নতুন ‘তান’ ও ‘লয়’ সৃষ্টি করেন। পারস্য সংগীতের ১২ পর্দা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়সমূহে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। জানা যায়, তিনি সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিশেষ আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করতেন। তৎকালীন সময়ে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিজয় লাভ করা ছিল অত্যন্ত মর্যাদার বিষয়। তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ নায়ক গোপালকে তিনি সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ বিজয় তাকে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের মর্যাদা প্রদান করে।
আমির খসরু কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন তালগুলোর মধ্যে ছিল-
সাওয়ার
ফিরুদাস্ত
পাহলোয়ান
জাট
কাওয়ালি
আড়াবৌতালি
জুমড়া
সুলকাকতা
খামসাহ ইত্যাদি।
বিশেষ ধরনের আরবি, ফার্সি ও ভারতীয় সংগীত ছাড়াও বিবিধ সংগীতশাস্ত্রে আমির খসরু শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সংগীতের যে যে ক্ষেত্রে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল, তা হলো-
কাওল
কানবালা
নাকশ
হাওয়া
তেরানা
সাহিলা ইত্যাদি।
আমির খসরুকে ভারতের প্রথম জাতীয় কবিও বলা হয়। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের একমাত্র মধ্যযুগীয় কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ, যার গান-কবিতার প্রভাব এখনও স্ব-মহিমায় বর্তমান আছে। উপমহাদেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংগীত সাধনায় তার অবদান চিরস্মরণীয়।
নজরুলের গানে ফারসি ও উর্দু গজল এর প্রভাব
আমরা কম-বেশি সকলেই জানি যে, শিশু বয়সে লেটোর দল দিয়ে নজরুলের সংগীত জীবন শুরু হয়। ওই অল্পবয়সেই তার সংগীত ও কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। মূলত ছেলেবেলায় তার বিচিত্র বিষয়ে গান রচনায় হাতেখড়ি হয়। ওই সময়ে পালাগান রচনা করতে গিয়ে নজরুল হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করেছেন। আসলে অল্প বয়সে পিতাকে হারাবার পর নজরুলের জীবন অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যায়। ১৯১৭ সালে নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য করাচি যান। সেইখানে নজরুলের নানান ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। এখানে ফারসি ভাষা ও গজলের সাথে তার পরিচয় ঘটে। এই বিষয়ে তার গভীর আগ্রহের ফলে তিনি এক পাঞ্জাবি মৌলবির কাছে ফারসি ও গজল বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। ফারসি গজল মূলত ঈশ্বর প্রেমের গান। পরে এতে নরনারীর প্রেমও বিষয়বস্তু হয়, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের ফারসি ও উর্দু গজলের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য। নজরুলের গজল উর্দু গজলের রসই গ্রহণ করেছে বেশি, তবে কিছু কিছু গজলে পারস্যের সুফি গজলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।
এই ধরনের একটি গজল—
তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন জানাও জানাও বেদিল প্রিয়ায়।ওগো বিজয়ী নিখিল হৃদয় কর কর জয় মোহন মায়ায়।।’
এইরকম আরেকটি গান— ‘রে অবোধ! শূন্য শুধু শূন্য ধূলো মাটির ধরা।
শূন্য ঐ অসীম আকাশ রংবেরং-এর খিলান-করা।।’
এই দুটি গানই পারস্যের সুফি দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রচিত গজল, কিন্তু এতে হিন্দুস্থানি রাগ-রাগিণীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম গানটি ভৈরবী রাগে রচিত, দ্বিতীয়টি বেহাগ রাগে রচিত। এই রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ নজরুলের গজলকে পারস্যের ঐশী বাণীসম্বলিত গজল থেকে আলাদা করেছে, বিশিষ্ট করে তুলেছে। পাশাপাশি নজরুলের অনেক গজলে আমরা নর-নারীর প্রেম বিষয়বস্তু হিসেবে লক্ষ্য করি। এখানে উর্দু গজলের প্রভাবই বেশি। যেমন—
‘নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জলমলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল।।’
এইরকম আরেকটি উদাহরণ— ‘এ আঁখি জল মোছ প্রিয়া ভোলো ভোলো আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে (ওগো) ঝরে যে ফুল আঁধারে।।’
এছাড়া নজরুলের গজলে আমরা আধুনিক বাংলা গানের রচনারীতিও লক্ষ্য করি।
যেমন নজরুলের একটি গান—
‘বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চলো লো গোরী’
এই গানটির কথায় গ্রাম্য ললনার কলসি কাঁখে পানি সংগ্রহের যে বর্ণনা তা আধুনিক বাংলা গানের আঙ্গিকে রচিত। আবার গানটি শুনলে আমরা বুঝতে পারি যে গানটি গজলের আঙ্গিকে সুরারোপিত।
তাহলে নজরুলের গজল আঙ্গিকের গানে আমরা তিনটি গুণ প্রত্যক্ষ করি।
প্রথমত : এতে পারস্যের সুফিবাদ প্রভাবিত ঐশী ভাবনা; দ্বিতীয়ত : উর্দু গজলের প্রভাবে নরনারীর প্রেম; তৃতীয়ত : কখনো কখনো দেখি গানের কথায় আধুনিক বাংলা গীত রচনার আঙ্গিক।
এইসব গুণের কারণে নজরুলের গজল বাংলা গানে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে, বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম জীবনের এক পর্যায়ে গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে যুক্ত হন। ততদিনে তিনি বাংলা গজল গানের সফল রচয়িতা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তখনকার নামী কণ্ঠশিল্পীরা নানা স্থানে তার গজল গাইছেন। এই সময়ে আকাশবাণী রেডিও স্টেশন স্থাপিত হলো। শুরু হলো বাংলা চলচ্চিত্র তৈরি। ফলে বাংলা গানের নতুন যুগ এলো। চলচ্চিত্রের গান ও রেকর্ড বিপণনের প্রয়োজনে বাংলা গানে হিন্দুস্থানি সংগীতের ঘনিষ্ঠতা কিছুটা শিথিল করে তার আবেদন আরও বৃহত্তর শ্রোতার কাছে বিস্তারিত করার প্রয়োজন দেখা দিল। ঠিক তখনই নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়ে তার সংগীত জীবনের এক অসামান্য সফল ও ফলপ্রসূ অধ্যায়ের সূচনা করেন। এই সময়ে বাংলা আধুনিক গানে নজরুলের ভূমিকা বিচিত্রমুখী, তার বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। নজরুলের আধুনিক গানের দুই একটা দিক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামোফোন কোম্পানি মানুষের ঘরে ঘরে রেকর্ড পৌঁছে দিতে আগ্রহী, তাই তারা গানের জনপ্রিয়তা বাড়াবার উদ্দেশ্যে সহজ কথায়, অপেক্ষাকৃত সরল সুরে গান রেকর্ড করার উদ্যোগ নিলো। নজরুল এই সময় কিছু প্রেমের গান রচনা করলেন, সেইখানে প্রেমের কথা এত সহজে এবং সরলভাবে তার গানে এলো যে, সেইসব গান দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ঐ সময় নজরুলের এইরকম দুইটা গান—
‘মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল।।’
আর
‘তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?
চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী বলে না তো কিছু চাঁদ।।’
গান দুটি যখন রেকর্ড করা হয়, সেই সময়ে এই দুটি প্রেমের গান সর্বাধিক শ্রুত বাংলা গানের অন্যতম ছিল। নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির সংগীত প্রশিক্ষক হিসেবে এই নতুন আঙ্গিকের গানের ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাকে সাহায্য করেন কিছু গুণী সুরকার। এদের অনেকের সুরে নজরুলের বহু গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।
যেমন কমল দাশগুপ্তের সুরে—
‘আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে
আধখানা চাঁদ নিচে’
এই নতুন ধারায় গানের সুর সরল রাখার ব্যাপারে গ্রামোফোন কোম্পানি আগ্রহী ছিল, তাই সেইখানে হিন্দুস্থানি সংগীতের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য ছিল। নজরুলের যেমন প্রতিভা তেমন তার হিন্দুস্থানি সংগীতে দখল এবং তার প্রতি অনুরাগ।
তার দুটি উদাহরণ—
‘চাঁদ হেরিছে চাঁদ–মুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনা–ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে।।’
আর
‘নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল
ফুল নেব না, অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল।।’
গ্রামোফোন কোম্পানির নিয়ম রক্ষা করে গান দুটি মনোগ্রাহী সরল সুরে রচিত, অথচ উচ্চাঙ্গ সংগীত জানা এবং বোঝা লোক মাত্রেই দুটি গানেই বাগেশ্রী রাগের প্রভাব লক্ষ্য করবেন।
আধুনিক গানে সুরকার আর গীতিকার বেশিরভাগ সময় আলাদা। নজরুল বিরল প্রতিভা গুণে দুই দিকেই পারদর্শী ছিলেন—তার গানে বাণী ও সুরের গভীর সমন্বয় তার আধুনিক গানকে উচ্চতর মাত্রা দিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের গানের সুর ও বাণী থেকে আজকের আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার ও সুরকাররা অনেক কিছু শিখতে পারেন। নজরুলের অসাধারণ প্রতিভার কারণে নতুন সুরকার ও গীতিকাররা নজরুলের গান আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন। কারণ ঐতিহ্যের ওপর ভর করেই আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।