০১.
আমাদের কাছে ঐতিহ্য বিষয়টিই যেনো জৌলুশ হারানো কোনো চরিত্র বা ইতিহাসের বেদনা বয়ে বেড়ানো কোনো ধ্বংসস্তূপ। সেটির মাঝে প্রাণ সঞ্চার করা বা পরম মমতায় লালন করে যাওয়া বা গৌরবের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রাখার বিষয়টি যেনো বেমানান। ফলে কতো ঐতিহ্য নিত্যক্ষয় হয়ে যায়, মানুষের চিন্তা-মনন থেকেও ধীরে ধীরে মুছে যায়, তার খবর কে রাখে!
প্রাচীন আমল থেকে এদেশের কৃষির পর গ্রামীণ অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ভিত ছিলো তাঁতশিল্প। তাঁতশিল্প হচ্ছে আমাদের এমনই এক ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের ভেতরেও আছে ক্ষয় হয়ে যাওয়া বা ক্ষয়িষ্ণু আরও ঐতিহ্য—জামদানি, মসলিন, টাঙ্গাইল শাড়ি ইত্যাদি। কত হাজার তাঁত বন্ধ হয়ে যায়, কতো লাখ তাঁতশ্রমিক বেকার হয়ে যান, কতো তাঁতি নিজের পূর্বপুরুষের ভিটা ফেলে ভারতে পাড়ি জমান, সেখানে নতুন করে সাজায় তাঁতঘর, তাতে কার কী আসে-যায়!
খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতকের সেই সময়ের চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া একাধিক পোড়ামাটির ফলকে শাড়ির সবচেয়ে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। শাড়ি ব্যবহারের নিদর্শন মিলে অষ্টম শতকের পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকেও। তবে তখনকার শাড়ি পরার ধরন যে এখনকার মতো ছিলো না, তা সহজেই অনুমেয়।
বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এবং হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ কাহিনীতেও স্থান পেয়েছে আমাদের টাঙ্গাইলের এই বস্ত্র, তথা তাঁত শিল্প। বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত রিহলাতে বাংলার তাঁতবস্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। এ ভ্রমণবৃত্তান্ত জানা যায় যে, সেই সময় সুতি কাপড় ছিলো বাংলার অন্যতম রপ্তানি পণ্য। সোনারগাঁ থেকে দিল্লির সুলতানের দূত হিসেবে চীন যাওয়ার পথে ইবনে বতুতা কিছু মুসলিম অধিবাসীর দেখা পান, যাঁরা বাংলা অঞ্চল থেকে উন্নত সুতিবস্ত্র এনে নানা জায়গায় বিক্রি করেন। ইবনে বতুতার এ ভ্রমণবৃত্তান্ত ছিল ১৪ শতকের। এ থেকে ধারণা করা যায়, এ অঞ্চলের তাঁতের বয়স কতো প্রাচীন।
০২.
তাঁত শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত ‘তন্তু’ থেকে। লাখো মানুষের জীবিকা নির্বাহের হাতিয়ার তাঁতেরও রয়েছে রকমফের। যেমন- পিট লুম বা গর্ত তাঁত বা খটখটি তাঁত, চিত্তরঞ্জন বা মিহি বা জাপানী তাঁত, ফ্রেম লুম, কোমর তাঁত। ভারতীয় উপমহাদেশের পুরাতন তাঁতযন্ত্র এই পিটলুম বা গর্ত তাঁত। বিখ্যাত মসলিন শাড়ী তৈরি করা হতো এই পিটলুমেই। এখন তৈরি হয় ঐতিহ্যবাহী জামদানীসহ অন্যান্য শাড়ি।
এই তাঁতের সাথে পরবর্তীতে যোগ করা হয় ফ্লাই শাটল, যা তাঁতপল্লীতে মাকু নামে পরিচিত। এই মাকু দিয়ে একটির পর একটি সূতা গেঁথেই তৈরি হয় টাংগাইলবাসীর স্বপ্ন, জন্ম হয় টাঙ্গাইল শাড়ীর। মাকু যখন দ্রুত গতিতে দুই পাশে বাড়ি খায়, তখন সৃষ্টি হয় খটখট শব্দের। সব সৃষ্টিই একই সাথে কষ্টের, বেদনার এবং আনন্দের। খটখট শব্দের জন্যেই এই তাঁতের এমন নাম- খটখটি তাঁত।
গর্তে বসানো লাগে না এমন খটখটি তাঁত শুধুমাত্র তাঁত নামেই পরিচিত। এটার আঞ্চলিক আপডেট ভার্সন হ্যান্ডলুম নামে পরিচিত। মর্টার বসিয়ে করা হয় সেমি অটোমেটিক টাইপ। চলে বিদ্যুতের সাহায্যে, ফলে এর উৎপাদন ক্ষমতাও বেশী। আবার সম্পূর্ণ অটোমেটিক তাঁত, পাওয়ার লুম নামে যেটি পরিচিত, সেটি চব্বিশ ঘণ্টাই উৎপাদনে সক্ষম।
শাড়িতে বিভিন্ন বাহারি নকশা করার জন্য পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিন। সহজ-সরল তাঁতীদের কাছে এই জ্যাকার্ড মেশিনই জ্যাকেট বা মালা। দিন দিন নকশা করার কাজে প্রযুক্তি তথা কম্পিউটারের ব্যবহারও বাড়ছে।
০৩.
বিভিন্ন গবেষণা এবং এই শিল্পের আদি ধারার সাথে সম্পৃক্তদের বয়ানে এই শাড়ির উৎপত্তিস্থল হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে উঠে আসছে পাথরাইল, নলশোধা, ঘারিন্দাসহ টাঙ্গাইলের এমন বাইশ-তেইশটি গ্রামের নাম। একসাথে এগুলোকে “বাইশগ্রাম” বলে চিহ্নিত করা হতো। এসব গ্রামই ঠিকানা ছিল তাঁতিদের। যাদের পদবি ছিল ‘বসাক’। বসাক সম্প্রদায়ের লোকেরাই টাঙ্গাইলের আদি তাঁতী। এরা আসলে দেশান্তরী তাঁতী। ঢাকা ও ধামরাই ছিল যাদের আদি নিবাস।
আরেকটা গবেষণায় আবার পাওয়া যায় যে, জগৎ বিখ্যাত মসলিন শাড়ি বুনতো এক সময় টাঙ্গাইলের তাঁতীরা। এ সবই এখন হারানো ঐতিহ্য। তবে মসলিন শাড়ি কালের প্রভাবে বা বিদেশী বণিকদের কূটচক্রান্তে কালের গর্ভে বিলীন হলেও সেই কালেরই সাক্ষী বা উত্তরাধিকার হিসেবে টিকে আছে টাংগাইলের জামদানী, বেনারসী ও তাঁতের শাড়ি।
ঊনিশ শতকে মসলিনের দুর্দিন শুরু হলে বা আবহাওয়াগতভাবে আরও ভালো জায়গার খোঁজে এরা বসতি স্থাপন করে টাঙ্গাইলে। পরবর্তীতে এ শিল্পের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পরলে বসাক ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও বসাক তাঁতীদের মতোই দক্ষ হয়ে ওঠেন।
সে যাই হোক, বসাক হিন্দুদের কোনো সম্প্রদায়ের জাত-পদবি নয়। বসে বসে তাঁতের কাজ করার কারণে তাঁদের পদবি বসাক হয়ে ওঠে। মূলত তাঁত বোনা হিন্দুদের জাত-পদবি হচ্ছে তন্তুবায়। ঐতিহাসিকভাবে টাঙ্গাইল শাড়ির তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের তাঁতিরা। পরে এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন মুসলিমরাও। মুসলমান তাঁতীদের বলা হয় জোলা বা কারিগর। তবে টাঙ্গাইলের পাথরাইল ইউনিয়নের হিন্দুদের বসাক সম্প্রদায়ের অবদান আলাদাভাবে উচ্চারিত হয়।
০৪.
১৮৫০ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে তৎকালীন ধামরাই এবং চৌহট্ট নামে দুটি গ্রামে মসলিনের উত্তরসূরি কিছু তাঁতি বসবাস করতেন। সন্তোষ, করটিয়া, দেলদুয়ারে জমিদারি পত্তনের সময় অন্যান্য পেশাজীবীদের পাশাপাশি ওই তাঁতিদেরও সেসব জায়গায় নিয়ে বসতি স্থাপন করা হয়। এসব গ্রামের মানুষেরা যে শাড়ি বয়ন করতেন তাই ‘টাঙ্গাইল শাড়ি’ নামে পরিচিতি লাভ করে।
১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বসাক সম্প্রদায়ের বড় অংশই ভারতে চলে যান। তাদের ভিড়টা বেশি হয় নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রাম এবং পূর্ব বর্ধমানের ধাত্রী গ্রাম ও সমুদ্রগড়ে। তাদের বদৌলতে নদীয়া ও পূর্ব-বর্ধমানে ‘টাঙ্গাইল শাড়ি’ পরিচিতি লাভ করে। এই বিদ্যেটা জানা ছিল বলে তাদের উদ্বাস্তু জীবনের বোঝা বইতে হয়নি।
পাকিস্তান পর্বে তো বটেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেও বসাক সম্প্রদায়ের পরিবারের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। স্বাধীনতার পর পুরো নলশোধা গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে তাঁত থাকলেও ২০১৪ সালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় মাত্র ২২টি পরিবার এই পেশায় যুক্ত আছে।
বর্তমান অবস্থা হলো, গত দুই-আড়াই দশকে হাজার হাজার তাঁত ইউনিট বন্ধ হয়েছে যায় টাঙ্গাইলে। ২০০৬ সালের এক প্রতিবেদনে উঠে আসে, টাঙ্গাইলের কালিহাতীর বল্লা–রামপুরে গত চার মাসে অন্তত পাঁচ হাজার তাঁত ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। তবে করোনা মহামারির ধাক্কা টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্পের মন্দা আরও বাড়িয়ে দেয়।
অতএব, এ কথা সত্য যে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কিছু তাঁতি বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলেন। তারাই সেখানে টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি শুরু করেন। কিন্তু শাড়ির নাম সেই টাঙ্গাইলই রয়ে গেছে। শাড়ির এই ইতিহাস তুলে ধরেছে খোদ ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা।
০৫.
বাংলার এ নিজস্ব পোশাক তৈরির ঐতিহ্যের রক্ষাকবচে প্রথম আঘাত আসে ব্রিটিশ আমলে। সে সময় ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের মেশিনে তৈরি কাপড়ের প্রসার ঘটে এ অঞ্চলে। তবে ১৯০৬ সালে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের মেশিনে তৈরি কাপড়ের বর্জনের ডাক দিলে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলার তাঁতবস্ত্র। সে সময়টাতে পুরান ঢাকাসহ সোনারগাঁ ও আশপাশের অঞ্চল থেকে তাঁতশিল্পের প্রসার ঘটে টাঙ্গাইলসহ আরও অনেক জায়গায়।
এই শাড়ি শুরুর দিকে জমিদারদের জন্য বোনা হতো। টাঙ্গাইলের পাথরাইল বাজার থেকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা মিহি সুতার কাপড় নিয়ে যেতেন। দেশ ভাগের পূর্বে মহানগরী কলকাতায় বসতো টাঙ্গাইল শাড়ির বাজার। স্টীমার বা জাহাজে চড়ে কলকাতায় যেতেন তাঁতীরা। কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীরা কিনতেন এই সব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের তাঁতের শাড়ী। বর্তমানে টাঙ্গাইলের বাজিতপুর ও করোটিয়াতে বসে টাঙ্গাইল শাড়ীর বড় বাজার।
মোদ্দাকথা, টাঙ্গাইল শাড়ির ঐতিহ্য অন্তত পাঁচশ বছরের। টাঙ্গাইলে তাঁতশিল্প প্রসার প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। টাঙ্গাইল তাঁতশিল্প দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্প। এটা মোটেও পার্শ্ববর্তী বর্ণবাদী দেশ ভারতের নিজস্ব কোনো পণ্য নয়। এর উৎপত্তি বাংলাদেশে। পরবর্তীতে এর কর্মকাররা তাদের যোগ্যতা নিয়ে যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই একইকার্য সম্পাদন করেছে। এর মানে তো এই নয় যে, মানুষ তাঁতের উৎপত্তিস্থল, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভুলে যাবে।
০৬.
অতএব, এখানে ভারতের কোনো অধিকার নেই যে আমাদের সম্পদ তারা নিজেদের বলে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করাবে, জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করবে। গত পহেলা ফেব্রুয়ারি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে টাঙ্গাইল তাঁত-শাড়ি নিজেদের বলে দাবি করেছে। ওই পোস্টে দাবি করা হয়েছে, “টাঙ্গাইল শাড়ি পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্ভূত একটি ঐতিহ্যগত হাতে বোনা মাস্টারপিস। এর সূক্ষ্ম গঠন, স্পন্দনশীল রং এবং জটিল জামদানি মোটিফের জন্য বিখ্যাত– এটি এ অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।”
পার্শ্ববর্তী দেশের এমন আচরণ মোটেও নতুন না। সুন্দরবনের মধু পর্যন্ত তারা নিজেদের বলে দাবী করেছে, জিআই পণ্য হিসেবেও স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে উঠে আসে জিআই পণ্যের কথা। তাহলে জিআই পণ্য কী?
কোনো একটি দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া এবং ওই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে সেটিকে ওই দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই পণ্য শুধু ওই এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও উৎপাদন করা সম্ভব নয়।
কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে পণ্যগুলো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে। ওই অঞ্চল বাণিজ্যিকভাবে পণ্যটি উৎপাদন করার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা পায়।
জিআই হলো ভৌগলিক নির্দেশক চিহ্ন যা কোনো পণ্যের একটি নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থলের কারণে এর খ্যাতি বা গুণাবলী নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত জিআইতে উৎপত্তিস্থলের নাম (শহর, অঞ্চল বা দেশ) অন্তর্ভুক্ত থাকে। জিআই (GI) এর পূর্ণরুপ হলো (Geographical indication) ভৌগলিক নির্দেশক। WIPO (world intellectual property organization) হলো জিআই পণ্যের স্বীকৃতি দানকারী প্রতিষ্ঠান।
কোনো নির্দিষ্ট স্থানের কোনো পণ্য খুব নামকরা হলে এবং সেই নামের ওপর বিশ্বাস করেই পণ্যটি কেনা ও ব্যবহার করার গুরুত্ব দিতেই এই জিআই সনদ দেওয়া হয়। প্রতিটি পণ্যের সঙ্গে সে স্থানের নাম যুক্ত করা হয়।
অতএব, টাঙ্গাইলের তাঁত-শাড়ি ভারতের নিজেদের পণ্য হিসেবে পৃথিবীর সামনে পরিচিত করাতে পারবে। নিজেদের মতো করে ব্যবসা করতে পারবে। শাড়ির উৎপত্তিস্থল হিসেবে নিজেদের পরিচিত করতে পারবে। অথচ, তা সম্পূর্ণ অনৈতিক, মিথ্যা, বানোয়াট।
০৭.
তাহলে একটু বর্তমান অবস্থার দিকে নজর দেওয়া যাক, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এর বিপরীতে কী অবস্থান নেওয়া হয়েছে।
গত ৪ ফেব্রয়ারি রোববার মতিঝিলে পাট অধিদফতরে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী বলেন, “ভারত টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই স্বত্ব নিয়েছে। এটি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমরা আমাদের টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই স্বত্ব সম্পর্কে যা ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে জরুরি বৈঠক হয়েছে। আর টাঙ্গাইল শাড়ি আমাদের ছিল। আমাদেরই থাকবে।”
গত ৫ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল শাড়ির ইন্টাল্যাকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটসের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় আপিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুস শহীদ। সেদিন বিকেলে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “টাঙ্গাইল শাড়ির রাইটসের বিষয়ে আপিলের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।”
এবং একইদিনে, টাঙ্গাইল শাড়িকে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতির জন্য যে সব আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে তা দ্রুত সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা। তিনি বলেন, “আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি ও নিবন্ধন দেয়া হবে। এজন্য অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে সংশ্লিষ্টদের। টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি ছাড়াও মধুপুরের আনারস, নরসিংদীর লটকন, সাগর কলা, ভোলার মহিষের কাঁচা দুধের দই ইত্যাদিসহ জিআই পণ্যের স্বীকৃতির জন্য যে সব আবেদন অনিষ্পন্ন আছে তা দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো গাফিলতি গ্রহণযোগ্য নয়।”
এর পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসক মো. কায়ছারুল ইসলাম বলেন, “ভৌগলিক দিক থেকে টাঙ্গাইল বাংলাদেশের একটি অংশ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে টাঙ্গাইল নামধারী যে কোন পণ্যই বাংলাদেশের পণ্য হবে। আমরা ইতোমধ্যে উপযুক্ত স্থানে মেইল করে আবেদনের সকল ডকুমেন্ট পাঠিয়েছি। এবং বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রণালয়ে হার্ডকপি জমা দেওয়া হবে।”
সর্বোপরি আমরা চাই, আমাদের পণ্য আমাদের নিকটই ফিরে আসুক। তাঁতশিল্পের সুদিন ফিরে আসুক। আমাদের ইতিহাস—ঐতিহ্য আমাদের নিকটই গচ্ছিত থাকুক।
লেখিকা: মিফতাহুল জান্নাত (শিক্ষার্থী, শিউলিমালা একাডেমি)।
তথ্যসূত্র…
০১. https://www.google.com/…/story/opinion/column/acpgtfam03
০২. https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-556681
০৩. https://www.google.com/…/bengali/articles/cjqj77872eko.amp
০৪. https://www.samakal.com/opinion/article/221154/গর্বের-ধন-%E2%80%8C’টাঙ্গাইল-শাড়ি’-বেহাত-হলো-কার-দোষে
০৫. https://www.somoynews.tv/news/2024-02-02/uTMvQ5DF
০৬. https://egiyecholo.com/article/tangail-saree
০৭. https://www.somoynews.tv/news/2024-02-04/4wI2vH58
০৮. https://www.somoynews.tv/news/2024-02-06/FwUHGWB9
০৯. https://www.somoynews.tv/news/2024-02-05/MJIK01VC
১০. https://www.somoynews.tv/news/2024-02-05/F4GXHAH9



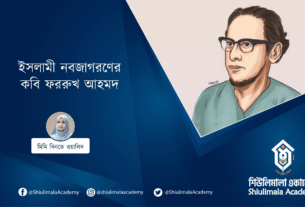


জাতির ঐক্য সেতুতে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নিজেদের ইচ্ছা, রুচি, অভ্যাস , অগ্ৰাধিকারে টিকিয়ে রাখতে হবে আমাদের ঐতিহ্য।