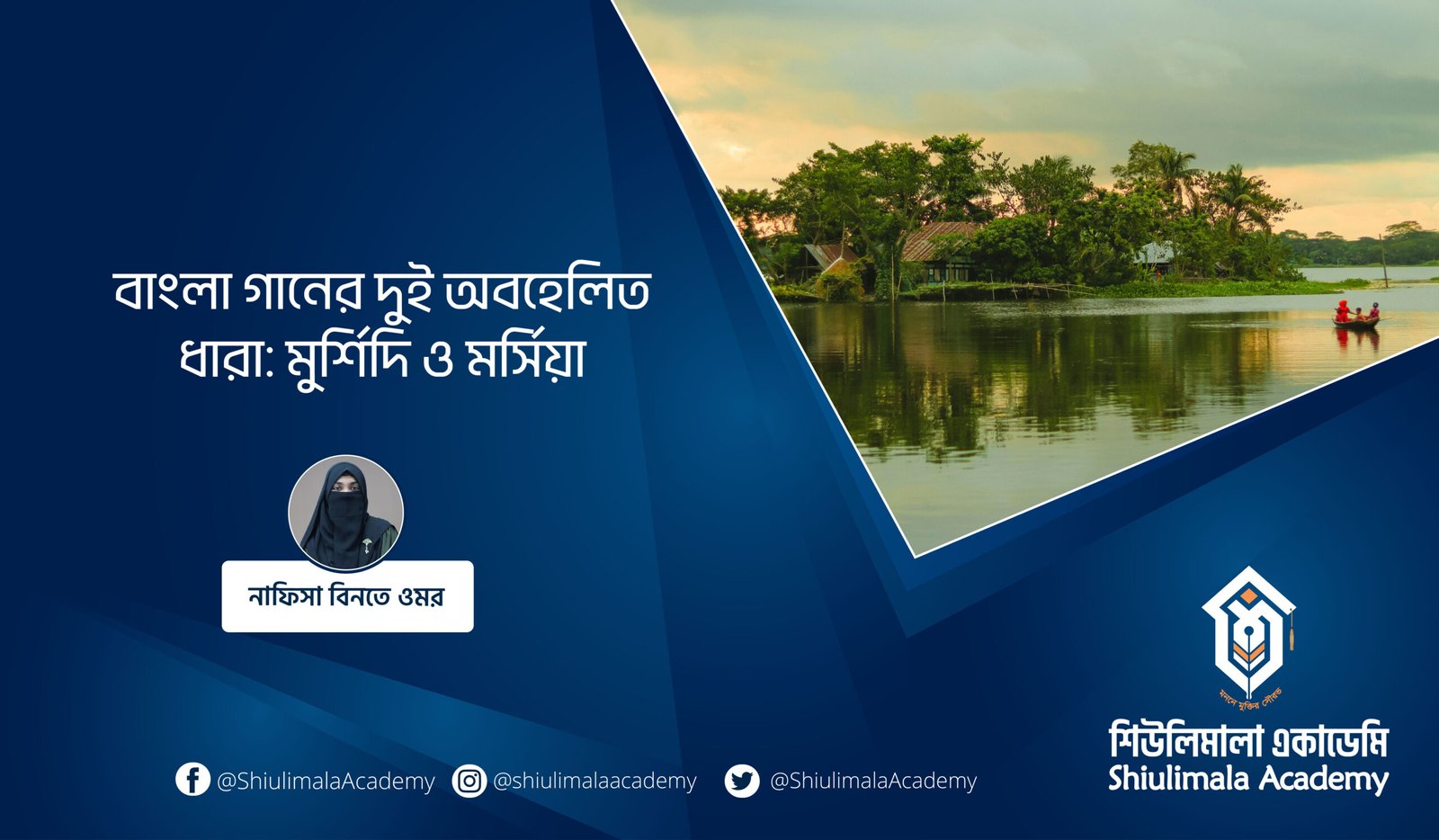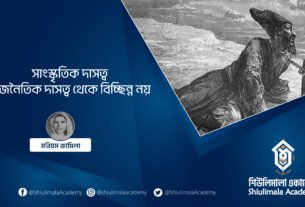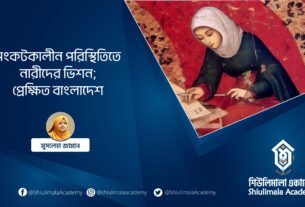সঙ্গীত মানবজীবনের এক চিরন্তন অনুষঙ্গ। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষ আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, ভক্তি-অনুরাগ ও আত্মঅনুসন্ধানের ভাষা হিসেবে গানকে বেছে নিয়েছে। মানুষের হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি, সমাজের সামষ্টিক চেতনা এবং ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক সাধনা—সবকিছুরই এক অপূর্ব প্রকাশভঙ্গি হলো সঙ্গীত। একটি জাতির সঙ্গীত সেই জাতির আত্মার প্রতিধ্বনি—যা তার সংস্কৃতি, বিশ্বাস, রুচি, ইতিহাস ও জীবনবোধকে ধারণ করে যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে চলে।
বাংলা গানও তেমনই এক বিশাল ঐতিহ্যভূমি, যার বুকে সহস্র রঙের সুরধারা প্রবাহিত—বাউল, ভাটিয়ালি, মারফতি, পালাগান, ভক্তিগান, জারি-সারি, পল্লীগান ইত্যাদি। এই সঙ্গীতধারারই দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অথচ আজ প্রায় বিস্মৃত অধ্যায় হলো—মুর্শিদি ও মর্সিয়া গান। এক সময় বাংলার গ্রামাঞ্চলে, মেলা-উৎসবে, আসর ও দরবারে এই গান ছিল জনমানুষের আত্মার আহার; আজ সেগুলো কালের গহ্বরে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।
মুর্শিদি গান:
‘মুর্শিদি গান’ মূলত এক প্রকার আধ্যাত্মিক লোকসঙ্গীত, যার উৎস সুফি দর্শনে। ‘মুর্শিদ’ শব্দটি আরবি এরশাদ ধাতু থেকে আগত, যার অর্থ—উপদেশ দেওয়া, পথপ্রদর্শন করা। যিনি মুরিদকে (শিষ্যকে) আধ্যাত্মিক সাধনার পথে পরিচালিত করেন, তিনিই মুর্শিদ। তাই, মুর্শিদের উদ্দেশে রচিত ভক্তিমূলক গান—যেখানে মুরিদ তাঁর পরম গুরুর প্রতি আনুগত্য, প্রেম, আরাধনা ও আত্মসমর্পণের কথা গেয়ে ওঠেন—সেই গানই মুর্শিদি গান নামে পরিচিত।
বাংলার সুফি-সাধক ও দরবেশগণ মধ্যযুগে ধর্মপ্রচার ও তরিকতের বিস্তারের পাশাপাশি এই সঙ্গীতধারাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। পূর্ববঙ্গের নদীবিধৌত অঞ্চলে বিশেষত ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও সিলেট জেলায় মুর্শিদি গান গভীরভাবে শিকড় গেড়েছিল। এর সুরে ভাটিয়ালি, বাউল ও মারফতি গানের মিশ্র ধ্বনি শোনা যায়—একদিকে নদীর একাকী মাঝির মতো গভীর বেদনা, অন্যদিকে আত্মার মুক্তির আকুলতা।
মুর্শিদি গানের মূল ভাব হলো—গুরুপ্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার সন্ধান। এই গানে শিষ্য মুর্শিদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। করুণ, ধীর ও গভীর লয়ে পরিবেশিত এই গানগুলো সাধারণত সন্ধ্যাকালে সুফি-সাধকদের মজলিস বা দরবারে পরিবেশিত হতো। ‘সারিন্দা’, ‘দোতরা’, ‘একতারা’ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের কোমল সুরে এই গানগুলোর বেদনামাখা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।
কিছু বিখ্যাত মুর্শিদি কবি ও তাঁদের গানের উদাহরণ:
মুর্শিদি হোসেন – চিত্ত কারে দেবে ওগো প্রাণের সুখ
মুর্শিদি আলী – শুনেছি মানুষ যার বাণী
মুর্শিদি শাহারী – আমি মাটির মাসে একটা পানি
এইসব গানে ধ্বনিত হয় মানুষের আত্মার ক্রন্দন, স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত প্রাণের আকুতি এবং মানবজীবনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অসীমের সন্ধান।
মর্সিয়া গান: শোক ও আত্মত্যাগের সঙ্গীত
‘মর্সিয়া’ শব্দটি এসেছে আরবি রিসা (رثاء) থেকে, যার অর্থ শোক প্রকাশ বা বিলাপ। ইসলামী ঐতিহ্যে মর্সিয়ার উৎপত্তি মূলত বীরত্বপূর্ণ বা করুণ মৃত্যুকে স্মরণ করে লেখা শোকগাথা থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে কারবালা প্রান্তরের করুণ ইতিহাস—ইমাম হোসেন (রাঃ) ও তাঁর পরিবার-সহচরদের আত্মত্যাগ—এই ধারার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।
বাংলা সাহিত্যেও মুসলিম কবিরা এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন মর্সিয়া গান—যা কখনও কারবালার বেদনাকে ধারণ করে, কখনও মানবজীবনের নশ্বরতা, মৃত্যু ও ত্যাগের অর্থকে ব্যাখ্যা করে। এ গানের সুরে আছে ক্রন্দন, কিন্তু সেই ক্রন্দন দুর্বলতার নয়—বরং সত্য, ন্যায় ও ত্যাগের মহিমা প্রচারের এক জাগ্রত সুর।
গ্রামীণ সমাজে এক সময় মর্সিয়া গান ছিল শোকের মজলিস, মাহফিল ও বার্ষিক ধর্মীয় সমাবেশের প্রধান অংশ। পল্লির সাধারণ মানুষ মর্সিয়ার মাধ্যমে কারবালার বীরত্বগাঁথা জানত, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিধ্বনি শুনত।
কিছু বিখ্যাত মর্সিয়া গীতিকার:
হোসেন সরকার – আমার মারা গেছে জীবন
কান্তা বাইল – আমি যে তার মর্সিয়া, তুই যে আছিস কোথায়
গল্প গান – আমি তোমার মত থাকতে পারতাম না
এই গানগুলো ধর্মীয় আবেগ, করুণরস ও মানবিক চেতনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে—যেখানে মৃত্যু এক পরিসমাপ্তি নয়, বরং আত্মত্যাগের মহিমান্বিত প্রতীক।
মুর্শিদি ও মর্সিয়া—দুটি ধারাই বাংলা মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এই গানগুলো কেবল ধর্মীয় গীতিই নয়; এগুলো ছিল সমাজ-সংস্কৃতির আয়না। একদিকে মানুষকে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা দিয়েছে, অন্যদিকে জীবনের দুঃখ, মায়া, নশ্বরতা ও মানবপ্রেমের গভীর উপলব্ধি জাগিয়ে তুলেছে।
কালের প্রবাহে, মানুষের রুচি ও বিনোদনের ধারা বদলে গেছে। আধুনিক প্রযুক্তি, বাণিজ্যিক সঙ্গীত ও ডিজিটাল বিনোদনের চাপে এই ঐতিহ্যবাহী গানগুলো আজ প্রায় হারিয়ে গেছে। এক সময় যেসব আঙিনায় সন্ধ্যার আসর বসত, আজ সেখানে বাজে যান্ত্রিক সংগীতের তীব্র আওয়াজ।
তবু এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, মুর্শিদি ও মর্সিয়া গান আমাদের আত্মার গান—যেখানে নিহিত আছে বাঙালি মুসলমান সমাজের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান, মানবিক বেদনা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের চেতনা। এই গানগুলো পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা মানে আমাদের সাংস্কৃতিক শিকড়কে পুনরায় জীবন্ত করা।
এই প্রাচীন ধারাগুলোকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এখনই উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সঙ্গীত বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর উচিত—মুর্শিদি ও মর্সিয়া গান সংরক্ষণ, পুনরায় রেকর্ডিং এবং একাডেমিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া।
এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই গানগুলোকে প্রচার করা, তরুণ শিল্পীদের উৎসাহিত করা, এবং আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সাথে প্রাচীন সুরের সমন্বয়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করা—এসব উদ্যোগই পারে এই দুটি ধারা পুনর্জীবিত করতে।
কারণ সংস্কৃতি কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, এটি জীবন্ত উত্তরাধিকার।
যতদিন মুর্শিদি ও মর্সিয়ার সুর বাংলার বাতাসে ভেসে বেড়াবে, ততদিন আমাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের শিকড় অটুট থাকবে।