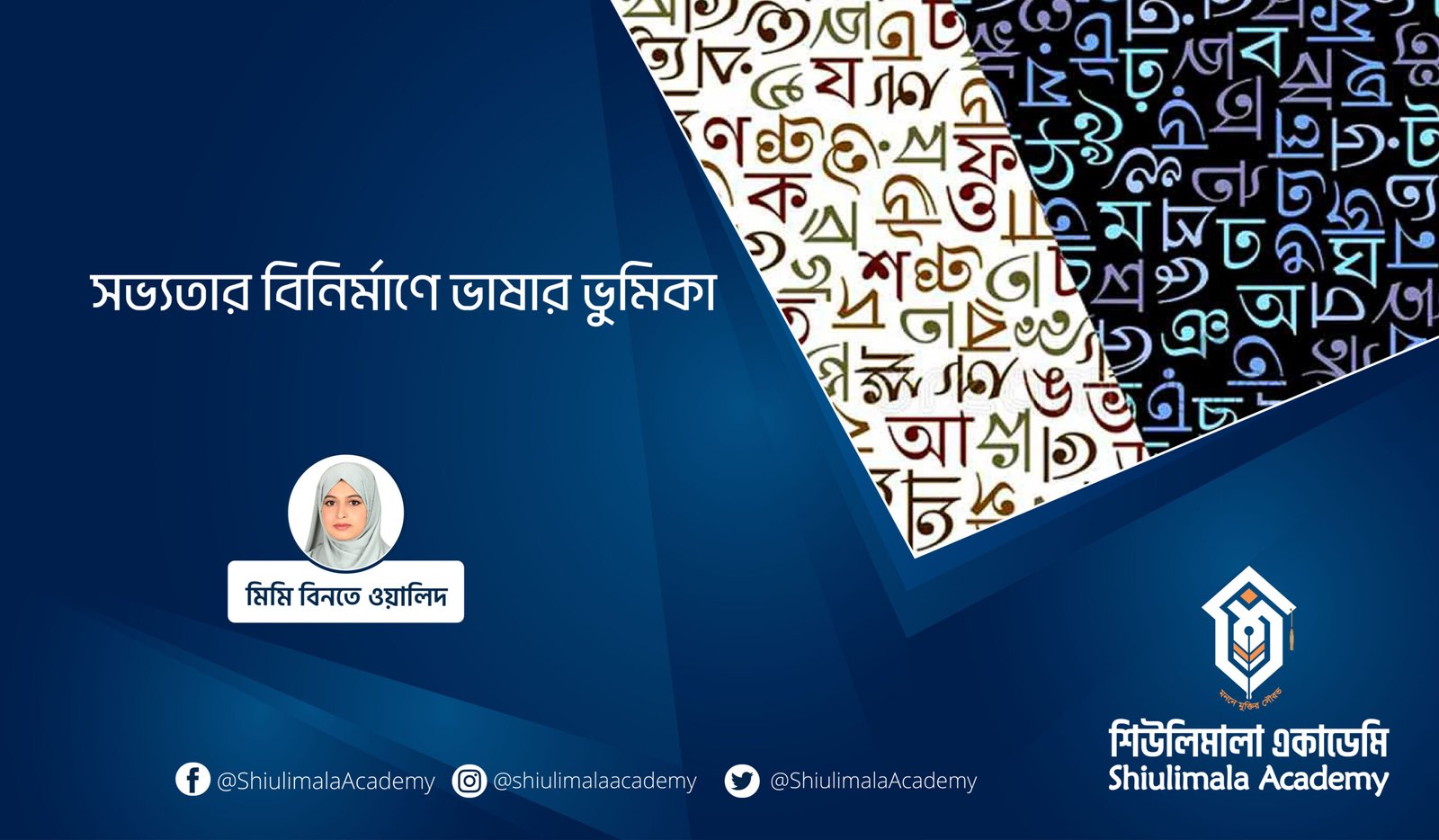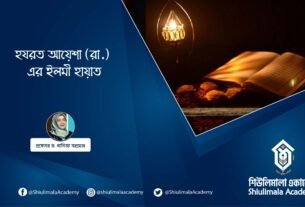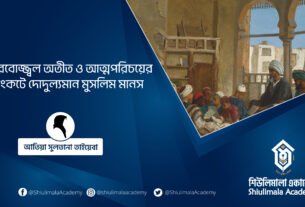সভ্যতা বিনির্মানের ক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠীকে ভাষা, ধর্ম, ভৌগোলিক অবস্থানসহ আরো কিছু মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয় এবং সভ্যতা বিনির্মানের সফর শুরু হয় সমাজের রূহকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। উল্লিখিত অনুসঙ্গসমূহ স্থান, কাল ভেদে বৈচিত্যপূর্ণ হওয়ায়, এমন কিছু শাশ্বত , সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক যা সকল সমাজের ভিন্নতাকে পরিগ্রহ করে। আমরা যেহেতু বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে সভ্যতার আলাপ তুলছি, সেহেতু বাংলা ভাষা এবং প্রায় নব্বরই শতাংশ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় পরিচয় হিসেবে দ্বীনে ইসলামে সভ্যতা বিনির্মানের সম্ভাবনা ও সক্ষমতার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া জরুরি। সেই সাথে সমাজের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য এ দুটি অনুসঙ্গে কীভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে সে আলাপ উত্থাপনও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।
বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় আট হাজার ভাষা, প্রায় দশ হাজার ধর্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা ভূখণ্ড রয়েছে যা বৈচিত্র্যময় সব সমাজজীবন গড়ে তুলেছে। বিশেষ কোনো অঞ্চল থেকে সমাজকে বিশ্লেষণ করলে সে বিশ্লেষণ কেবল সেই অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞান হিসেবে আটকে থাকার সম্ভাবনা যেমন থেকে যায় তেমনি সমাজের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের কারণে এ সমাজবিজ্ঞান অল্পকালই প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে। ইবনে খালদুন তাঁর ইলমুল উমরান তত্ত্বে এই সীমাবদ্ধতাসমূহ পরিত্যাগ করে কিছু মূলনীতি হাজির করেছেন যা শাশ্বত ও সর্বজনীন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ , ‘আল মুকাদ্দিমা’ র প্রথম অধ্যায়ে তিনি তুলে ধরেছেন, একটি জীব সত্তা হিসেবে মানুষ কীভাবে অন্য মানুষের সাথে বসবাস করে। মানুষ যে একত্রে বসবাস করে এটি মানুষের ইচ্ছার আওতাভুক্ত কোনো বিষয় নয় বরং এটি একটি অপরিহার্য ঘটনা। কারণ মানুষ যদি তার পাশের মানুষকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে নিজের অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ইবনে খালদুন এ বিষয়কে তুলে ধরেছেন এভাবে :
আল্লাহ মানুষকে একটি প্রজাতি হিসাবে সৃষ্ট করেছেন এবং মানুষ যেন এভাবেই টিকে থাকতে পারে সেজন্য মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আল্লাহ তায়া’লা একটি ‘অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নীতি দান করেছেন’। আর এই নীতি মানুষের অন্য কোনো পরিচয়ের ধার না ধেরে কেবল প্রজাতি হিসেবে অপরের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। আর এভাবেই মানুষকে সমাজবদ্ধ হিসেবে পরিচালনার প্রথম ধাপ আসাবিয়্যাত তথা সংহতি হিসেবে কাজ করে।
এশিয়া, ইউরোপ , আফ্রিকা- পৃথিবীর যে প্রান্তেই সমাজ গড়ে উঠুক না কেন, আসাবিয়্যাত প্রাণ ভ্রমরার ভূমিকা পালন করে। মজার বিষয় হলো, সংহতির বড় একটি অংশ ভাষার দখলে কারণ সংহতি কেবল ধারণের বিষয় নয়, প্রকাশেরও বিষয়। একটি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যাবহারের ক্ষেত্রে যত বেশি আখলাকের নজরানা পেশ করবে তাদের আসাবিয়্যাত তথা সংহতি ততবেশি মজবুত হবে। ভাষা সংহতি প্রকাশের ক্ষেত্রে যত বেশি পারঙ্গম হবে, সভ্যতা বিনির্মানের ক্ষেত্রে সে ভাষা ততবেশি সক্রিয় হয়ে উঠবে। বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ধর্ম নিরপেক্ষতার জোয়ার আসলেও বিশ্বাসের দলাদলি এক মুহূর্তও অনুপস্থিত থাকেনি কারণ এরই মধ্যে অসংখ্য মতবাদ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে এবং এগুলো বিশ্বাস দ্বন্দ্বের কাজা কাফফারা পূরণ করে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নফলের বিপুল আয়োজন ঘটিয়েছে। একই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারীদের সাংঘর্ষিক অবস্থান, আসাবিয়্যাতকে মারাত্মকভাবে জখম করেছে। এক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ‘আখলাকের মুখাপেক্ষীতা’ আসাবিয়্যাতের জখমে অব্যর্থ মলমের ভূমিকা পালন করতে পারে।
ইবনে খালদুন দ্বিতীয় মূলনীতি হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন , সমাজ গঠনের জন্য এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন যা মানুষের অভিযোজনের ক্ষেত্রে উপযোগী হবে। এ জন্যই তিনি বলছেন, মরুভূমি বা বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে উমরান তথা সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ এসব স্থানে প্রকৃতিক আনুকূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকালে নদী, সমুদ্র , সমতল ভূমি , পাহাড়-পর্বতের অসাধারণ মেলবন্ধন দেখতে পাই। এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য শুধু আবহাওয়া জলবায়ুই নয় বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, উপমা, অলংকারকেও অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে।
ইবনে খালদুন সামাজিক অস্তিত্বের তৃতীয় মূলনীতি হিসেবে নবুয়্যতকে যুক্ত করেছেন। নবুয়্যত আল্লার পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রাপ্ত এমন এক শক্তিশালী চেতনা যা সেই পয়গাম্বরের অনুসারীদের রক্ষা করতে সর্বদা উজ্জীবিত রাখবে। আর এই মূলনীতির বিশেষ তাৎপর্য হলো, এটি আসাবিয়্যাতের পরিসরকে ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারও বাইরে নিয়ে বিস্তার ঘটাতে সক্ষম। সর্বশেষ নবুয়্যতপ্রাপ্ত রাসুল, মুহাম্মাদ সা. এর উম্মত হিসেবে আমরা উম্মাহর অংশীদার হতে পারি। ইবনে খালদুনের তৃতীয় মূলনীতিতে যে উম্মার ধারণা উঠে এসেছে, তা আমাদের বাংলাভাষীদের সভ্যতা বিনির্মানে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়। কারণ, বাংলা ভাষা মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার যে সংস্কার করানো হয় সেখানে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা মোড়লের ভূমিকায় ছিলেন এবং তাঁরা বাংলা ভাষায় প্রায় ষাট ভাগ সংস্কৃত শব্দের কৃত্রিম প্রবেশ ঘটান। অন্যদিকে সাহিত্য চর্চায় মুসলমানদের আকাল বাংলা ভাষাকে সাম্প্রদায়িক রূপ লাভে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের প্রায়শ্চিত্ত না করে উল্টা বাংলা ভাষার উপর গোসা করেন এবং দ্বীনে ইসলাম এবং ভাষাকে সাংঘর্ষিক সম্পর্ক ঠেলে দেন। কিন্তু বাংলা ভাষার উত্থান ও বিকাশের ইতিহাসে আমরা এই দ্বন্দ্বের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি পাই না। বরং মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষার এতদূর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন যে বাংলা ভাষা সেই সময় সংহতি প্রতিষ্ঠার গুরুভার বহন করতে সক্ষম হয়েছিল। এর আগে আম জনতার ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ছোটলোকদের ভাষা হিসাবে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছে। মুসলমান শাসকেরা ইসলামের মূল্যবোধকে সামনে রেখে আমজনতার মুখের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে নিয়ে যান। মুসলমানদের শাসন আমলেই রামায়ণ , মহাভারত অনুবাদ হয়। মুসলমান কবিদের পাশাপাশি হিন্দু কবিরাও সমানভাবে বরং আরো বেশি কাব্য চর্চা করেছেন এবং বিষয়বস্তু হিসেবে নিজেদের ধর্ম, পুরাণ বেছে নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকগণ এতদূর ভূমিকা পালন করেছেন যে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে- মুসলমান শাসকগণ এ অঞ্চলে না এলে বাংলা ভাষা সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে এভবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারতো না, উপরন্তু বাংলা ভাষা অস্তিত্বের সংকটে তলিয়ে যেতে পারতো। সুতরাং এ সময়ে এসে বাংলা ভাষা ও দ্বীনকে সাংঘর্ষিক রূপে বিবেচনা করা মুসলমানদের ইতিহাস বিমুখতাকে স্পষ্ট করে তোলে।
ইবনে খালদুন উমরান আল হাদারিকে অর্থাৎ শহর কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে সত্যিকারের উমরান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কারণ হচ্ছে, শহরে জীবন বেশি বৈচিত্র্যময়। আল ফারাবীর ভাষায় , মানুষ আখলাকী পরিপূর্ণতা মূলত শহরেই লাভ করে থাকে। আমাদের ঢাকা শহর, বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের সবকটি জেলার মানুষের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ। এছাড়া নৈতিক বিপর্যয়ের সবধরনের পথ খোলা থাকে বলে, উচ্চতর মূল্যবোধে পৌঁছাতে মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। আর সংগ্রামের উৎস হিসেবেই শহরকে আখলাকী পরিপূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। এছাড়া অঞ্চল ভেদে বাংলা ভাষার উপভাষাগুলোও অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক হলো, এখানে আঞ্চলিক ভাষা যেমন বৈচিত্র্যের যোগান দেয় অন্যদিকে বাংলা ভাষার সুসংবদ্ধ প্রমিত রূপও রয়েছে যা আঞ্চলিক ভাষা থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার লাগাম টেনে ধরে।
সভ্যতা বিনির্মানে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে- এটি মূলত স্বপ্নের পর্যায়ভুক্ত আর এ স্বপ্নের সবচেয়ে বড় প্রেরণা হলো বিশ্বাস। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পৌঁছাতে সর্বপ্রথম আমাদের সময়ের বাস্তবতার দারস্থ হতে হবে। সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রথম পদক্ষেপ বিন্দুর স্বরূপ জানা জরুরি। এ বিষয়ে আলজেরিয়ার অকুতোভয় তাত্ত্বিক মালিক বিন নবী যাকে একালের আরব দুনিয়ার দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর মর্যাদা দেওয়া হয় আমরা তাঁর স্মরনাপন্ন হতে পারি। মালেক বিন নবী ইবনে খালদুনের আসাবিয়্যাত তত্ত্বকে আরো এক ধাপ অগ্রসর করে সভ্যতার বিবর্তন তত্ত্ব হিসেবে হাজির করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রত্যেক সভ্যতায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়। সভ্যতার বিবর্তন দেখাতে গিয়ে মালেক বিন নবী মুসলিম ইতিহাস ও সভ্যতাকে তিনটি স্তরে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমটি হলো, রাসুল (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদিনা সভ্যতা। এ সভ্যতার সতেজতা হারায় হজরত আলী (রা.) এবং মুআবিয়া (রা.) এর মধ্যে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং এ যুদ্ধেই মদিনা সভ্যতার আসাবিয়্যাত তথা সংহতি প্রথমবারের মতো বিনষ্ট হয়। পরবর্তী সময়ে আবার ইসলামি সভ্যতা শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে পৌঁছে — এটিকে মালেক বিন নবী ইসলামি সভ্যতার দ্বিতীয় পর্যায়ে বলেছেন। মুসলমানদের পতন পরবর্তী সময়কে বিবর্তনের তৃতীয় এবং সর্বশেষ রূপ হিসেবে দেখিয়েছেন তিনি। এই তৃতীয় পর্যায়ে উপনিবেশ প্রবণ এবং উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বলেছেন। মালেক বিন নবীর এই চিন্তা ইবনে খালদুনের চিন্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এবং এটি এমন এক সময় যখন বিজিত জাতি বিজেতাকে অনুসরণ করে কারণ বিজিত জাতির প্রতিরোধ শক্তি ফুরিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধের শুরুর দিকে ইংরেজদের থেকে দানে পাওয়া উপকরণসমূহকে ভারতীয়দের জন্য আশীর্বাদপুষ্ট বলে মনে করেছেন। পরবর্তী অংশে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চেহারার বিকৃতরূপ প্রত্যক্ষ করে পূর্ববর্তী চিন্তা থেকে সরে আসেন। তবে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা প্রত্যক্ষ না করলে হয়তো ইংরেজদের বয়ে আনা চিন্তাগত কাঠামোর আদলেই ভারতীয়দের সভ্য করার স্বপ্নে অবিচল থাকতেন।
কিন্তু মালেক বিন নবী বলছেন — সভ্যতা কুড়িয়ে পাওয়া বা অনুসরণের কোনো বিষয় নয় বরং সভ্যতা বিনির্মানের বিষয়। যেমন — স্থাপত্যকে বিনির্মান করা হয়।
কিন্তু উপনিবেশিক ও উত্তর উপনিবেশিক সময়ে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর চিন্তা করার সক্ষমতা এত বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যে এ জনগোষ্ঠীর দ্বারা অনুসরণ না করে কেবল নিজস্ব পরিসর থেকে চিন্তা উৎপাদন এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন্তার এই ঊষরতাই আমাদের সমাজকে সর্বাংশে পচনশীল করে তুলেছে। মালেক বিন নবী সভ্যতার বিনির্মানের ক্ষেত্রে এই পচনশীল সমাজকে পরিবর্তন করার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে পরিবর্তনের মূল শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে এই পরিবর্তন আবার আরোপিত হলে চলবে না বরং মানুষের কলবকে স্পর্শ করবে এবং সেই পরশমণির স্পর্শে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে। কারণ তিনি মনে করেন, যে পরিবর্তন মানুষের ভেতরকে পরিবর্তন করতে পারে না সেই পরিবর্তন দ্বারা সভ্যতার বিনির্মান কখনোই সম্ভব নয়। মালেক বিন নবী সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হৃদয়কে গুরুত্ব দিলেও বাহ্যিক যে রূপ থাকে সেটি কোনো না কোনোভাবে ভাষার সাথে সম্পৃক্ত।
বস্তুত সভ্যতার আলাপে এমন কোন দিক নেই যেখানে ভাষা অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে। বরং সভ্যতার মানে হচ্ছে একটি সচেতন জাতি যখন চিন্তাশীলভাবে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তোলে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে মানবতার মঞ্চে আত্মপ্রকাশ ঘটায়।
সভ্যতা বিনির্মানের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু স্বপ্ন এবং বিশ্বাসের পর্যায়ে রয়েছি, তাই বিশ্বাস প্রসঙ্গে দুটি কথা বলে শেষ করতে চাই। বর্তমান বাংলাদেশ বিভিন্ন অপরিণামদর্শী ব্যবস্থাপনা এবং বিতিকিচ্ছিরি নগর পরিকল্পনার কারণে এত বেশি অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে যে এখান থেকে সভ্যতা বিনির্মানের স্বপ্ন ইউটোপিয়া মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের স্বরণ রাখা উচিত, আমাদের অস্বস্তির দায় ভূমির নয়, ভাষার নয় আমাদের সৃষ্টি করা ব্যবস্থাপনার।
তথ্যসূত্র :
১. ইবনে খালদুন ও ইলমুল উমরান : প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন, অনুবাদ: বুরহান উদ্দিন।
২. ‘মালেক বিন নবী: চিন্তা ও কর্মের সমন্বিত উত্তরাধিকার’, রোয়াক ব্লগ
৩ ‘সভ্যতার বিনির্মানে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ভূমিকা: মালেক বিন নবীর বয়ান’, লেখক: প্রফেসর ড. আব্দুল আজিজ বারগৌত, অনুবাদ: নাজিয়া তাসনীম
৪. ‘ কালান্তর’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর