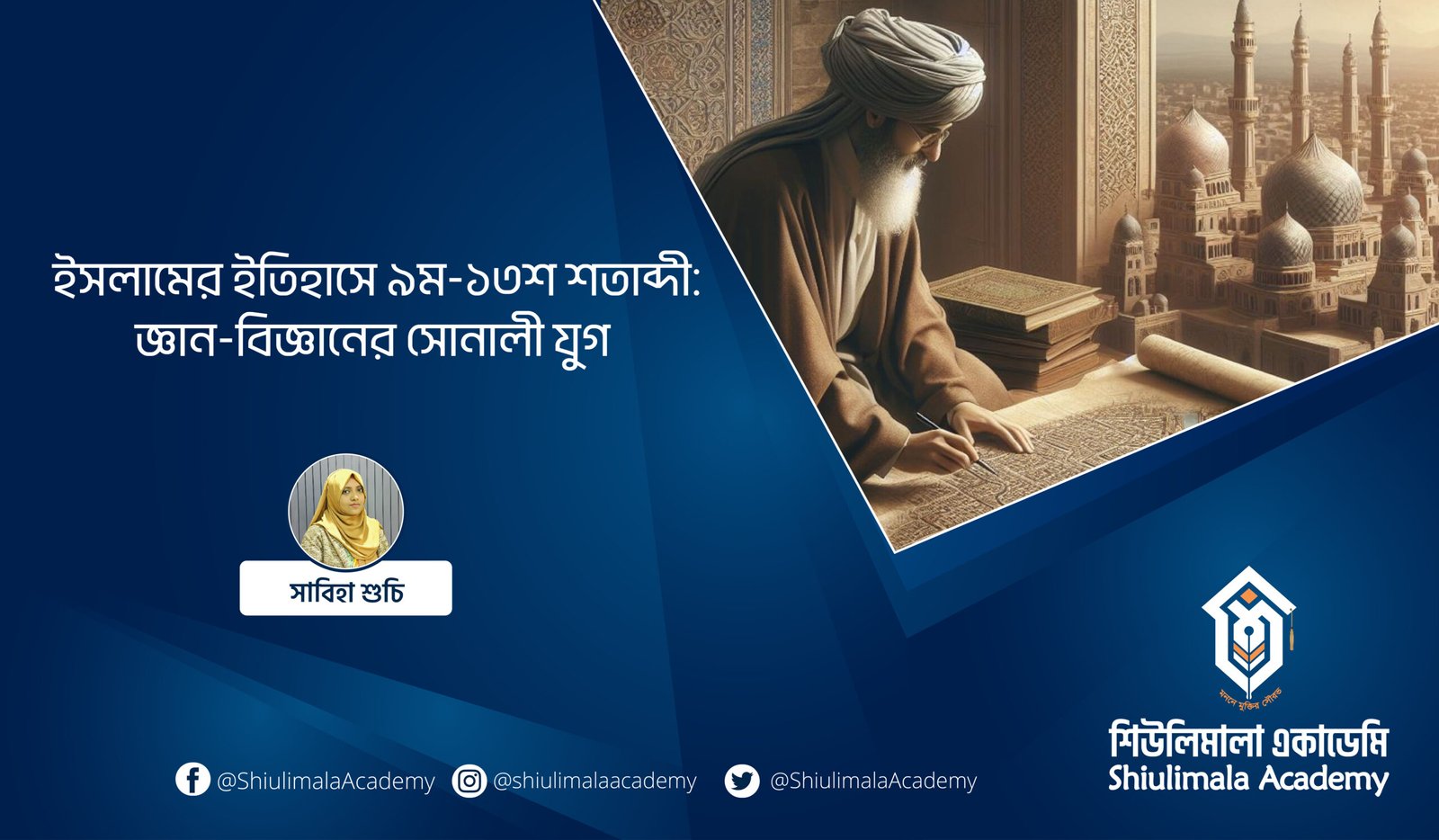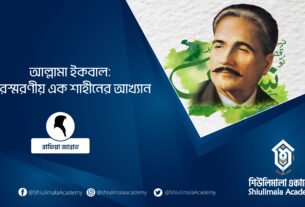ইসলামের ইতিহাসে ৯ম থেকে ১৩শ শতাব্দী ছিল উম্মাহর জন্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির অগ্রগতির এক সোনালি যুগ। এই কয়েক শতাব্দীতে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে উচ্চতা অর্জন করে, তা মানব ইতিহাসে বিরল। আরবের মরুভূমি থেকে উদ্ভূত হয়ে ইসলামের নূর তখন স্পেন (আন্দালুস) থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেই বিস্তারের ধারায় ইসলামি খিলাফত ও সালতানাত পরিণত হয় বহু ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের এক সমন্বিত ও জ্ঞাননির্ভর সমাজে।
ইসলামি সভ্যতা পূর্ববর্তী গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যকে অনুবাদ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপন করে। কুরআনের উৎসাহে ও হাদীসের আলোকে মুসলিম উলামা, হাকিম, মুফাক্কির ও ফুযালারা চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শনসহ নানা শাখায় যুগান্তকারী অবদান রাখেন। তাঁদের এই অবদান পরবর্তীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের জন্য পথপ্রদর্শক হয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে দেয়।
আব্বাসীয় খিলাফতের শাসনামলে, যার সীমা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, রাজধানী ছিল বাগদাদ। এই শহর ছিল ইসলামি সভ্যতার হৃদয়কেন্দ্র, যেখানে বসবাস করত প্রায় ১০ লাখ মানুষ — মুসলিম, আহলুল কিতাব, ফারসি, হিন্দু, গ্রিকসহ বহু জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ। বাগদাদ হয়ে ওঠে জ্ঞানচর্চার এক মহা কেন্দ্র, যেখানে প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞান একত্রিত হতে থাকে।
সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন (রহিমাহুল্লাহ) যিনি ৮১৩ থেকে ৮৩৩ হিজরিতে শাসন করেন, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞান, যুক্তি ও গবেষণা ছাড়া আদর্শ ইসলামি সমাজ কায়েম করা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে আলমে ইসলাম-এ ছড়িয়ে থাকা জ্ঞান ও আলিমদের একত্র করে মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করলেই উম্মাহর উন্নতি নিশ্চিত হবে। এই চেতনায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন “বাইতুল হিকমাহ” — জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল কেন্দ্র, যেখানে অনুবাদ, গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞানচর্চা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায়।
বাইতুল হিকমাহ: ইসলামি স্বর্ণযুগের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র
আব্বাসীয় খিলাফতের শাসনামলে ইরাকের বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত বাইতুল হিকমাহ ছিল একটি অনন্য গ্রন্থাগার, অনুবাদকেন্দ্র এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ইসলামি স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রধান জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। খলিফা হারুনুর রশিদ (শাসনকাল: ৭৮৬–৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ) বাইতুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁর পুত্র খলিফা আল মামুন (শাসনকাল: ৮১৩–৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) এর শাসনামলে এটি তার সর্বোচ্চ উৎকর্ষে পৌঁছে।
আল মামুন বিশ্বাস করতেন, জ্ঞান ও গবেষণার চর্চা ছাড়া উম্মাহর উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম, পারসিয়ান ও খ্রিস্টান পণ্ডিতদের বাইতুল হিকমাহতে একত্রিত করেন। এই পণ্ডিতরা শুধু গ্রন্থ অনুবাদ করেই থেমে থাকেননি, বরং চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শনসহ বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণাও চালান। নবম শতকের মধ্যভাগে বাইতুল হিকমাহ হয়ে ওঠে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থভাণ্ডারগুলোর একটি।
আব্বাসীয় খিলাফতের অনুবাদ আন্দোলন ছিল এই জ্ঞানচর্চার ভিত্তি। হারুনুর রশিদের সময় থেকেই গ্রীক, চৈনিক, সংস্কৃত ও সিরিয়াক ভাষার অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক বই বেশি অনূদিত হলেও অল্প সময়েই দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র এতে যুক্ত হয়।
হারুনুর রশিদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল বাইতুল হিকমাহের পূর্বসূরি। ইতিহাসবিদ আল কিফতি এটিকে নাম দেন “খিজানাত কুতুবুল হিকমাহ”, অর্থাৎ “জ্ঞানগ্রন্থের ভাণ্ডার”। এটি ছিল এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞান ছিল সম্মানের, ওলামা-মুফাক্কিরদের কাজ ছিল শ্রদ্ধার বিষয়।
আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বাইতুল হিকমাহর আর্থিক অবকাঠামো ব্যাপকভাবে মজবুত হয়। খলিফার নির্দেশে ও তার ব্যক্তিগত আগ্রহে এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা, বিতর্ক, অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জোরদার হয়। তিনি নিয়মিতভাবে বাইতুল হিকমাহর পণ্ডিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তাদের মাঝে বিতর্কে অংশ নিতেন এবং বিভিন্ন গবেষণাগোষ্ঠী গঠন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, আলমাজেস্ট-এর (Ptolemy-এর জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কাজ) তথ্য যাচাই, পৃথিবীর আকৃতি ও মানচিত্র নির্ধারণের জন্য তিনি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গবেষণার নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি মিশর নিয়ে গবেষণায় আগ্রহ দেখান এবং ব্যক্তিগতভাবে পিরামিড অনুসন্ধানে অংশগ্রহণ করেন।
আব্বাসীয় সমাজে জ্ঞান ও বইয়ের মর্যাদা এতটাই বেড়ে যায় যে, অনেক সময় যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদের চেয়েও বই ছিল বেশি কাঙ্ক্ষিত। বাইতুল হিকমাহ তখন শুধু একটি প্রতিষ্ঠান ছিল না; এটি ছিল উম্মাহর চিন্তা-চর্চার প্রাণকেন্দ্র, যেখানে আলেম, অনুবাদক, গবেষক ও পাণ্ডিত্যের সমাহার ঘটেছিল।
জ্ঞানের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে খলিফা আল মামুন (রহিমাহুল্লাহ) বাগদাদে গড়ে তোলেন এক অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যার নাম ছিল “বায়তুল হিকমাহ” — অর্থাৎ “জ্ঞানের গৃহ” (ইংরেজিতে House of Wisdom)। এটি ছিল শুধুমাত্র কোনো পাঠাগার নয়; বরং একই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়, অনুবাদকেন্দ্র, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার — সব মিলিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র।
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিক কোনো একাডেমির মতো কাঠামোবদ্ধ ছিল না, বরং এর প্রকৃতি ছিল অনেক বেশি উন্মুক্ত, গবেষণানির্ভর এবং বহুজাতিক পণ্ডিতসমন্বিত। এর আগে উমাইয়া খিলাফতের শাসনামলে কিছু ক্ষুদ্র পাঠাগার ও মাদরাসার প্রচলন ছিল। তবে জ্ঞানচর্চায় যে বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা ও গুরুত্ব আব্বাসীয় খেলাফত বিশেষত আল মামুনের আমলে দেখা যায়, তা ইসলামী ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
কথিত আছে, সে সময়ে যদি কোনো পণ্ডিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বইকে মূল ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করতেন, তাহলে তাঁর পরিশ্রমের সম্মানস্বরূপ বইটির ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হতো। এই রকম উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম ও অমুসলিম জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ বাগদাদমুখী হন। তারা পঙ্গপালের মতো ছুটে আসেন বায়তুল হিকমাহ-তে অংশগ্রহণের জন্য।
এই প্রথমবারের মতো পারস্য, মিশর, ভারতবর্ষ ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতরা এক ছাদের নিচে একত্রিত হন — যা মানব ইতিহাসে এক বিপ্লবী ঘটনা। ফলত, এই মিলনমেলায় এমনসব বৃহৎ গবেষণা ও আবিষ্কার সাধিত হয়, যা পরবর্তীকালে মানব সভ্যতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
আল মামুন ইতিহাসে সেই অল্পকিছু শাসকদের একজন, যিনি দ্বীনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও যুক্তির সমন্বয়কে উৎসাহ দিয়েছেন এবং খলিফার আসন থেকেও জ্ঞানের চর্চায় সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি নিজের প্রয়োজন ও কৌতূহলের বশে পৃথিবীর আকৃতি নির্ধারণ, মানচিত্র তৈরি, মিশরীয় পিরামিড অনুসন্ধানসহ নানা বিষয়ে গবেষণার নির্দেশ দেন এবং এসব কাজে ওলামা, জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদদের দল গঠন করেন।
মুসলিম উম্মাহর এই জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগকে স্মরণীয় করে রেখেছে আরও কিছু বিষয়। এর একটি হলো বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় — আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়, যা মরক্কোর ফেজ শহরে ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে একজন মুসলিম নারী ফাতিমা আল-ফিহরি (রহি.) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি এখনও কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে আছে এবং উচ্চশিক্ষার ধারাকে বহন করে চলেছে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, যখন মুসলিমরা খেলাফতের বিস্তার শুরু করে, তখন তারা সেই অদৃশ্য দেয়াল ভেঙে দেয়, যা ধর্ম, ভাষা ও বর্ণভেদের মাধ্যমে মানুষকে বিভক্ত করে রেখেছিল। খেলাফতের ছায়াতলে জ্ঞান, চিন্তা ও সংস্কৃতি নির্বিঘ্নে আদানপ্রদান শুরু হয়। ফলে ইসলামী সভ্যতা এক পরিপূর্ণ মানবিক জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থার রূপ নেয়।
ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট ও গণিতশাস্ত্রে মুসলিমদের অবদান
দ্বিতীয়ত, ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিভাজন এতটাই গভীর ছিল যে, আলেকজান্দ্রিয়ার (বর্তমান মিশর) একজন ব্যক্তি কখনো সাসানীয় পারস্যে (ইরান) গিয়ে পড়াশোনার কথা ভাবতেও পারত না। এমনকি কেউ যদি সাহস করে ভিনদেশে গিয়েও থাকত, তবে ভাষার ভিন্নতা ও সামাজিক বাধার কারণে সেখানে সে উপযোগীভাবে কিছু করতে পারত না। সেখানকার অধিবাসীরাও একজন বহিরাগতকে নিজেদের সমাজে গ্রহণ করত না।
তবে ইসলামি খিলাফতের বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যবধান দূর হয়ে যায়। খিলাফতের প্রসারের কারণে আরবি ভাষা এক সার্বজনীন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামে নামায, কুরআন পাঠ, দোয়া, ও ইবাদতের প্রায় সকল কার্যক্রম আরবিতেই সম্পাদিত হয়; ফলে উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য আরবি ভাষার ন্যূনতম জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ আরবিকে শুধু ধর্মীয় প্রয়োজনে নয়, বরং জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও গ্রহণ করতে থাকে। মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও গবেষকগণ আরবিকে তাঁদের জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন।
তৃতীয়ত, ইসলাম একমাত্র দ্বীন, যা জ্ঞানার্জনের ওপর এতটা গুরুত্ব দিয়েছে যে, একে ইবাদতের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস-এ জ্ঞান অন্বেষণ ও গবেষণার ব্যাপারে অসংখ্য উৎসাহমূলক বাণী পাওয়া যায়। একাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ ঘোষণা করেছেন:
> “যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়, আল্লাহ তা’আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”
(সহীহ মুসলিম)
এই বিশ্বাস থেকেই সোনালি যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞানচর্চাকে শুধু পার্থিব উন্নয়নের উপায় মনে করতেন না; বরং তাঁরা একে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাঁদের মতে, গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল এক ধরনের ইবাদত। এই আকিদা ও মানসিকতা থেকেই ইসলামের জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটে।
এই তিনটি প্রধান কারণ —
১. খেলাফতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ,
২. আরবি ভাষার সর্বজনীনতা, এবং
৩. দ্বীনের ভিতর জ্ঞানচর্চার ইবাদতী গুরুত্ব —
এইগুলোই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক বৈজ্ঞানিক চেতনার জন্ম দেয় এবং তাঁদের মৌলিক গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তোলে।
বাস্তবতা হলো, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরপরই মুসলিম সমাজে এই জাগরণ না ঘটত, তবে শুধুমাত্র সেনা অভিযানের মাধ্যমে মুসলিম খেলাফতকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে যেত। জ্ঞান ও চিন্তার ভিত্তিতেই মুসলিম উম্মাহর সত্যিকারের শক্তিমত্তা গড়ে উঠেছিল।
গণিতে মুসলিমদের অবদান
ইসলামের স্বর্ণযুগে যে সকল শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি গবেষণা ও উন্নতি সাধিত হয়, তার মধ্যে গণিত ছিল অন্যতম। কারণ গণিত হলো বিজ্ঞানের মূলভিত্তি — পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোলসহ প্রায় সকল বিজ্ঞানের মৌলিক কাঠামো গণিতের ওপরই নির্ভরশীল।
সেই যুগের মুসলিম পণ্ডিতরা গণিতকে শুধুমাত্র একটি ব্যবহারিক বিষয় নয়, বরং তাওহিদের অনুধাবনের একটি উপায় হিসেবে দেখতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টিজগতে পরিপূর্ণ নির্ণয় ও নিখুঁত সামঞ্জস্য—আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন—গণিতের মাধ্যমে বুঝে আসা সম্ভব। তারা বলতেন, যদি কেউ গণিতের গভীরে প্রবেশ করে, তাহলে সে সৃষ্টিজগতের রহস্য ও আল্লাহর সৃষ্টির কৌশল আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।
তখনকার বিজ্ঞানীদের কাছে মহাকাশ এক রহস্যময় সৃষ্টি ছিল, কিন্তু তারা ধারণা করতেন এই বিশাল মহাবিশ্ব আল্লাহর নির্ধারিত গাণিতিক বিধান অনুসারে চলমান। তাঁরা গণিতচর্চাকে শুধু জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয়, বরং আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে বোঝার এক পবিত্র পথ মনে করতেন।
ফলে গণিত তখন ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে। মুসলিম গণিতবিদদের মধ্যে যেমন ছিলেন আল-খাওয়ারিজমি, উমর খইয়াম, আল-বাতানি প্রমুখ, যাঁদের কাজ পরবর্তী ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বেও গভীর প্রভাব ফেলে।
মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিজমি: গণিতশাস্ত্রের জনক
ইসলামের সোনালি যুগে যেসব মহাপণ্ডিত গণিত ও বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম আসে মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিজমি (রহিমাহুল্লাহ)-এর। তিনি একজন পারসিয়ান মুসলিম, যিনি আনুমানিক ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে বাগদাদে বাইতুল হিকমাহ-তে প্রথম দিকের অন্যতম প্রধান আলিম ও গবেষক ছিলেন। জ্ঞান ও গণিতচর্চার যে পরিশীলিত ধারা পরবর্তী সময়ে বিকশিত হয়, তার বীজ তিনিই রোপণ করেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।
ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন ও শূন্যের ধারণা
আল-খাওয়ারিজমির অন্যতম যুগান্তকারী অবদান হলো, তিনি ভারতীয় দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিকে আরবি ভাষায় জনপ্রিয় করে তোলেন। তার আগ পর্যন্ত আরবরা রোমান সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত, যা ছিল জটিল ও সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে অপূর্ণাঙ্গ সংখ্যা বা জটিল গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলো রোমান সংখ্যায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতিতে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সরল অঙ্ক ব্যবহার করে যে কোনো সংখ্যা সহজেই প্রকাশ করা যেত। এর মাধ্যমে গণনার জগতে এক বিপ্লব আসে।
তিনি শুধু এই সংখ্যাগুলোই গ্রহণ করেননি, বরং এর সঙ্গে যুক্ত করেন ‘শূন্য’ (০) — যা গাণিতিক ইতিহাসে একটি মৌলিক ও বৈপ্লবিক ধারণা। যদিও তিনি শূন্যের পূর্ণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, তবুও তার প্রয়োগ ও গণনায় সফল ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি গণিতের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।
বীজগণিত ও দ্বিঘাত সমীকরণে অনন্য অবদান
আল-খাওয়ারিজমির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হলো তাঁর বীজগণিত (Al-Jabr) বিষয়ক বই “Al-Kitāb al-Mukhtaṣar fī Ḥisāb al-Jabr wal-Muqābala”। এই বইয়ে তিনি বর্গক্ষেত্র সম্পূর্ণ করে কীভাবে দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করা যায় তা ব্যাখ্যা করেন। দ্বাদশ শতকে এই গ্রন্থটি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং পরবর্তী প্রায় ৪০০ বছর ধরে এটি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রধান গণিত পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় অবদান
তিনি শুধু গণিতবিদ ছিলেন না; ছিলেন একজন দক্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ। তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক পণ্ডিত টলেমি-র ভূগোল সংশোধন করেন এবং বিভিন্ন নগর ও অঞ্চলের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ তালিকাভুক্ত করেন। খলিফা আল মামুনের আদেশে তিনি ৭০ জন ভূগোলবিদের একটি দলের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব মানচিত্র তৈরির কাজ পরিচালনা করেন।
এছাড়া তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সারণি (astronomical tables) প্রস্তুত করেন, বর্ষপঞ্জি হিসাব করেন এবং অ্যাস্ট্রোল্যাব ও সূর্যঘড়ি সম্পর্কিত যন্ত্র ও প্রযুক্তির ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা অনন্য — তিনি সঠিক sine ও cosine টেবিল তৈরি করেন এবং tangent-এর প্রাথমিক সারণি প্রবর্তন করেন।
ইউরোপে প্রভাব ও ‘অ্যালগরিদম’-এর জন্ম
১২শ শতকে যখন মুসলিম জ্ঞান ইউরোপে অনূদিত হতে শুরু করে, তখন আল-খাওয়ারিজমির রচনাগুলোও লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিপ্লবী প্রভাব বিস্তার করে। তার লাতিনকৃত নাম “Algorismus” থেকে পরে “Algorithm” শব্দটির উৎপত্তি ঘটে — যা আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণনার মূলভিত্তি।
তার এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে ইউরোপে প্রচলিত আবাকাস-ভিত্তিক গণনা পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করে দেয়। যদিও তার রচনাগুলোর যেসব লাতিন অনুবাদ বর্তমান আছে, সেগুলোর মধ্যে কোনোটিই পরিপূর্ণরূপে একে অপরের অনুরূপ নয়, তবুও প্রতিটি অনুবাদই ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাসে নতুন জোয়ার এনেছিল।
আল-খাওয়ারিজমি ছিলেন ইসলামী জ্ঞানচর্চার একটি প্রগাঢ় স্তম্ভ। তার নিরলস গবেষণা, নব উদ্ভাবন ও চিন্তাশীলতা পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম ও অমুসলিম উভয় জ্ঞানীর জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে। গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা — সর্বত্রই তার অবদান এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো উম্মাহর ইতিহাসকে আলোকিত করে রেখেছে।
আল-খাওয়ারিজমির ভূগোলচর্চা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা
মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিজমি (রহিমাহুল্লাহ) কেবল গণিতেই নয়, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত “কিতাব সুরতুল আরদ” (আরবি: كتاب صورة الأرض, অর্থাৎ “পৃথিবীর চিত্র”) গ্রন্থটি তাঁর ভূগোল বিষয়ক প্রধান কীর্তি হিসেবে পরিচিত। এই গ্রন্থের মূল আরবি অনুলিপি একমাত্র সংরক্ষিত রয়েছে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। এর একটি লাতিন অনুবাদ সংরক্ষিত রয়েছে মাদ্রিদের ‘বিবলিওতেকা নাসিওনাল দে এস্পানায়’।
এই কিতাবে আল-খাওয়ারিজমি পৃথিবীর স্থানগুলোর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ আবহাওয়াগত অঞ্চল অনুযায়ী (climatic zones) সাজিয়ে তালিকাভুক্ত করেন। প্রতিটি আবহাওয়া অঞ্চলে শহর ও স্থানগুলোর অবস্থান দ্রাঘিমাংশের ক্রম অনুসারে উপস্থাপন করা হয়। যদিও গ্রন্থের সংরক্ষিত অনুলিপিটি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং পাঠোদ্ধার করা কঠিন, তথাপি আধুনিক গবেষক হুবার্ট ডাউনিশ্ট স্থানাঙ্ক বিশ্লেষণ করে অনুপস্থিত মানচিত্রটি পুনর্গঠন করতে সক্ষম হন।
ডাউনিশ্ট প্রাপ্ত স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ-এর তথ্য নিয়ে সেগুলোকে গ্রাফ কাগজে স্থানান্তর করেন এবং একে অপরের সঙ্গে সরল রেখায় সংযুক্ত করে মূল মানচিত্রে উপকূলরেখা, নদী, শহরের আনুমানিক চিত্র উপস্থাপন করেন। যদিও মূল আরবি পাঠ কিংবা লাতিন অনুবাদে কোন মানচিত্র সরাসরি অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তথাপি এই পদ্ধতিতে ভূগোলের নির্ভুল বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে।
টলেমির ত্রুটি সংশোধন ও আধুনিক ভূগোলের বীজ
আল-খাওয়ারিজমি বিখ্যাত গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমি-র ভূগোল সংশোধন করে বাস্তবভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করেন। যেমন, টলেমি কানারি দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত দূরত্ব ৬৩ দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণ করেছিলেন, যা ছিল বাস্তবের তুলনায় অতিরঞ্জিত। আল-খাওয়ারিজমি এই দূরত্ব সংশোধন করে প্রায় সঠিকভাবে ৫০ দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণ করেন।
তিনি টলেমির মতো আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরকে স্থলবেষ্টিত বলে দেখাননি, বরং উন্মুক্ত জলাভূমি হিসেবে উপস্থাপন করেন — যা ছিল যুগান্তকারী ধারণা। আল-খাওয়ারিজমির মানচিত্রে ব্যবহৃত মূল মধ্যরেখা (prime meridian) ছিল ফরচুনেট দ্বীপপুঞ্জে, যা টলেমি ও মারিনাস ব্যবহৃত রেখার তুলনায় প্রায় ১০° পূর্বে অবস্থিত। পরবর্তী অনেক মুসলিম ভূগোলবিদ তার এই মধ্যরেখাই ব্যবহার করে তাঁদের নির্দেশিকা তৈরি করেন।
ইহুদি বর্ষপঞ্জি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণা
আল-খাওয়ারিজমি ইহুদি বর্ষপঞ্জি সংক্রান্ত একটি বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম:
“রিসালাহ ফি ইস্তিখরাজ তারিখিল ইয়াহুদ” (আরবি: رسالة في استخراج تأريخ اليهود, অর্থাৎ “ইহুদিদের ইতিহাস ও বর্ষপঞ্জি নির্ণয়ের পদ্ধতি”)।
এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন:
মেটোনীয় চক্র (১৯ বছরের চাঁদের চক্র),
তিশরেই মাসের প্রথম দিন নির্ধারণের নিয়মাবলি,
সৃষ্টাব্দ, ইহুদি বর্ষপঞ্জি ও সেলিউসিড যুগের মধ্যে ব্যবধান,
সূর্য ও চন্দ্রের গড় দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের নিয়ম।
এই গবেষণামূলক কাজগুলোর অনুরূপ আলোচনা পরবর্তীতে মুসলিম পণ্ডিত আল-বিরুনি ও ইহুদি দার্শনিক ইবনে মৈমুন-এর লেখায়ও পাওয়া যায়, যা আল-খাওয়ারিজমির বহুমাত্রিক জ্ঞানের পরিধিকে নির্দেশ করে।
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
আল-খাওয়ারিজমির অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁর আনুমানিক ১২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে, যার তারিখ ছিল ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩। এই স্মারকচিহ্ন তাঁর অবদানকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে চিহ্নিত করে দেয়।
আল-খাওয়ারিজমি ছিলেন এমন এক আলেম, যিনি শুধু গণিতে নয়, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সময়চক্র বিশ্লেষণ, মানচিত্রবিদ্যা ও ধর্ম-ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি সম্পর্কিত গবেষণায়ও অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর কাজগুলো শত শত বছর পরও ইউরোপ ও মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং বিশ্ববিজ্ঞান ও ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।
আল-খাওয়ারিজমি ও ইসলামী গণিতের উত্তরাধিকার
মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিজমি (রহিমাহুল্লাহ)-র স্মরণে আজও তাঁর নাম অম্লান হয়ে আছে পৃথিবীর বাইরে, মহাকাশেও। তাঁর নামে চন্দ্রপৃষ্ঠে একটি অভিঘাত গহ্বর রয়েছে, যা “আল-খাওয়ারিজমি (চন্দ্রগহ্বর)” নামে পরিচিত। এছাড়াও দুটি গ্রহাণু তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে:
১৩৪৯৮ আল-খাওয়ারিজমি — মূলরেখার একটি গ্রহাণু, যা ১৯৮৬ সালের ৬ আগস্ট স্মোলিয়ানে ই. ডব্লিউ. এলস্ট ও ভি. জি. ইভানোভা কর্তৃক আবিষ্কৃত।
১১১৫৬ আল-খাওয়ারিজমি — আরেকটি মূলরেখার গ্রহাণু, যা ১৯৯৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রেসকটে পি. জি. কম্বা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।
ইউরোপে ইসলামী গণিতের প্রভাব
দশম শতাব্দীতে ইউরোপে যখন জ্ঞান ও গণিতচর্চা প্রায় স্তব্ধ, তখনই ক্যাথলিক পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে গণিতের জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি মুসলিম স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা সফরের সময় সেখানকার মুসলিম আলিমদের থেকে গণিতশাস্ত্রে দীক্ষা নেন এবং ইউরোপে গণিতচর্চার নতুন ধারা সূচিত হয়।
বীজগণিতের জনক: আল-খাওয়ারিজমি
আল-খাওয়ারিজমির সবচেয়ে বড় ও স্থায়ী অবদান নিঃসন্দেহে বীজগণিত (Algebra)। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ
“আল-কিতাব আল-মুখতাসার ফি হিসাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা”
(বাংলা: “পূর্ণতা ও ভারসাম্যের মাধ্যমে গণনার সংক্ষিপ্ত পুস্তক”)-তে ব্যাখ্যা করেন কীভাবে বীজগাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ভূগোল, হিসাববিজ্ঞানসহ নানা বাস্তব বিষয় সমাধান করা যায়।
এর আগে গ্রিকরা জ্যামিতিকে প্রাধান্য দিলেও, তারা বীজগণিতকে জ্যামিতি থেকে আলাদা করে আত্মনির্ভর কোনো শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। এই সীমাবদ্ধতা দূর করেন আল-খাওয়ারিজমি। তিনি বীজগণিতকে স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ একটি শাস্ত্ররূপে গড়ে তোলেন এবং এর বাস্তবপ্রয়োগ দেখিয়ে দেন।
তার বইয়ের শিরোনামের “আল-জাবর” (الجبر) শব্দ থেকেই ইংরেজি “Algebra” শব্দটির উৎপত্তি। ‘আল-জাবর’ অর্থ হলো পূর্ণতা আনা বা ভারসাম্য স্থাপন। কারণ, বীজগাণিতিক সমীকরণ সমাধানে প্রতিটি পদ্ধতির লক্ষ্যই হলো সমীকরণের উভয় পাশে সমতা আনা।
উমর খৈয়াম: গণিত ও কবিতার সমন্বয়ে এক বিস্ময়
আরেক মুসলিম গণিতবিদ যিনি গণিত ও কাব্যচর্চা উভয় দিকেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তিনি হলেন উমর খৈয়াম (১০৪৮–১১৩১)। যদিও বিশ্বজুড়ে তিনি মূলত আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম নিয়ে রচিত কবিতার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন গভীর গবেষণাধর্মী গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী।
তিনি গণিতচর্চাকে তার আগের পণ্ডিতদের তুলনায় আরও গভীর ও বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে যেতে চান। বিশেষ করে তিনি কিউবিক (তিন মাত্রার) সমীকরণ সমাধানের জন্য একাধিক পদ্ধতির সূচনা করেন এবং বীজগাণিতিক পন্থায় এর বাস্তব প্রয়োগ দেখান। তিনিই প্রথম যুগের গণিতজ্ঞদের একজন, যিনি দ্বিপদী তত্ত্ব (Binomial Theorem) প্রণয়ন করেন — যা পরবর্তীতে আধুনিক গণিতের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে ওঠে।
এইসব পদ্ধতি দেখতে তাত্ত্বিক মনে হলেও, এগুলোর ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী সময়ে উচ্চতর বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও ক্যালকুলাস গড়ে ওঠে।
আল-খাওয়ারিজমি ও উমর খৈয়াম শুধু মুসলিম জ্ঞানবিশ্বে নয়, বরং বিশ্বজুড়ে গণিত ও বিজ্ঞানের মৌল ভিত্তি রচনায় অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের আবিষ্কার, চিন্তাধারা ও গবেষণাই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁস, আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই দুই মনীষীর জীবন ও কর্ম মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় — যে ঐতিহ্য ধর্ম, বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণকে একসূত্রে গেঁথে ফেলে।
আল বাত্তানি, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলিমদের অনন্য অবদান
ইসলামের সোনালি যুগে মুসলিম পণ্ডিতরা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এমনসব মৌলিক অবদান রাখেন, যার প্রভাব আজকের আধুনিক প্রযুক্তিতেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। সেইসব মহাপণ্ডিতদের মধ্যে আল বাত্তানি (আলবাটেনিয়াস নামেও পরিচিত) ছিলেন একজন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যিনি ত্রিকোণমিতিকে বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেন।
কিবলার নির্ণয় ও ত্রিকোণমিতির প্রয়োজনীয়তা
ত্রিকোণমিতির তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং তারকার গতিপথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে নিজের অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। এটি মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ নামায আদায়ের সময় কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো একটি অপরিহার্য বিধান। তখনকার উলামা ও পণ্ডিতরা পৃথিবীর বিভিন্ন শহর থেকে মক্কা শরিফের দূরত্ব ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করতে ত্রিকোণমিতির সাহায্য নেন।
এই প্রয়োজন থেকেই একটি বিশেষ বই সংকলিত হয়, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন শহর থেকে মক্কার দিকনির্দেশনা ও দূরত্ব নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। ফলে আজ যখন আমরা হাজার বছরের পুরোনো মসজিদগুলোর দিকে তাকাই—যা মক্কা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত—তখন বিস্মিত না হয়ে পারি না যে, সেই সময়েও কিবলামুখী স্থাপনাগুলো কী নিখুঁতভাবে নির্মিত হয়েছিল! বাস্তবিক অর্থে, আজকের জিপিএস প্রযুক্তির ভিত্তিও অনেকাংশে এই মুসলিম পণ্ডিতদের প্রাথমিক ত্রিকোণমিতিক হিসাব-নিকাশের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
আল বাত্তানির জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান
আল বাত্তানির সবচেয়ে বিখ্যাত ও সুনির্দিষ্ট অবদান হলো সৌরবর্ষের নির্ভুল পরিমাপ। তিনি গণনায় দেখান যে, এক সৌর বছর হয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড, যা আধুনিক পরিমাপের চেয়ে মাত্র ২ মিনিট ২২ সেকেন্ড কম — এক কথায় আশ্চর্যজনক নির্ভুলতা!
এছাড়া তিনি গ্রিক পণ্ডিত টলেমি-এর বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা সংশোধন করেন, বিশেষ করে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ-সংক্রান্ত তত্ত্ব। আল বাত্তানি এই গ্রহণগুলোর প্রকৃত কার্যকারণ ও সময়কাল নতুন প্রামাণিক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এমনকি পরবর্তী শতাব্দীতে বিখ্যাত ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস যে সব পরিমাপ উপস্থাপন করেন, তার অনেক আগে থেকেই আল বাত্তানির হিসাবগুলো আরও নিখুঁত ছিল।
মহাকাশ বিজ্ঞান ও ইসলামি চেতনা
মুসলিম পণ্ডিতদের গণিতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি একটি বিশাল সুফল বয়ে আনে মহাকাশ বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে। তারা যে সকল তত্ত্ব, সূত্র ও সূত্রবদ্ধ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, তা-ই হয়ে ওঠে তারকারাজি, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ নিয়ে গবেষণার ভিত্তি।
তবে শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নয়—এখানে ইসলামী ঈমানি চেতনা-ও ছিল এক বড় উৎসাহের উৎস। পবিত্র কুরআনুল কারিমে বহু আয়াতে নভোমণ্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্যের গতি এবং আকাশে ভেসে থাকা তারাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে:
> “সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব অনুসারে চলমান।”
(সূরা আর-রহমান: ৫)
“রাতের আঁধারে তারা-সমূহের মাধ্যমে মানুষ পথ খুঁজে নেয়।”
(সূরা আন-নাহল: ১৬)
এই আয়াতগুলো মুসলিম পণ্ডিতদের মনে গভীর ঈমানি দায়বদ্ধতা ও গবেষণার প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। তাঁরা মনে করতেন, কুরআনের নির্দেশিত এই নিদর্শনগুলো বুঝে নেওয়া এবং তা থেকে উপকার লাভ করাও এক প্রকার ইবাদত।
এ সময় আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিম বসবাস করতেন, যাঁরা এই বৈজ্ঞানিক প্রয়াসকে নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতিটি বিষয় ছিল তাঁদের নিকট শুধু গবেষণার বস্তু নয়—বরং আল্লাহর সৃষ্টিজগত বুঝে নেয়ার একটি আমল।
আল বাত্তানি ও তাঁর সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিতরা ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশচর্চার জগতে যে পথ উন্মোচন করেন, তা শুধু মুসলিম জগৎ নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁদের এই অবদানই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করে, যার ফল আমরা এখনো ভোগ করছি।
কুরআনিক অনুপ্রেরণা ও মুসলিমদের মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চা
কুরআনুল হাকিম-এ নভোমণ্ডল, নক্ষত্র, গ্রহ ও সৃষ্টিজগতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাকাশ বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেন। প্রাচীন কালে জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) ও জ্যোতিষশাস্ত্র (astrology)-কে একই শাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যার ফলে মানুষের জীবনে নক্ষত্র ও গ্রহের প্রভাব নিয়ে নানা কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে।
মুসলিমদের বৈপ্লবিক অবদান: জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের পৃথকীকরণ
মুসলিম বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যাকে জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে আলাদা করে একটি বিশুদ্ধ, পর্যবেক্ষণভিত্তিক বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের গবেষণায় যুক্তি, পরিমাপ, গাণিতিক বিশ্লেষণ এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণই ছিল মুখ্য উপাদান।
এই শাখায় মুসলিমদের ব্যাপক অগ্রগতির পেছনে আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন (রহ.) এবং বায়তুল হিকমাহ-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাগদাদে অবস্থিত এই বিদ্যাপীঠে মুসলিম পণ্ডিতরা গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমি-র তত্ত্বগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তার অনেক ভুল তত্ত্ব সংশোধন করেন।
আল-বিরুনি ও ভূ-কেন্দ্রিকতার সংশোধন
টলেমির মূল বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী স্থির এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র তার চারপাশে ঘুরছে — অর্থাৎ ভূকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষা। কিন্তু মুসলিম গবেষকগণ গবেষণার মাধ্যমে দেখতে পান, এই ধারণা বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণভিত্তিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
একাদশ শতাব্দীতে ইমাম আল-বিরুনি (রহিমাহুল্লাহ) স্পষ্টভাবে বলেন যে, পৃথিবী স্থির নয়; বরং তা নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণনশীল। যদিও তাঁর এই বক্তব্য তৎকালীন সব মুসলিম বিজ্ঞানীর দ্বারা গৃহীত হয়নি এবং এই বিষয়টি নিয়ে কিছু বিতর্ক ছিল, তবুও এটি ছিল এক বিপ্লবী চিন্তার সূচনা।
আল-বিরুনি আরও একটি চমকপ্রদ বিষয় করেন — তিনি ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদি ক্যালেন্ডার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঘণ্টাকে সেক্সাজেসিমাল পদ্ধতিতে ভাগ করেন — অর্থাৎ ঘণ্টাকে মিনিট, সেকেন্ড, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে বিভক্ত করেন। এটি সময় গণনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে ওঠে।
আল মাজরিতি ও ইউরোপে প্রভাব
আন্দালুসিয়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত আল মাজরিতি (রহ.) মহাকাশ-সংক্রান্ত গণনার টেবিল ও ডেটাগুলো পুনর্গঠন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও ইউরোপীয় পণ্ডিতরা আইবেরীয় উপদ্বীপে এসে মুসলিম জ্যোতির্বিদদের কাজ অনুবাদ ও গবেষণা অব্যাহত রাখে। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে বিকাশ লাভ করা মহাকাশ তত্ত্বগুলো ধীরে ধীরে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।
এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তী সময়ে কোপারনিকাস, গ্যালিলিও প্রমুখ পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যান। যদিও মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তার দ্বারা তারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন, পশ্চিমে তখনও বিজ্ঞানচর্চা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ — কারণ চার্চের বিরোধিতার কারণে অনেক বিজ্ঞানীকে নির্যাতন ও কারাবরণ করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে মুসলিম জগতে বিজ্ঞানচর্চা ছিল ইবাদত হিসেবে বিবেচিত; তাই মুসলিম বিজ্ঞানীরা এমন বাধার সম্মুখীন হননি।
মহাকাশবিজ্ঞানে এস্ট্রোল্যাবের ভূমিকা
মহাকাশ ও নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে মুসলিমদের আরেকটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার হলো এস্ট্রোল্যাব নামক যন্ত্রের উন্নয়ন। যদিও এর আদিরূপ গ্রিক আমলে তৈরি হয়েছিল, মুসলিম বিজ্ঞানীরা এতে ত্রিকোণমিতিক সূত্র ও গণিতীয় উন্নয়ন যুক্ত করে এটিকে আরও কার্যকর করে তোলেন।
এই যন্ত্রের মাধ্যমে তারকার অবস্থান দেখে জাহাজের অক্ষাংশ নির্ধারণ করা যেত। এটি ধরে আকাশে নির্দিষ্ট তারাপুঞ্জের দিকে তাক করলে জাহাজ কোথায় অবস্থান করছে তা নির্ণয় করা যেত।
উল্লেখযোগ্যভাবে, মুসলিম পণ্ডিতদের তৈরি করা বিশেষ বই (যেখানে মক্কা থেকে বিভিন্ন শহরের দূরত্ব ও কিবলার দিক উল্লেখ ছিল) এর সঙ্গে মিলিয়ে নাবিকেরা আপনার অবস্থান নির্ণয় করে গন্তব্যের দিক ঠিক করতে পারতেন। এর মাধ্যমে বিশেষ করে দূরদেশ থেকে হজে আগত মুসলিমদের যাতায়াত আরও নিরাপদ, সহজ ও সময়মাফিক হতো।
যেহেতু মুসলিম সভ্যতা সেই সময় আন্দালুস থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাই স্থল ও নৌপথে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও নিরাপদ চলাচল ছিল একটি বাস্তবিক প্রয়োজন। ১৮শ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত এস্ট্রোলেব ছিল নৌবাহিনীর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য যন্ত্র।
ভূগোল ও মুসলিম জ্ঞানচর্চার বিপ্লব
গণিতের ভিত্তির উপর যেমন মহাকাশবিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি মহাকাশ ও জ্যোতির্বিদ্যার নানাদিক থেকে উৎসাহ নিয়ে ভূগোলবিদ্যা ইসলামি সভ্যতায় এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। ইসলামের সোনালি যুগে মুসলিম খিলাফত ও সালতানাত-এর বিস্তৃতি এতই ব্যাপক ছিল যে, একক নেতৃত্বে পরিচালিত এমন বিশাল ভূখণ্ড মানব ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নিরাপদ যাতায়াত ও প্রশাসনিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।
এই বাস্তবিক প্রয়োজনেই আব্বাসীয় শাসনামলে এমন সব মুসলিম ভূগোলবিদ আবির্ভূত হন, যাঁরা পৃথিবীর গঠন, পরিধি ও মানচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রাখেন।
পৃথিবীর আকৃতি ও পরিধি নির্ণয়ে মুসলিমদের সাফল্য
সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাসই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি পৃথিবীকে গোলাকার বলে প্রমাণ করেন। বাস্তবে এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ, বহু পূর্ব থেকেই বিশেষ করে নাবিক সম্প্রদায় জানত যে পৃথিবী সমতল নয়। নৌযাত্রায় দিগন্তের আড়ালে জাহাজের ধীরে ধীরে অদৃশ্য হওয়া এবং তার আগা প্রথম দেখা যাওয়ার বিষয়টি থেকেই তারা ধারণা করেছিল পৃথিবী বক্রপৃষ্ঠবিশিষ্ট।
গ্রিক দার্শনিকরা পৃথিবীর পরিমাপের চেষ্টা করলেও তাদের হিসাব ছিল অসম্পূর্ণ এবং আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলত, তাদের দেওয়া পৃথিবীর আকৃতি ও পরিধির হিসাব প্রকৃত পরিমাপ থেকে অনেক দূরে ছিল।
অপরদিকে, আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে মুসলিম বিজ্ঞানীরা, গণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির সাহায্যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন ১২,৭২৮ কিলোমিটার, যা প্রকৃত ব্যাসার্ধ (১২,৭৬৫ কিমি) থেকে মাত্র ৩৭ কিমি কম। তারা পৃথিবীর পরিধি নির্ধারণ করেন ৩৯,৯৬৮ কিমি, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে এটি ৪০,০৭৪ কিমি — এক কথায়, নিখুঁত!
এই হিসাব তারা কোনো স্যাটেলাইট, টেলিস্কোপ বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই করেছিলেন, কেবল পাটিগণিত, চন্দ্র-সূর্য পর্যবেক্ষণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই অসামান্য সাফল্য সত্যিই বিস্ময়কর।
আল-ইদরিসি ও ইসলামী বিশ্ব-মানচিত্র
মুসলিম ভূগোলবিদদের সবচেয়ে উজ্জ্বল নামগুলোর মধ্যে অন্যতম হলেন আল-শরীফ আল-ইদরিসি (১১০০–১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি সিসিলির অধিবাসী ছিলেন — একটি অঞ্চল যা একসময় মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরবর্তীকালে নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজারের শাসনাধীন হয়। আল-ইদরিসির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সেই রাজাই তাঁকে বিশ্ব মানচিত্র অঙ্কনের পৃষ্ঠপোষকতা দেন।
তিনি যেই মানচিত্র আঁকেন, সেটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম বিস্তৃত ও তথ্যবহুল বিশ্ব মানচিত্র। শুধু ভৌগোলিক চিত্রই নয়, তিনি এতে বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ দেন। এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল মূলত পর্যটক, নাবিক ও যাত্রাপথে ঘুরে আসা মানুষের কাছ থেকে, যার কারণে মানচিত্রটি বাস্তবসম্মত ও তথ্যভিত্তিক ছিল।
এই মানচিত্রটি পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ও মুসলিম বিশ্বে প্রধান মানচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি বিশ্ববিখ্যাত অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও ভাস্কো দা গামা তাঁদের সমুদ্র অভিযানের সময় আল-ইদরিসির মানচিত্র-ই ব্যবহার করেছিলেন।
আল-ইদরিসির মানচিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি যেসব মানচিত্র অঙ্কন করতেন, সেগুলোর দিকবিন্যাস ছিল উল্টো — অর্থাৎ উত্তর ছিল নিচে, দক্ষিণ উপরে। এটি ছিল সে সময়কার অনেক ইসলামি মানচিত্রের প্রচলিত রীতি, যা কিবলার দিক ও হিজরতের ভূমির প্রতি সম্মান প্রকাশের একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি।
ভূগোলশাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান ছিল একাধারে বৈজ্ঞানিক, বাস্তবিক এবং দীন-অনুপ্রাণিত। বিশ্বমানচিত্র অঙ্কন, পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় কিংবা দিকনির্দেশনা সংক্রান্ত জ্ঞান— প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিমরা এমন নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি স্থাপন করেন, যার প্রভাব আজও টিকে আছে।
এই অবদানের মাধ্যমেই মুসলিম বিশ্ব ইলম (জ্ঞান) ও আমল (কার্যকর প্রয়োগ)-এর সংমিশ্রণে সত্যিকার অর্থে জ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।
আটলান্টিক অভিযানে মুসলিমদের ভূমিকাঃ কলম্বাস-পূর্ব অভিযাত্রার ইতিহাস
ইসলামের সোনালি যুগে মুসলিম ভূগোলবিদদের দৃষ্টি শুধু পরিচিত জগৎ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং অজানা জগৎ সম্পর্কেও তাঁদের ছিল গভীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। পবিত্র কুরআনের অনুপ্রেরণায় মুসলিমরা সবসময় নতুন নতুন ভূমি, জাতি, ভূখণ্ড ও সৃষ্টির নিদর্শন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন।
আজকের প্রচলিত পশ্চিমা ইতিহাসে ক্রিস্টোফার কলম্বাস-কে এমন একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যিনি ১৪৯২ সালে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ‘নতুন পৃথিবী’ (আমেরিকা মহাদেশ) আবিষ্কার করেন। তবে এই তথাকথিত “আবিষ্কার”-এর বয়ানটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ, কলম্বাসের আগেই বহু প্রমাণ-সমৃদ্ধ মুসলিম অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় যা এই তথ্যে পরিবর্তন আনার দাবি রাখে।
ইতিহাসবিদরা এখন স্বীকার করছেন যে ১০ম শতাব্দীতেই ভাইকিংরা উত্তর আমেরিকার (আজকের কানাডা) উপকূলে পৌঁছেছিল। এর মানে হচ্ছে, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অভিযানের বহু আগেই মানুষ ‘নতুন পৃথিবী’ সম্পর্কে জানত। আর ভাইকিংদেরও পূর্বে মুসলিম নাবিকদের বহু আটলান্টিক যাত্রার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে মুসলিম ভূগোলবিদদের লেখায়।
আল-মাসউদির অভিযাত্রার বিবরণ
প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ আবুল হাসান আল-মাসউদি (৮৯৫–৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর লেখায় ১০ম শতকের মাঝামাঝি মুসলিমদের একটি আটলান্টিক অভিযানের বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দেই মুসলিম আইবেরিয়া থেকে ‘দেলবা’ বন্দরের দিকে একটি নৌবহর পশ্চিমে যাত্রা শুরু করে। সেখানে পৌঁছে তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং পরে নিরাপদে ফিরে আসে।
এ ছিল এক প্রামাণ্য উল্লেখ, যা থেকে বোঝা যায়—কলম্বাসের বহু শতাব্দী আগেই মুসলিমরা আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেছিলেন এবং ‘নতুন জগতের’ দ্বার খুলে দেন।
আল-ইদরিসির লেখায় মুসলিম অভিযাত্রার চমকপ্রদ তথ্য
পরবর্তীকালে বিশ্বখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ আল-ইদরিসি তাঁর পুস্তকে আরও এক অভিযানের বিবরণ দেন। সেখানে বলা হয়, মুসলিমদের একটি নৌদল ৩১ দিন আটলান্টিকে ভেসে থাকার পর এক অজানা দ্বীপে নোঙর ফেলে। দ্বীপের অধিবাসীরা তাদের বন্দি করে নিলেও, সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় একজন আরবি ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তি তাদের মুক্ত করে দেয়।
এই বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, মুসলিম বিশ্বে আটলান্টিক-অভিযান ও ‘নতুন দেশ’ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা বহু পূর্বে থেকেই বিদ্যমান ছিল।
ইবনে বতুতার বর্ণনায় মালির অভিযান
আরেক বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায় ইবনে বতুতা (রহ.)-র ভ্রমণ বিবরণ থেকে। তিনি লিখেছেন, পশ্চিম আফ্রিকার মালি সালতানাতের শাসকরা ২০০টি জাহাজের একটি বিশাল বহর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে অজানা দেশে পাঠিয়েছিলেন। ঝড়ের কারণে একটি মাত্র জাহাজ ফিরে আসতে সক্ষম হয়, যার বিবরণ পেয়ে রাজার আগ্রহ আরও বাড়ে এবং তিনি আরও জাহাজ অভিযানে পাঠান। তবে তাদের গন্তব্য ও পরিণতির তথ্য ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়নি।
তবুও এই বর্ণনা প্রমাণ করে—মুসলিম শাসকেরা শুধু জ্ঞানার্জনে নয়, ভৌগোলিক অভিযাত্রায়ও সাহসী ও সক্রিয় ছিলেন।
পশ্চিমা ইতিহাসের একচোখা বয়ান ও মুসলিমদের বিস্মৃত অবদান
দুঃখজনকভাবে, এইসব মুসলিম অভিযানের ইতিহাস আড়ালেই থেকে গেছে। ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত তথাকথিত আধুনিক ইতিহাসে শুধু ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের ‘আবিষ্কার’ই গুরুত্ব পায়। ফলে আজকের পাঠ্যপুস্তকে ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা বা ম্যাগেলান-এর নাম যতটা উচ্চারিত হয়, মুসলিম অভিযাত্রীদের নাম ততটাই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।
আমরাও এই ইতিহাসের ফাঁক গলে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ভুলে গেছি এবং পশ্চিমা বিভ্রান্তিকর ইতিহাস-কেই গ্রহণ করে ফেলেছি।
মুসলিম পণ্ডিতগণ, কুরআনের অনুপ্রেরণায় মহাকাশ বিজ্ঞানের জগতে যেভাবে চিন্তা ও প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তা শুধু ধর্মীয় চেতনায় নয়, বরং মানব সভ্যতার গতি ও দিক নির্ধারণে এক অবিচ্ছেদ্য অবদান। তাঁদের কাজ শুধু বিজ্ঞান নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টি অনুধাবনের এক ফিকরি আমল হয়ে ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে আছে।
যদি আমরা মুসলিম সভ্যতার এই ভূগোল, সমুদ্র অভিযাত্রা ও ভূখণ্ড আবিষ্কারের গৌরবময় অধ্যায়গুলো গবেষণা ও প্রচারের মাধ্যমে পুনরায় বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে পারি, তবে আজ প্রচলিত ইতিহাসের অনেক ভুল ধারণাই পুনর্লিখনযোগ্য হয়ে উঠবে।
এটাই হবে ইলম, ইতিহাস ও ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রকৃত প্রচেষ্টা।
ইসলামী সভ্যতায় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ ও আল রাজির অবদান
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা হলো—চিকিৎসাশাস্ত্র কেবল অনুমাননির্ভর কিছু প্রচলিত পদ্ধতি কিংবা হাতুড়ে চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। অনেক শিক্ষিত মানুষও বিংশ শতাব্দীর আগের চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা ভাবলে কল্পনায় তুলে আনেন এক সরল গ্রাম্য চিকিৎসকের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস ভিন্ন।
ইতিহাস প্রমাণ করে, ইসলামী সভ্যতায় চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল একটি উন্নত ও গবেষণানির্ভর শাস্ত্র। প্রাথমিকভাবে মুসলিম পণ্ডিতরা প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসাবিদদের জ্ঞানকে অনুবাদ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আত্মস্থ করেন। তবে শুধু গ্রিকদের উপর নির্ভর না থেকে তাঁরা এই জ্ঞানকে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেন, বহু মৌলিক তত্ত্ব ও চিকিৎসাপদ্ধতির সূচনা করেন—যার প্রভাব আজও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বহন করে চলেছে।
চিকিৎসায় পেশাগত মান ও নিয়ন্ত্রণ
৯ম–১০ম শতাব্দীর মধ্যেই বাগদাদে চিকিৎসক হতে হলে নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এটি ছিল ইতিহাসে প্রথম চিকিৎসক লাইসেন্সিং সিস্টেম, যা দেখায় যে চিকিৎসাবিদ্যাকে মুসলিম সমাজে কতটা পেশাগত ও নৈতিক কাঠামোর মধ্যে রাখা হয়েছিল।
গ্যালেনের তত্ত্ব এবং মুসলিমদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি
প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসাবিদ গ্যালেন (২য় শতাব্দী) মনে করতেন, মানুষের শরীর মূলত চারটি ‘ধাতু’ বা শরীরবৃত্তীয় উপাদান নিয়ে গঠিত: রক্ত, কালো পিত্ত, হলুদ পিত্ত এবং কফ। তার মতে, এই চার উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হলেই মানুষ অসুস্থ হয়। এই তত্ত্ব প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসার মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
তবে এই তত্ত্বেই প্রথম চ্যালেঞ্জ আনেন নবম শতাব্দীর মুসলিম চিকিৎসাবিদ মুহাম্মাদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি (রহ.)। তিনি ছিলেন বাগদাদের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক, দার্শনিক ও শিক্ষক। আল রাজি তাঁর “Doubts about Galen” (আরবি: الشُكوك على جالينوس) নামক গ্রন্থে যুক্তিপূর্ণভাবে প্রমাণ করেন যে, মানুষের অসুস্থতার কারণ কেবল ‘ধাতু’-র ভারসাম্যহীনতা নয়; বরং রোগের পেছনে রয়েছে বহুবিধ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণ।
এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি সাধারণ রোগ যেমন জ্বর, কফ, মাথাব্যথা, আমাশয় ইত্যাদির কার্যকর চিকিৎসাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন, যা তাঁর সময়কার চিকিৎসাশাস্ত্রকে এক যুগান্তকারী মোড়ে নিয়ে যায়।
আল রাজি ও চিকিৎসাশাস্ত্রের নৈতিক দর্শন
আল রাজি শুধু একজন চিকিৎসক ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক নৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত আদর্শ চিকিৎসাবিদের প্রতিমূর্তি। তাঁর রচিত “আল-হাওয়ি” এবং “আখলাক আল-তাবিব” নামক গ্রন্থগুলোতে তিনি চিকিৎসকের ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ব ও পেশাগত চেতনা সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করেন।
বিশেষভাবে তাঁর “The Virtuous Life” (তিব্ব বিষয়ক একটি এনসাইক্লোপেডিয়া) গ্রন্থে তিনি বলেন:
> চিকিৎসাশাস্ত্র একটি মহৎ ও মানবিক দায়িত্ব; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের নিকট একটি আমানত। রোগী দরিদ্র হোক বা শত্রু হোক, সেবা পাওয়ার অধিকার তার রয়েছে।
এই বিশ্বাস থেকেই আল রাজি বাগদাদের বড় বড় হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করতেন, যার ফলে তিনি সাধারণ মানুষের মাঝে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।
ইউরোপে প্রভাব ও উত্তরাধিকার
আল রাজির চিকিৎসাবিদ্যা শুধু মুসলিম বিশ্বেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর রচনাসমূহ লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর কাজ পরবর্তী মুসলিম চিকিৎসাবিদদের যেমন ইবনে সিনা, আল-জাহরাওয়ি, ইত্যাদির পাশাপাশি ইউরোপীয় চিকিৎসা-ঐতিহ্যেও প্রভাব বিস্তার করে।
ইসলামী সভ্যতায় চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও নৈতিকতায় ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। আল রাজি ছিলেন সেই আলোকবর্তিকা, যিনি প্রাচীন তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নতুন চিকিৎসাগত চেতনার সূচনা করেন। তাঁর কর্ম ও দর্শন আজও চিকিৎসাশাস্ত্রে আদর্শ মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গেছে।
মুহাম্মাদ ইবন যাকারিয়া আল-রাজি (রহ.): চিকিৎসাশাস্ত্রের পথিকৃৎ
মুহাম্মাদ ইবন যাকারিয়া আল-রাজি (৮৬৫–৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন একজন প্রখ্যাত পারসিক চিকিৎসক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। তিনি শুধু চিকিৎসা নয়, রসায়ন (আলকেমি), পদার্থবিদ্যা, এবং দর্শনসহ বহু বিষয়ের উপর ১৮০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গবেষণাগার ছিল বাগদাদে, যেখান থেকে তিনি যুগান্তকারী আবিষ্কার ও বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারার সূচনা করেন।
প্রযুক্তিগত অবদান:
সালফিউরিক অ্যাসিড আবিষ্কারে তিনি ছিলেন অগ্রগামী, যা পরবর্তী সময়ে রসায়নের মূল উপাদানগুলোর একটি হয়ে ওঠে।
তিনি প্রথম ইথানল (মদ্যপানযোগ্য অ্যালকোহল) উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন এবং এর চিকিৎসায় প্রয়োগের পথ দেখান।
চিকিৎসায় অবদান:
তাঁর রচিত “আল-জুদারী ওয়াল-হাসবাহ” (গুটিবসন্ত ও হাম সম্পর্কে) গ্রন্থটি ছিল বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ, যেখানে এই দুটি রোগকে আলাদা রোগ হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এতে তিনি রোগের লক্ষণ, কার্যকারণ ও চিকিৎসার আলাদা আলাদা দিক ব্যাখ্যা করেন। এই বইটি একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ হয় এবং কয়েক শতাব্দী ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
তিনি নিরাময়যোগ্য ও দুরারোগ্য রোগের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টেনে চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেন।
আল রাজি মনে করতেন, চিকিৎসা হলো একটি ইবাদতসুলভ দায়িত্ব। তাঁর মতে, চিকিৎসককে শত্রু বা দরিদ্র যেকোনো রোগীর প্রতিও সমান সহানুভূতি ও সেবা দিতে হবে, কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি অর্পিত একটি আমানত। এ কারণেই তিনি বাগদাদের হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করতেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়।
ইবনে সিনা (আবু আলী হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা): চিকিৎসাশাস্ত্রে যৌক্তিক বিপ্লব
ইবনে সিনা (৯৮০–১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি ইউরোপে ‘Avicenna’ নামে পরিচিত, ছিলেন ইসলামী স্বর্ণযুগের সবচেয়ে বিখ্যাত বহুবিদ্যাজ্ঞ। ১১শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তিনি পারস্যের এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হলেও, এই সময়েই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ইসলামী জ্ঞানবিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে।
চিকিৎসাশাস্ত্রে যৌক্তিকতার সূচনা:
যেখানে আল রাজি অনেকটা অভিজ্ঞতানির্ভর চিকিৎসা অনুসরণ করতেন, সেখানে ইবনে সিনা চিকিৎসাকে একটি যৌক্তিক ও বিশ্লেষণভিত্তিক বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন—
> “চিকিৎসা হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির সমন্বয়। এখানে কোনো রহস্য নেই, ভাগ্যের স্থান নেই।”
তাঁর গবেষণায় উঠে আসে যে—রোগ শুধুমাত্র শরীরের অভ্যন্তরীণ ব্যাধি নয়, বরং তা পরিবেশগত উপাদান যেমন বাতাস, পানি ও মাটি থেকেও সংক্রমিত হতে পারে। পাশাপাশি তিনি বলেন, প্রতিটি রোগের স্বতন্ত্র উপসর্গ ও আচরণ রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী রোগের চিকিৎসাও হতে হবে পৃথকভাবে।
বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল-কানুন ফিৎ তিব’ (The Canon of Medicine):
ইবনে সিনার সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজ হলো তার পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট চিকিৎসা বিশ্বকোষ – “আল-কানুন ফিৎ তিব্ব”। এটি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
এই বইতে তিনি বলেন,
> “ওষুধের কার্যকারিতা যদি পরীক্ষায় প্রমাণিত না হয়, তবে সেটিকে ওষুধ বলা যায় না।”
তিনি ছিলেন প্রথম চিকিৎসাবিদ, যিনি নিরীক্ষাভিত্তিক ওষুধের প্রয়োগ এবং রোগের ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন
আল রাজি ছিলেন সেই চিকিৎসক যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রকে নৈতিকতা ও সেবার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন, আর ইবনে সিনা সেই মনীষী যিনি চিকিৎসাকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার স্তরে উন্নীত করেন। এই দুই মহান ব্যক্তির অবদান শুধু ইসলামী জ্ঞানভান্ডারেই নয়, বরং সার্বজনীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণে অসামান্য গুরুত্ব বহন করে।
আল-কানুন ফিৎ তিব: মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের অমর দলিল
ইবনে সিনার অমর সৃষ্টি “আল-কানুন ফিৎ তিব্ব” শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয়, বরং গোটা দুনিয়ার চিকিৎসা জগতে চিকিৎসাশাস্ত্রের এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত হতো। খলিফার দরবার হোক কিংবা পাশ্চাত্যের রাজদরবার—এই গ্রন্থ ছিল চিকিৎসাবিদদের হাতে থাকা সর্বাধিক পাঠযোগ্য ও প্রামাণ্য পুস্তক।
আন্তর্জাতিক প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা
১৭তম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এই বইটির ল্যাটিন অনুবাদ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক শিক্ষা অর্জন করতেন। অপরদিকে, ১৩–১৪ শতকে চীনের ইউয়ান সালতানাতের আমলে চীনা মুসলিমরা বইটি চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করে ছড়িয়ে দেন। এভাবে বইটি এক আন্তঃসভ্যতাগত জ্ঞানের সেতুবন্ধন রচনা করে।
বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়বস্তু
এই গ্রন্থে শুধু রোগের উপসর্গ ও প্রতিকার নয়, বরং অন্তর্ভুক্ত ছিল:
অ্যানেসথেশিয়া
স্তন ক্যান্সার
জলাতঙ্ক
আলসার
কিডনি রোগ
যক্ষ্মা
বিষক্রিয়ার চিকিৎসা
শুধু দেহ নয়, ইবনে সিনা মানবমনের রোগ এবং শারীরিক অসুস্থতার মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেন—নেতিবাচক চিন্তা শরীরের ওপর বিষক্রিয়ার মতোই প্রভাব ফেলে। আধুনিক কালে মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড ও কার্ল ইউং যেটা পুনরাবিষ্কার করেন, তার শতাব্দীখানেক আগেই মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ এই যোগসূত্র উদ্ঘাটন করেছিলেন।
মুসলিম শাসকদের চিকিৎসাবিদ্যায় পৃষ্ঠপোষকতা
একজন চিকিৎসক তাঁর গৌরবোজ্জ্বল গবেষণাকে সফল রূপ দিতে পারেন কেবল তখনই, যখন তাঁকে একটি সুষ্ঠু ও সমর্থনশীল কাঠামো প্রদান করা হয়। মুসলিম সালতানাতসমূহের শাসকগণ ঠিক এ কথাটিই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের নিকট চিকিৎসা ছিল শুধু দেহের রোগ সারানো নয়, বরং একটি ইবাদতসুলভ খিদমত। তাই তাঁরা রাষ্ট্রীয় অর্থে নির্মাণ করেন বহুসংখ্যক হাসপাতাল—যা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জনগণের জন্য উন্মুক্ত।
ফুস্তাত হাসপাতাল: ইতিহাসের প্রথম দাতব্য মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্র
৮৭২ হিজরিতে মিসরের তৎকালীন গভর্নর আমির আহমদ ইবনে তুলুন, ফুস্তাত নগরে একটি আধুনিক মানের বিমারিস্তান (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ব্যয় হয় প্রায় ৬০,০০০ স্বর্ণদিনার। শুধু শারীরিক চিকিৎসাই নয়, এই প্রতিষ্ঠানে মানসিক রোগীদের জন্যও আলাদা বিভাগ চালু করা হয়—যা আজকের দিনেও বিরল বিষয়।
হাসপাতালের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
তৎকালীন মুসলিম জগতে গড়ে ওঠা হাসপাতালসমূহে যা থাকত:
বহির্বিভাগ
গর্ভবতী নারীদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড
অপারেশন থিয়েটার
মানসিক রোগীদের আলাদা ওয়ার্ড
প্রশিক্ষিত নার্স, সার্জন ও হেকিম
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—এই হাসপাতালগুলো সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিত। আজ যেখানে চিকিৎসা বাণিজ্যিকীকরণের চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে, সেখানে মুসলিম যুগের এই দাতব্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ছিল ইসলামী সমাজনীতির বাস্তব প্রয়োগ।
বাগদাদ, দামেস্ক, কায়রো, মক্কা-মদিনা, আইবেরিয়া, গ্রানাডা—এসব শহরে নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে উসমানী খিলাফতে এই ঐতিহ্য আরও জাঁকজমকভাবে অব্যাহত থাকে। উসমানীয়দের কাছ থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ‘Public Hospital’ ধারণাটি পৌঁছে যায়।
ইবনে সিনা ও আল রাজির মতো মহামনীষীরা ছিলেন না কেবল চিকিৎসাবিদ, বরং তাঁরা ছিলেন ইসলামী ইলম ও খিদমতের ধারক ও বাহক। তাঁদের রেখে যাওয়া জ্ঞান ও আদর্শ আজকের আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও মুসলিম সভ্যতার গোপন অনুপ্রেরণা
ইউরোপের তথাকথিত রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণকালে—যেটিকে আজকের পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রারম্ভিক ধাপ হিসেবে ধরা হয়—তখন মূলত মুসলিম জ্ঞানসম্পদকেই তারা পুনরাবিষ্কার করেছিল। পাদুয়া, বলোনিয়া, সালের্নো, কর্ডোভা, গ্রানাডা, তোলেদো—এইসব শহরগুলোতে মুসলিম চিন্তাবিদদের আরবি গ্রন্থাবলিকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছিল। আর এর সূত্র ধরেই গড়ে ওঠে ইউরোপের প্রথম দিককার বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্র।
বিশেষ করে ইবনে সিনা ও আল রাজির চিকিৎসা-দর্শন ইউরোপের চিকিৎসাশাস্ত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। পশ্চিমা বিশ্ব আজ যে আধুনিক চিকিৎসা, হাসপাতাল, ও গবেষণাকেন্দ্র নিয়ে গর্ব করে—এর মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল মুসলিমদের সোনালি যুগে, ইসলামি সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকতায়।
কিন্তু আজ সেই ইতিহাসকে ধূসর করে ফেলা হয়েছে। একটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আরেক সভ্যতার অবদান অস্বীকার করে দেওয়া হয়েছে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করা হয়েছে। এই সত্যকে উদ্ঘাটন করা আমাদের ইলম ও হকের দায়।
পদার্থবিদ্যা: ইলমুন ফিজিয়া ও মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক বৈপ্লবিকতা
আল কায়েনাত (সৃষ্টিজগত) সম্পর্কে তাওহিদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যখন কোনো মুসলিম চিন্তাবিদ গবেষণা শুরু করেন, তখন তিনি তা করেন আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য অনুধাবনের এক ইবাদতসুলভ আন্তরিকতা থেকে। এ চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা গণিতকে ভিত্তি করে পদার্থবিজ্ঞানের (Ilm al-Tabi’ah) বহু জটিল সূত্র উদ্ভাবন করেন।
প্রাচীন জ্ঞানচর্চার উত্তরাধিকার ও তার নবজাগরণ
প্রথমে মুসলিমরা গ্রিক, পারস্য, ভারতীয় জ্ঞানধারার অনুবাদ করেন, পরে সেই অনুবাদিত জ্ঞানকে কেবল ধারণ করেই থেমে থাকেননি—বরং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করান। এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন:
ইবনুল হাইসাম: অপটিকসের জনক ও নিরীক্ষার পথপ্রদর্শক
ইবনুল হাইসাম (৯৬৫–১০৪০) ছিলেন বাসরা-নিবাসী একজন মুহাক্কিক (গবেষক), হাকিম (দার্শনিক) ও ফালাসিফা (বিজ্ঞানী)। প্রাথমিকভাবে তিনি আব্বাসীয় প্রশাসনে কর্মরত ছিলেন, পরে সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন এবং জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে মিশরে ফাতেমীয় খিলাফতের অন্তর্গত এক কেন্দ্রীয় নগরীতে যান।
ফাতেমীয় শাসকের সন্দেহের কারণে একটি বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় থাকা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেই গৃহবন্দি অবস্থাতেই তিনি শুরু করেন আলোর প্রকৃতি ও দৃষ্টির কার্যপ্রণালি নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা। এবং সেখান থেকেই জন্ম নেয়:
> “কিতাব আল-মানাজির” (Book of Optics) — যেটিকে আধুনিক অপটিকসের ভিত্তিগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।
ইবনুল হাইসামের বৈপ্লবিক আবিষ্কারসমূহ:
চোখ দেখে কীভাবে বস্তু বোঝে—এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।
গ্রিক চিকিৎসাবিদরা মনে করত—চোখ থেকে আলো বের হয় এবং বস্তুকে ছুঁয়ে আসে।
কিন্তু ইবনে হাইসামই প্রথম সঠিক ব্যাখ্যা দেন—বস্তুর উপর আলো পড়ে এবং তা প্রতিফলিত হয়ে চোখে প্রবেশ করে, তবেই আমরা দেখতে পাই।
আলো সোজা পথে চলে—এটি তিনি প্রমাণ করেন একটি গোপন চেম্বার বা “কামরা” নির্মাণ করে। এই চেম্বারকেই আধুনিক ক্যামেরার পূর্বসূরি হিসেবে ধরা হয়।
প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের নিয়ম তিনি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করেন, যা পরবর্তীতে আধুনিক লেন্স ডিজাইন, চশমা, টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
তিনি ‘বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি’ বা সায়েন্টিফিক মেথড-এর অন্যতম পূর্বসূরি। পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন উত্থাপন, অনুমান, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ—এই ধাপে ধাপে কাজ করাই ছিল তার মূলনীতি।
ইবনুল হাইসাম ও আলোর রহস্য: ইসলামি সভ্যতার অপটিকস বিপ্লব
মানব ইতিহাসে ‘আলো’ সবসময়ই রহস্যঘেরা একটি বিষয় ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিকেরা আলো কী এবং কীভাবে আমরা বস্তুকে দেখি—তা নিয়ে নানা রকম ধারণা পেশ করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত মত ছিল গ্রিক দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমির তত্ত্ব, যার মতে চোখ থেকেই আলো নির্গত হয়, পরে তা বস্তুর ওপর পড়ে প্রতিফলিত হয়ে আবার চোখে ফিরে আসে—ফলে আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।
এই ধারণাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রিক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ইসলামি স্বর্ণযুগে, আল্লাহর কুদরতের রহস্য উন্মোচনের তাওহিদী স্পৃহায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইবনুল হাইসাম (রহ.) এই ভুল ধারণার মূলোচ্ছেদ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মুহাক্কিক—যিনি দার্শনিক জল্পনা নয়, বরং পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণকেই ইলম অর্জনের প্রকৃত উপায় বলে বিশ্বাস করতেন।
ইবনুল হাইসাম আলোর প্রকৃতি ও গতি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা ও নিরীক্ষা চালান। তিনি লক্ষ করেন—চোখ নয়, বরং বস্তু থেকেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। এই প্রতিফলিত আলোর অসংখ্য রশ্মি একসাথে চোখে প্রবেশ করে, আর তার ভিত্তিতে মস্তিষ্ক বস্তুর চেহারা ও রঙ সনাক্ত করে।
তাঁর গবেষণারই ফল আল-কিতাব আল-মানাযির (ইংরেজিতে Book of Optics)—যেটি পরবর্তীতে শত শত বছর ধরে ইউরোপের পাঠ্যবই হয়ে ওঠে এবং মডার্ন অপটিকসের ভিত্তিশিলা স্থাপন করে। বইটিতে তিনি প্রমাণ করেন:
আলো সবসময় সোজা পথে চলে।
আলো হলো রশ্মির একটি ধারা, যা বস্তুর গায়ে পড়ে প্রতিফলিত হয়ে চোখে প্রবেশ করে।
দৃষ্টিশক্তি হলো চোখে আসা আলোর প্রক্রিয়ার ফল, না যে চোখ থেকে আলো বের হয়।
ক্যামেরার সূচনা: কামরা অবসকিউরা
এই বৈজ্ঞানিক ধারণার বাস্তব প্রয়োগেই ইবনুল হাইসাম আবিষ্কার করেন “ক্যামেরা অবসকিউরা” (Camera Obscura)। এটি একটি অন্ধকার বাক্স, যার এক পাশে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র থাকে। ওই ছিদ্র দিয়ে বাইরের দৃশ্যের আলো বাক্সে প্রবেশ করে এবং বিপরীত দেয়ালে উল্টোভাবে চিত্র তৈরি করে। আধুনিক ফটোগ্রাফির ধারণা মূলত এখান থেকেই এসেছে। পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা এই পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে লেন্স সংযোজন করে আধুনিক ক্যামেরা তৈরি করে।
তবে ইবনুল হাইসাম এই যন্ত্রটি নির্মাণ করেছিলেন আধুনিক ফটোগ্রাফির জন্মেরও প্রায় ১০০০ বছর আগে। অথচ, আজকের পাঠ্যবইগুলোতে আমরা অনেক সময় এই কৃতিত্ব ভুল করে অন্যের নামে আরোপিত হতে দেখি।
একই সময় পারস্যে ইবনে সিনা (রহ.) চোখের গঠন ও আলো কিভাবে চোখের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে, সে সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ফলে মুসলিম জ্ঞানবিজ্ঞানীরা পৃথক জায়গা থেকে সমান্তরাল গবেষণার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব দাঁড় করাতে সক্ষম হন। কেউ আলোর উৎস ব্যাখ্যা করেন, কেউ চোখের গঠন। এভাবেই মুসলিম সভ্যতার বুকে একটি স্বর্ণযুগ গড়ে উঠছিল—যেখানে চিন্তকরা কেবল নিজেদের খ্যাতির জন্য নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টিজগতের রহস্য অনুধাবনের জন্য কাজ করতেন।
বায়ুমণ্ডল ও সূর্যাস্তের আলো: পদার্থবিদ্যায় দিক পরিবর্তন
ইবনুল হাইসাম তাঁর অপটিকস জ্ঞানকে শুধু চোখ ও আলোয় সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি সূর্যাস্তের সময় আকাশের রঙ পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখান যে, আলোর প্রতিসরণ (refraction) এবং বায়ুমণ্ডলের গঠন-এর কারণে সূর্যাস্তে লালচে আভা দেখা যায়। তিনি বুঝতে পারেন, সূর্য যখন দিগন্তে নেমে আসে, তখন আলো বায়ুমণ্ডলের ভিন্ন ঘনত্বের স্তরে প্রবেশ করে ও বাঁকা হয়ে আসে—ফলে আমরা সূর্যকে কিছুটা অন্যরকম রঙে দেখি।
এই আবিষ্কার পরবর্তীতে মহাকাশবিজ্ঞান, স্যাটেলাইট পাঠানো এবং সৌর বিশ্লেষণ-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেক শতাব্দী পরে নাসা ও সোভিয়েত মহাকাশ গবেষণা সংস্থা যখন এসব বিষয়ে গবেষণা চালায়, তখন ইবনুল হাইসামের গবেষণাগুলোকেই প্রমাণিত সত্য হিসেবে দেখতে পায়।
ইবনুল হাইসাম ছিলেন শুধু একজন পদার্থবিদ নয়, বরং একজন আল্লাহর সৃষ্টিজগতের গবেষক (মুহাক্কিক), যিনি চেয়েছিলেন ইলমের মাধ্যমে হাক্ক ও হিকমাহ খুঁজে পেতে। তাঁর মতো মুসলিম চিন্তাবিদরাই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য সেই সেতু নির্মাণ করেন, যেটি ধরে হেঁটেই নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইনরা তাঁদের আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হন।
ইবনুল হাইসাম ও মুসলিম প্রযুক্তিবিপ্লব: বিজ্ঞানচর্চার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
ইবনুল হাইসাম (রহ.) ছিলেন এমন এক মহান মনীষী, যাঁর জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও আবিষ্কার নিয়ে বহু ভলিউম গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। ইতিহাসবিদদের মতে, তিনি দুই শতাধিক পাণ্ডুলিপি ও কিতাব রচনা করেন, যদিও সময়ের অতলে আজ মাত্র কয়েক ডজনই আমাদের হাতে রয়েছে। তিনি শুধু অপটিকস বা ‘আলোর বিজ্ঞান’-এ নয়, বরং চুম্বকীয়তা, গতি (Dynamics), ক্যালকুলাস, জ্যামিতি, মহাকাশবিদ্যা, পরীক্ষালব্ধ মনোবিজ্ঞান—এমনকি দর্শন ও ইসলামী চিন্তাচর্চায়ও অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।
তার জ্ঞানসাধনার গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব কেবল তখনই, যখন কেউ এসব শাস্ত্রের মধ্যে আসলেই একনিষ্ঠভাবে প্রবেশ করে। বিজ্ঞান, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা—এই তিনের সম্মিলনে গঠিত ছিল ইবনুল হাইসামের চিন্তার জগত। তিনি শুধু একের পর এক নতুন আবিষ্কার করেননি, বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ‘ইলম’ অর্জনের যে পদ্ধতি তিনি দাঁড় করিয়েছেন, তা-ই আজকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিমূল।
“ইলম” ও “হাকিকাত” অর্জনের ইবাদত
ইবনুল হাইসামের কাছে গবেষণা কোনো খালি বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যায়াম ছিল না, বরং তাওহিদের পথচলার একটি অংশ। তিনি বলেন:
> “আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে সব সময় জ্ঞান ও সত্যকে জানার চেষ্টা করেছি। আর এটা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আল্লাহকে জানার জন্য, তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সত্য ও জ্ঞানকে অনুসন্ধান করার চেয়ে উত্তম কোনো উপায় আর হতে পারে না।”
এই বাক্য একদিকে যেমন ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে, অন্যদিকে তা ইসলামি সভ্যতার ইলম ও তাদাব্বুর-নির্ভর বৈজ্ঞানিক ধারাকে বুঝতেও সাহায্য করে।
আল-জাযারির প্রযুক্তিবিপ্লব
ইবনুল হাইসামের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন ইসমাইল আল-জাযারি (রহ.)। দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি ছিলেন মুসলিম জগতের এক বিস্ময়কর মুফাক্কির ও প্রকৌশলী। তিনি নির্মাণ করেন:
অটোমেটিক হাত ধোয়ার যন্ত্র
পানিচালিত যন্ত্রচালিত ঘড়ি
প্রাক-মডার্ন রোবট (Musical Robot)
এই যন্ত্রগুলো শুধু কল্পনাপ্রসূত খেলনা ছিল না; বরং প্রকৃত ব্যবহারিক প্রয়োজনেই এগুলো উদ্ভাবিত হয়েছিল। তাঁর রচিত কিতাব “আল-জামি’ বাইন আল-ইলম ওয়াল-আমাল আল-না’ফি’ ফি সানা’আত আল-হিয়াল” (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices) আধুনিক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পূর্বসূরি বলেই বিবেচিত।
মুসলিমদের প্রযুক্তিগত বিপ্লব
ইবনুল হাইসাম ও আল-জাযারির রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৩ শতকের মধ্যেই মুসলিম জগতে জন্ম নেয় প্রযুক্তির এক বিপ্লব। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল:
ক্র্যাঙ্কশ্যাফট (যা আধুনিক ইঞ্জিনের পূর্বসূরি)
চশমা বা অপটিক্যাল লেন্স
কম্পাস ও নেভিগেশন যন্ত্র
ইঞ্জিনবিহীন বিমান নকশা (আব্বাস ইবনে ফিরনাস)
আধুনিক রাসায়নিক গবেষণাগারের রূপরেখা (জাবির ইবনে হাইয়ান)
হাসপাতাল-ভিত্তিক মেডিকেল ইন্সটিটিউশন
স্বয়ংক্রিয় মেশিন ও পানিচালিত অটোমেশন
এসবের প্রতিটি উদ্ভাবনই মানবসভ্যতার উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। অথচ এসবকেই আজ অনেক সময় ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ‘পূর্ব প্রস্তুতি’ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, মুসলিম অবদানকে গৌণ করে রেখে।
ইতিহাসচর্চায় উপেক্ষিত এক বাস্তবতা
যখন ক্রুসেডার বাহিনী মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসন চালায়, আর মোঙ্গল বাহিনী বাগদাদের মতো তৌহিদী জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান ধ্বংস করে দেয়, তখনই মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার ধারা মন্থর হয়ে পড়ে। এরপরই শুরু হয় ইউরোপীয় ‘রেনেসাঁ’। অথচ ইউরোপের রেনেসাঁর বহু পণ্ডিত—কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ—প্রকাশ্যে বা নীরবে আরবি ভাষায় অনূদিত মুসলিম বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ থেকে উপকৃত হন। বিশেষ করে ইবনুল হাইসাম, ইবনে সিনা, আল রাজি, আল-খারিজমি—তাঁদের চিন্তাধারাই ছিল পরবর্তীতর ‘পশ্চিমা বিজ্ঞানযাত্রার’ ভিত্তি।
মুসলিম সভ্যতা যে শুধু ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতা দিয়েই জাগতিক বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে তা নয়; বরং তার গৌরবোজ্জ্বল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জ্ঞানতত্ত্বও আজকের আধুনিক বিশ্বকে নির্মাণে মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করেছে।
ইবনুল হাইসামের মতো মনীষীদের অনুসরণ করে যদি আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ইলমকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে, তবে একদিন হয়তো আমরা আবার সেই হারিয়ে যাওয়া তাওহিদী জ্ঞান-সভ্যতার পুনর্জাগরণ দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।