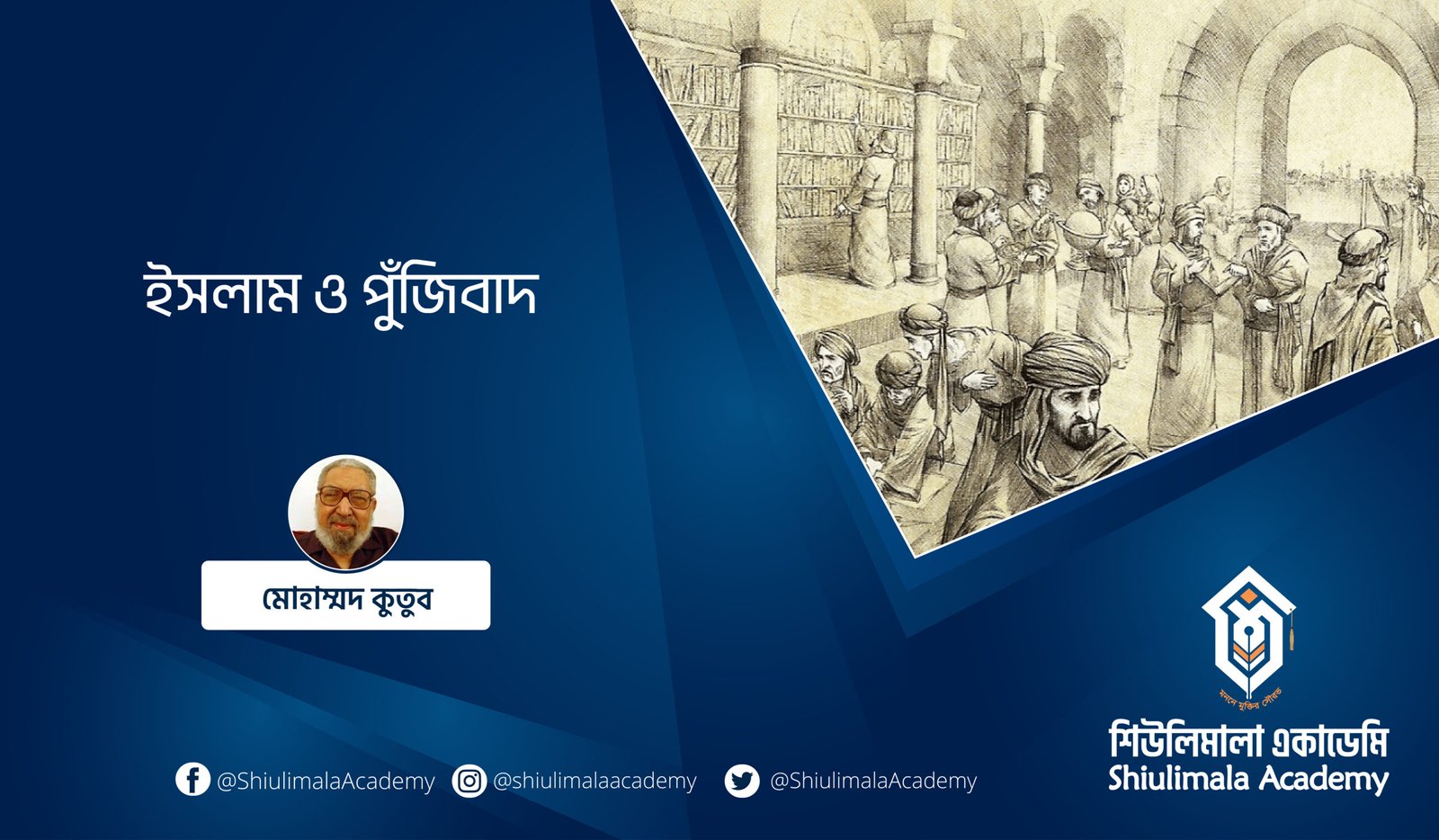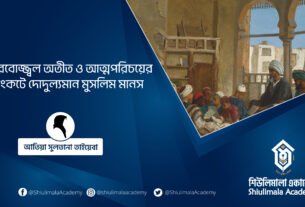পুঁজিবাদের জন্ম মুসলিম বিশ্বে হয়নি। পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে যন্ত্র আবিষ্কারের পর-আর এটি ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছিল ইউরোপে।
মুসলিম বিশ্বে পুঁজিবাদ আমদানী করা হয় এমন একটা সময়ে, যখন ইহা ইউরোপীয় শাসনাধীনে ছিল। মুসলিম বিশ্ব যখন দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য ও পশ্চাদপদতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল-উন্নয়নের নামে তখন এখানে পুঁজিবাদের প্রসার সাধন করা হয়। এ কারণে কতক লোক মনে করে, ভাল-মন্দ নির্বিশেষে গোটা পুঁজিবাদকেই ইসলাম সমর্থন করে। তারা আরও মনে করে যে, ইসলামী আইন বা ব্যবস্থায় এমন কোন বিধান নেই যা পুঁজিবাদের বিরোধী। তারা যুক্তি দেখার, ইসলাম যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দেয়, সুতরাং ইহা পুঁজিবাদেরও অনুমতি দেবে।
‘এই অভিযোগের জবাবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সূদ ও মনোপলি ছাড়া পুঁজিবাদ গড়ে উঠতে পারে না, আর পুঁজিবাদের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্বেই ইসলাম এগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।।
প্রশ্নটির আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। যন্ত্রের আবিষ্কার যদি মুসলিম বিশ্বে ঘটত তবে এরূপ আবিষ্কার-জনিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ইসলাম কিভাবে মুকাবেলা করত? শ্রম ও উৎপাদন সংগঠনে ইসলামী বিধান ও আইন কিভাবে প্রয়োগ করা হত?
কার্ল মার্কস প্রভৃতি ধনতন্ত্র-বিরোধী সহ প্রায় সকল অর্থনীতিবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, প্রথম দিকে মানবতার অগ্রগতি ও কল্যাণে পুঁজিবাদের যথেষ্ট অবদান ছিল। এতে উৎপাদন বেড়ে যায়, যোগাযোগ-ব্যবস্থার মান উন্নত হয় এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির হারও বেড়ে যায়। শ্রমজীবীদের জীবন-মান কৃষি-নির্ভর পর্যায়ের অবস্থা থেকে অনেক উন্নত হয়।
কিন্তু এই গৌরবজনক চিত্র বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এর কারণ স্বরূপ মনে করা হয়, পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে পুঁজিপতি মালিকদের হাতে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং শ্রমিক শ্রেণীর সম্পত্তি হ্রাস পেতে
থাকে। এর ফলে পুঁজিপতি মালিকরা কম্যুনিস্ট দৃষ্টিতে যারা প্রকৃত উৎপাদক সেই শ্রমিকদের ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হল। কিন্তু শ্রমিকদের এত কম মজুরী দেওয়া হল যে, তার দ্বারা কিছুতেই সুন্দর জীবন-যাপন সম্ভব নয়। অপরদিকে মালিকর। সমস্ত সুনাফা লুণ্ঠন করে বিলাস ও দুর্নীতির স্রোতে গা ঢেলে দিল।
এছাড়া শ্রমজীবীদের মজুরী অত্যন্ত কম হওয়ার দরুন পুঁজিবাদী দেশসমূহের সমস্ত উৎপাদন ভোগ করবার শক্তি তাদের হয়ে উঠল না। এর ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সঞ্চয় জমে উঠল। তার পরিণতিতে পুঁজিবাদী দেশসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য নতুন বাজার খোঁজ করতে শুরু করল। এমনি করে উদ্ভব হল উপনিবেশবাদের এবং তার সাথে বাজার ও কাঁচামালের প্রশ্নে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা বিরামহীন দ্বন্দ্ব। এসবেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ দেখা দিল ধ্বংসকারী যুদ্ধ।
তাছাড়া ধনতন্ত্রী ব্যবস্থা মাঝে মাঝে প্রায়ই মন্দা-জনিত সংকটাবস্থার সম্মুখীন হয়। ক্রমবধিষ্ণু উৎপাদনের তুলনায় আন্তর্জাতিক ভোগের পরিমাণ হ্রাসের ফলেই এই মন্দার সৃষ্টি হয়।
সমূহবাদের কোন কোন প্রচারবিদ ধনবাদী ব্যবস্থার সমস্ত সমস্যার জন্য পুঁজিপতির অন্যায় মনোভাব বা শোষণমূলক মনোবৃত্তির পরিবর্তে পুঁজির উপরই সমস্ত দোষ চাপাতে চেষ্টা করেন। এ ধরনের অযৌক্তিক ও অদ্ভুত যুক্তি শুনে মনে হয়, মানুষের অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি যতই থাকুক, সে যেন অর্থনীতির হাতে একটি অসহায় পুতুল মাত্র।
এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, ধনবাদ তার প্রথম দিকে যে সব নির্দোষ ও প্রগতিশীল কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, ইসলাম হয়ত সেগুলো অনুমোদন করত। কিন্তু শিল্প-সংগঠন এবং মালিকদের অসৎ মনোভাব বা পুঁজির মূল প্রকৃতিতে যে শোষণের সম্ভাবন। নিহিত রয়েছে, তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন না করে ইসলাম কিছুতেই পুঁজিবাদকে অবাধে বেড়ে উঠবার সুযোগ দিত না। এ সম্পর্কে ইসলামের নীতিতে মালিকদের সাথে শ্রমিকদেরও মুনাফার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন কোন মালিকী আইনজ্ঞ তো মালিকের সাথে শ্রমিকদের সমান মুনাফার অধিকারই স্বীকার করেছেন। মালিক সমস্ত পুঁজি সরবরাহ করে, আর শ্রমিক কাজ করে-উভয় প্রকার প্রচেষ্টাই সমান বলে তারা মুনাফারও সমান অংশের হকদার।
উপরোল্লিখিত নীতি থেকে ইনসাফ কায়েমে ইসলামের ব্যগ্রতা অনুধাবন করা যায়। ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় এই তাগিদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই ইসলাম রূপায়িত করেছিল। কোন অর্থনৈতিক জরুরী পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে যে এটা চাপান হয়েছিল তা নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের পরিণতিতেও এটা আসেনি-যদিও কোন কোন অর্থনৈতিক মতবাদের প্রচারকরা অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশে এই সংগ্রামকেই একমাত্র কার্যকরী নিয়ামক বলে মনে করেন।
শুরুর দিকে শিল্প বলতে বোঝায় সহজ দৈহিক শ্রম-ছোট ছোট কারখানার ক্ষুদ্র সংখ্যক শ্রমিক তা সম্পন্ন করত। উপরোল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে সেখানে শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সম্পর্ক ইনসাফের ভিত্তিতে নির্ণীত হত-যা ইউরোপে কখনও দেখা যায়নি।
অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, জাতীয় ঋণের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার ফলেই পুঁজিবাদ তার প্রাথমিক কল্যাণময়ী পর্যায় থেকে আজকের করিষ্ণু অকল্যাণকর স্তরে উপনীত হয়েছে। এর ফলে ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় আর এই ব্যাঙ্কই অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করে এবং সূদের বিনিময়ে অর্থ ধার দেয়। এইসব ঋণদান এবং ব্যাঙ্ক-কর্ম-সূচীর ভিত্তি হচ্ছে সূদ, যা ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।
অপরপক্ষে পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কঠোর প্রতিযোগিতা, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানীর ধ্বংস সাধন করে বা নিদেনপক্ষে এগুলো একত্রিকরণের মাধ্যমে বৃহৎ কোম্পানী গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। এর ফলে গড়ে ওঠে মনোপলি। এই মনোপলিও ইসলামে নিষিদ্ধ। রসূল (সা)-এর বেশ কয়েকটি হাদীসেই এর প্রমাণ মিলে। রসূল (সা) বলেছেন: “একচেটিয়া কারবারী জালিম।” ইসলাম যেহেতু গোড়াতেই সুদ ও মনোপলি নিষিদ্ধ করেছে-সুতরাং শোষণ, উপনিবেশ- বাদ ও যুদ্ধের প্রতীক পুঁজিবাদ ইসলামের আওতাধীনে কিছুতেই তার বর্তমান অশুভ পর্যায়ে বেড়ে উঠবার অবকাশ পেত না।
ইসলামী শাসনাধীনে শিল্পের উদ্ভব ঘটলে তার পরিণতি কি হত?
ইসলাম নিশ্চয়ই মালিক-শ্রমিকের মুনাফায় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজনে শিল্পকে ক্ষুদ্র কারখানার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখত না। উৎপাদন বৃদ্ধি করা হত; তবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তার থেকে পৃথক ধরনের সম্পর্ক এখানে গড়ে তোল। হত। হয়ত মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মুনাফার সম-বন্টনের যে নীতি উপরে উল্লিখিত হয়েছে ইসলামের সে ধরনের কোন মূলনীতির ভিত্তিতেই সেই সম্পর্ক পড়ে উঠত।
• এতে করে ইসলাম সূদ ও মনোপলির আশ্রয় গ্রহণ পরিহার করত এবং ধনতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকরা যে ধরনের নির্যাতন ও শোষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও অবমাননা সহ্য করতে বাধ্য হয় তাও ইসলাম বর্জন করতে পারত।
এটা কল্পনা করা আহাম্মকী হবে যে, কঠোর পরীক্ষা, শ্রেণীসংঘর্ষ ও অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যম ছাড়া ইসলাম এ ধরনের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারত না এবং এসব করতে গিয়ে তার বিধান সংশোধনের প্রয়োজন হত। এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও প্রাথমিক পর্যায়ের পুঁজিবাদের সমস্যাবলীর মুকাবিলায় ইসলাম অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অগ্রণী ছিল। এ কাজে ইসলাম বাইরের চাপ দ্বার। প্রভাবিত হয়নি। বরং এ কাজ ইসলাম সম্পূর্ণ স্বাধীন- ভাবেই এর নিজস্ব চিরন্তন ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতেই করেছে, যদিও এ ব্যাপারে কম্যুনিস্ট লেখকরা চিরকাল বিদ্রূপ করে আসছে। অপরদিকে ইহা বাস্তব সত্য যে, অন্যতম আদর্শ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়া সামন্তবাদের স্তর থেকে পুঁজিবাদের মধ্যবর্তী পর্যায়ের মধ্যে না গিয়েই কম্যুনিজমে পৌঁছেছে। এমনিভাবে রাশিয়া কার্ল মার্কসের আদর্শ গ্রহণ করে বিকাশের স্তর সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বকেই মিথ্যা প্রমাণ করেছে। অথচ মার্কসের মতে প্রতিটি রাষ্ট্রই এসব স্তর পেরোতে বাধ্য।
উপনিবেশবাদ, যুদ্ধ ও জনগণের শোষণ সম্পর্কে একথা বলা চলে বে, ইসলাম এগুলো এবং ধনবাদের সৃষ্ট অন্যান্য সব অভিশাপেরই ঘোরতর বিরোধী। অন্যান্য জাতিকে ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা অথবা শোষণের উদ্দেশ্যে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইসলামের নীতি নয়। আক্রমণের মুকাবিলায় অথবা এমন পরিস্থিতিতে যখন শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর বাণী প্রচারের পথ জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, শুধু তখনই ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়।
কম্যুনিস্ট ও তাদের অনুসারীদের ধারণা মানব সমাজের বিকাশে উপনিবেশবাদ একটি অপরিহার্য স্তর। তারা আরো বলেন, কোন তত্ত্ব বা নৈতিক আদর্শের হারাই উপনিবেশবাদ ঠেকান সম্ভব ছিল না; কারণ এটি একটি অর্থনৈতিক ঘটনা, যার উৎপত্তি শিল্পায়িত দেশের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও এসব উদ্বৃত্ত পণ্যের জন্যে বিদেশী বাজারের প্রয়োজন থেকে।
এ’কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, উপনিবেশবাদের অনিবার্যতা সম্পর্কে এ ধরনের কোন বস্তাপচা তত্ত্বে ইসলাম বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া কম্যুনিস্টরা নিজেরা বলে ও প্রচার করে বেড়ায় যে উৎপাদনের সময় কর্ম সময় ও শ্রমিকদের ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ করে রাশিয়া উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমস্যার সমাধান করবে।কম্যুনিজম যে সমাধান পেয়েছে বলে প্রচার করে তা অন্যান্য ব্যবস্থায়ও প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উপনিবেশবাদ একটি সুপ্রাচীন মানবীয় প্রবৃত্তি বিশেষ। ধনবাদের সাথে এর জন্ম হয়নি; যদিও ধনতন্ত্রের আধুনিক মারণাস্ত্র একে অধিকতর হিংস্র করে তুলেছে। পরাজিত দেশকে শোষণের ব্যাপারে রোমান উপনিবেশ- বাদীরা আধুনিক উপনিবেশবাদীদের চাইতেও অনেক বেশী হিংস্র ও বর্বর ছিল।
ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষ্য এই যে, যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্য সমস্ত মতবাদের তুলনায় ইসলামী বিধানে সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন মনোভঙ্গী রয়েছে। শোষণ এবং জবরদস্তিমূলক পথে অপরের আযাদী হরণের উদ্দেশ্যে ইসলামী যুদ্ধ সংঘটিত হয় না। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে শিল্প বিপ্লব ঘটলে যুদ্ধ বা উপনিবেশবাদের সাহায্য ছাড়াই ইসলাম উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে পারত। তাছাড়া এ কথাও বলা যেতে পারে যে, বাড়তি উৎপাদনের সমস্যা বর্তমান পর্যায়ের ধনবাদী ব্যবস্থারই একটা প্রতিফলন মাত্র। অন্য কথায় ধনতন্ত্রের মূল ভিত্তিই যদি উৎপাটিত করা যায় তবে এ-সমস্যাই থাকবে না।
অপরদিকে দেখা যায়, অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য ও বঞ্চনার যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হবে আর সম্পদ গুটিকতক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হবে-ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এট। বরদাস্ত করতে পারেন না। কারণ সম্পদের এই পুঁজিকরণ ইসলামী নীতির খেলাপ। জনগণের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে, যাতে সম্পদ কিছুতেই ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে না পড়ে। ইসলাম রাষ্ট্রনায়ককে ইসলামী আইন কার্যকরী করতে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবার দায়িত্ব দেয়-যাতে কোন নাগরিক বে- ইনসাফী ও অন্যায়ের শিকার না হয়। সম্পদ পুঁজিকরণ ব্যাহত করবার জন্য আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্হ্ আইনের আওতাধীনে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়। আমরা এ-প্রসঙ্গে উত্তরাধিকার-আইনের উল্লেখও করতে পারি; কারণ এই আইন প্রতিটি ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সুষম বন্টনের ব্যবস্থা দেয়। যাকাতের উল্লেখও এখানে করা যেতে পারে; কারণ এর মাধ্যমে মূলধন ও মুনাফার শতকরা আড়াই ভাগ দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়াও ইসলাম সম্পদ মজুতকরণ নিষিদ্ধ করেছে। অনুরূপভাবে ইহা সুদও নিষিদ্ধ করেছে। এই সুদই পুঁজি সৃষ্টির মূল ভিত্তি। ইসলামী সমাজের নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক পারস্পরিক দায়িত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, শোষণের উপর নয়।
রসূলে করীম (সা) জীবন-ধারণের বুনিয়াদী প্রয়োজনসমূহ সহ কতিপয় অধিকার কর্মচারীদের জন্যে সুনিশ্চিত করেন: “কোন লোককে আমাদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) কোন দায়িত্ব দেওয়া হলে তার যদি স্ত্রী না থাকে তার স্ত্রীর ব্যবস্থা করা হবে; তার যদি গৃহ না থাকে তার গৃহের ব্যবস্থা করা হবে, তার যদি চাকর না থাকে তার চাকর দেওয়া হবে, তার যদি গৃহপালিত জপ্ত না থাকে তার জন্তর ব্যবস্থা করা হবে।”
এই গ্যারান্টি শুধু রাষ্ট্রের কর্মচারীদের জন্য নয় প্রতিটি নাগরিকের জন্যই এগুলো মৌলিক প্রয়োজন। রাষ্ট্রের যে-কোন চাকুরীর বিনিময়ে এই মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা যেতে পারে। যারা এ কাজ না করে সমাজের কল্যাণ- কর অপর কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত থাকবেন তারা তার মারফতে এই প্রয়োজন পূরণের সুযোগ লাভ করবেন। রাষ্ট্র যদি তার কর্মচারীদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দান করে, রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রমরত প্রতিটি নাগরিকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। যারা বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অল্প বয়সের কারণে কাজ করতে অক্ষম তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বায়তুলমাল গ্রহণ করে-এ থেকেই আমরা উপরোক্ত নীতির সত্যতা অনুধাবন করতে পারি। যাদের সম্পদ তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের জীবিকার পূর্ণ দায়িত্বও বায়তুলমাল তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারের।
উপরোল্লিখিত তথ্যাবলী একথাই স্পষ্ট করে তোলে যে, কর্মজীবী মানুষের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকদের এই প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন্ উপায় গ্রহণ করা হবে তা বড় কথা নয়-বড় কথা এই যে, জাতির সমস্ত সদস্য সমভাবে লাভ ও ক্ষতির অংশীদার হবে। শ্রমিকদের এই প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা দিয়ে ইসলাম শোষণের বিরুদ্ধে যে গ্যারান্টি দিয়েছে শুধু তাই নয়, ইহা সকলের জন্য একটা সুন্দর জীবনও নিশ্চিত করেছে।
“সভ্যতা’-গর্বী পাশ্চাত্যে বর্তমানে যে মানবতা-বিধ্বংসী পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যবস্থায় তা কোনদিনই সম্ভবপর হত না। শরীয়ত কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত বা শরীয়তের মূল্যবোধের ভিত্তিতে আধুনিক পরিস্থিতির মুকাবিলার্থে প্রণীত ইসলামী আইনে পুঁজিবাদীকে শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করার সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হত না। ইসলামী শাসনে ঔপনিবেশিকতা, যুদ্ধ ও জন- গণের দাসত্ব প্রভৃতি পুঁজিবাদের প্রতিটি শয়তানীকেই নির্মমভাবে খতম করে দেওয়া হত।
ইসলাম শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইন ও বিধান রচনা করেই ক্ষান্ত হয় না। এ-সব আইন ছাড়াও ইসলাম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা ব্যবহারের প্রয়াস পার। ইউরোপে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোন বাস্তব তাৎপর্য নেই বলে কম্যুনিস্টদের কাছে এ-সব আদর্শ উপহাসের সামগ্রী। কিন্তু ইসলামে কখনই বাস্তব অবস্থা থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পৃথক করে বিবেচনা কর। যায় না। অন্তরের শুদ্ধিকরণ ও সমাজের সংগঠনের মধ্যে ইসলাম এক অদ্ভুত নিয়মে সমন্বয় সাধন করে। বাস্তবের সাথে আদর্শের কিভাবে সংযোগ ঘটান সম্ভব হবে এ-চিন্তায় বিমুচ হবার সুযোগ ইসলাম কাউকে দেয় না। ইসলাম একটি নৈতিক ভিত্তিতে এর আইন রচনা করে। তাই এর নৈতিক মূল্যবোধ এর আইনের সাথে সুসমঞ্জস হয়, এভাবে একে অপরের সম্পূরক হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোন সংঘাতের অবকাশ থাকে না।
স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিণামে তাদের মধ্যে বিলাস-ব্যসন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার উদ্ভব হয়। ইসলাম সর্বপ্রযত্নে একে নিষিদ্ধ ও নিরুৎসাহিত করেছে। এছাড়া কর্মচারীদের প্রতি বে-ইনসাফী করা এবং তাদের অপর্যাপ্ত বেতন দেওয়াকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কর্মচারীদের অপর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার ফলেই মজুত সম্পদ গড়ে ওঠে বলে একেও অবশ্যই নিরুৎসাহিত করতে হবে। ইসলাম মানুষের প্রতি আল্লাহর রাহে অর্থ ব্যয় করতে আহ্বান জানায়-এমন কি তাতে যদি তার সমস্ত অর্থও ব্যয় করতে হয়। ধনীরা আল্লাহ্ রাহের পরিবর্তে নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য অর্থ ব্যয় করে বলেই পুঁজিবাদী দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য ও বঞ্চনার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।
ইসলাম মানুষের আত্মিক উন্নতির এমন ব্যবস্থা করে বা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলে এবং যা তা তাকে পার্থিব বিলাস-ব্যসন ও স্বার্থচিন্তা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালে তাঁর করুণ। লাভের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য আত্মসমর্পিত এবং পরকালের পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, যে কিছুতেই অপরকে শোষণ করে বা হীন স্বার্থের লোভে পুঁজিকরণের জন্য উন্মত্ত হয়ে ছুটবে না। এইভাবে নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ অর্থনৈতিক আইন-প্রণয়নের পথ এমনভাবে প্রশস্ত করতে পারে, যার ফলে পুঁজিবাদের অভিশাপ চিরকালের জন্য খতম করা যায়। পরিণামে এসব আইন যখন রচিত হয় তখন তার মান্যতাও সুনিশ্চিত হয়-কারণ এখানে শাস্তির ভয়ই শুধু থাকে না, বিকাশপ্রাপ্ত বিবেকের নির্দেশও এ ব্যাপারে সাহায্য করে।
উপসংহারে আমরা বলতে চাই, মুসলিম বিশ্বের স্কন্ধে আজ যে দানবীয় পুঁজিবাদ চেপে বসেছে তার সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং তার অশুভ পরিণতির জন্য জবাবদিহির দায়িত্ব ইসলামের নয়।
ইসলাম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি
ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি স্বাভাবিক প্রবণতা প্রসূত? কম্যুনিস্ট ও তাদের সমদর্শীরা দাবী করে না যে, তা নয়। তারা দাবী করে, প্রাচীনতম সমাজে, যখন “আদিম কম্যুনিজম’ প্রচলিত ছিল, কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। তারা বলে, তখন সমস্ত দ্রব্যই ছিল সাধারণ সম্পত্তি, সমস্ত মানুষের তাতে অংশ ছিল এবং সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের ভাবধারায় সকলে উদ্বুদ্ধ ছিল। তারা বিলাপ করে যে, কৃষিকার্যের উদ্ভবের ফলেই অমন “দেবযুগ” টিকতে পারল না। কারণ কৃষিকার্যের উদ্ভবের ফলে কর্ষিত জমি ও উৎপাদনের হাতিয়ার নিয়ে গোল বেধে গেল, আর তারই পরিণামে লেগে গেল যুদ্ধ। কম্যুনিস্টরা বলে যে, মানুষ এই ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে “আদিম কম্যুনিজমে” প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে যেখানে কোন ব্যক্তির নিজস্ব কোন সম্পত্তি থাকবে না এবং সমগ্র উৎপাদনের উপর সকলের সমান অধিকার থাকবে। তারা বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে শান্তি, সম্প্রীতি ও সুষমা ফিরিয়ে আনবার এই একমাত্র পন্থা।
মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা কিন্তু মানবীয় অনভূতি, ধারণা ও আচরণকে প্রাকৃতিক ও অর্জিত-এই চুলচেরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে বিশ্বাস করেন না। অনুরূপভাবে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কেও ভিন্ন মত পোষণ করেন। কতক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাভাবিক প্ৰৰণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অন্যের। মনে করে যে, ইহা পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে অর্জিত। তারা বলেন, শিশু যে তার খেলনা অন্যকে দিতে রাধী হয় না, তার কারণ সম্ভবত খেলনার সংখ্যা কম, নতুবা অন্য কোন শিশু সেটা নিয়ে যাবে-এই আশঙ্কা সে করে। তারা বলেন, দশটি শিশুর জন্য একটি খেলনা থাকলে ঝগড়া লেগে যেতে বাধ্য, কিন্তু দশটি ছেলের জন্য দশটি খেলনা থাকলে প্রত্যেকেই একটা করে পাবে এবং কোন সংঘর্ষই বাধবে না।
কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদর্শিত যুক্তির জবাবে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপঃ
১. কোন বিজ্ঞানীই এ যাবত সর্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করে এমন প্রমাণ দিতে পারেন নি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বভাবজাত নয়। বামপন্থীগণ এ যাবত এ ব্যাপারে যা বলতে পেরেছে সে হচ্ছে, এটা যে স্বাভাবিক প্রবণতা-প্রসূত তারও কোন চূড়ান্ত দলীল নেই। কিন্তু সেটি অন্য প্রশ্ন।
২. শিশু ও তার খেলনার যে দৃষ্টান্ত কম্যুনিস্টরা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে দিয়ে থাকে তা থেকে তাদের তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। দশটি ছেলেকে দশটা খেলনা দিলে যে বাগড়া বাধে না, তার মানে এ নয় যে, ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক প্রবণতা সেখানে নেই। এটা বরং প্রমাণ করে যে, একটা সুস্থ পরিবেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাসনা নিরংকুশ সমতার মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত উক্ত বাসনার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করে না, এর প্রকৃতি নির্ধারণে সহায়তা করে মাত্র। তাছাড়া একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এমন অনেক ছেলে আছে যারা বাধা না পেলে অন্যান্যদের খেলনা জবরদখল করতে দ্বিধা করে না।
৩. আদিম সমাজে একটি ‘দেব-যুগ’ ছিল বলে কম্যুনিস্টর। যে অনুমান করে এ সম্পর্কে বলা চলে যে, এমন একটি যুগের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন বাস্তব প্রমাণই নেই। এমন কি যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, এমন একটি যুগ ছিল তবুও সেখানে উৎপাদনের কোন হাতিয়ার ছিল না। সুতরাং যার অস্তিত্বই ছিল না তা নিয়ে দ্বন্দ্ব লাগবে কি করে? সে-সময়ে মানুষ সহজ পন্থায় বৃক্ষ হতে তাদের আহার্য সংগ্রহ করত। তারা যখন শিকার করতে যেত, বন্য জন্তুর ভয়ে তারা দলবদ্ধ হয়ে থাকত। নিহত জন্তু জমিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল। তাতে তা পচে গলে যেত। সুতরাং একে সাত-তাড়াতাড়ি তাদের খেয়ে শেষ করতে হত। তাই সেদিন সংঘর্ষ না থাকায় এটা প্রমাণ হয় না যে, ব্যক্তিগত অধিকারের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সেদিন সংঘর্ষ না থাকবার কারণ এই ছিল যে, সংঘর্ষের উপযুক্ত কারণই সেদিন ছিল না। এ জন্যেই কৃষিকার্য আবিষ্কারের সাথে সাথেই সংঘর্ষ দেখা দিল। উপরোক্ত আবিষ্কার মানুষের মধ্যকার এতদিনের সুপ্ত, এমন একটা প্রবণতাকে খুঁচিয়ে তুলল যার কর্মপ্রেরণ এতদিন ছিল না।
৪. একথা কেউই জোর করে বলতে পারবে না যে, সেই প্রাচীন যুগেও একটি বিশেষ নারীর উপর অধিকার কায়েমের জন্যে একাধিক পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগত না। কল্পনার সেই যুগে যৌন-সাম্যবাদ চালু থাকেনি অথবা উক্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও একটি সুন্দরী নারীকে পাওয়ার জন্যে একাধিক পুরুষেরা যে লড়াই করেনি এ’কথা কেউ জোর করে প্রমাণ করতে পারবে না।
এর থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: যেখানে সৰ বস্তু সমান ও সদৃশ, সংঘাতের সম্ভাবনা সেখানে কিছুটা অস্বীকার করা যায়। কিন্তু দ্রব্যসমূহ যতদিন পৃথক ধরনের থাকবে, সংঘাত ও সংঘর্ষ সেখানে দেখা দিতে বাধ্য-এমন কি কল্পনার যে দেবসমাজের উপর কম্যুনিস্টরা তাদের ভাবী দুনিয়ার সমাজের সুখছবি অংকন করে সেটা সম্বন্ধেও একথা সমভাবে সত্য।
৫. সর্বশেষে, একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, প্রাচীন যুগে যারা বাস করত তাদের অনেকে সাহস, দৈহিক শক্তি বা অন্য কোনরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের বাসনা রাখত। তথাকথিত ‘আদিম সাম্যবাদী সমাজের’ দৃষ্টতান্তরূপী কতক আদিম উপজাতি অদ্যাবধি এমন সব লোকের সাথে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দিতে অস্বীকার করবে যারা উহ্-আহ্ না করে একশতটি বেত্রাঘাত সহ্য করতে পারে না। নওজোয়ানরা যে এ ধরনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে আকৃষ্ট হয় তার একমাত্র কারণ যে ব্যক্তিগত গৌরব অর্জন, সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই।
সব জিনিসই যদি নিরংকুশ সাম্য-নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় তা হলে কিছু সংখ্যক লোক কেন নিজেদেরকে অন্যের সমান মনে না করে অন্যান্যদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, তার কারণ গবেষণা করে দেখতে হবে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের স্বভাবজাত প্রেরণা থেকে যদি উদ্ভুত নাও হয়, তবুও এটা অপর একটি স্বাভাবিক প্রবণতার ফল অর্থাৎ আদি যুগ থেকেই ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে, এটা তারই পরিণতি-ফল।
কম্যুনিস্টরা বলে থাকে যে, প্রত্যেক যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যেই অবিচার সংঘটিত হয়েছে এবং এজন্যেই মানুষ যদি শান্তি চায় ও তিক্ত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পেতে চায় তবে অবশ্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করতে হবে।কিন্তু কম্যুনিস্টরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ সত্য ভুলে যায়: মানবতার অগ্রগতিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রচুর অবদান রয়েছে। তাছাড়া ‘আদিম সাম্যবাদের’ সেই তথাকথিত ‘দেব-যুগে’ কোন প্রগতিই সাধিত হয়নি। একথা বলা চলে যে, সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হবার পরই মানুষের প্রগতি শুরু হয়। অর্থাৎ এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র অভিশাপ নয়-বরং যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে এর অস্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন।
এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মানবতাবিরোধী সর্বপ্রকার অবিচারের মুলে-এমন কথ। ইসলাম স্বীকার করে না। ইউরোপ ও অন্যান্য অমুসলিম দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে বে-ইনসাফীর সয়লাব বইয়ে এনেছে তার কারণ এই যে, ওসব দেশে সম্পদশালী লোকেরাই একাধারে আইন-প্রণেতা ও শাসক। এ অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এসব লোক এমন আইন রচনা করবে, যা অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থ বলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।
একটি বিশেষ শাসকশ্রেণীর অস্তিত্ব ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামে বিশেষ কোন সুবিধাভোগী শ্রেণী আইন রচন। করে না-সমস্ত শ্রেণীর সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ তা’আলাকেই ধরা হয় মূল আইন প্রদাতা। এটা কল্পনা করা যায় না যে, আল্লাহ্ কতক ব্যক্তি বা শ্রেণীর যুপকার্ডে অন্যান্যদের স্বার্থ বলি দেবেন। এ ধরনের পক্ষপাতিত্বে তাঁর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? ইসলামের মতে সমস্ত মুসলিম মিলে স্বাধীনভাবে শাসক নির্বাচন করবেন। কোন শ্রেণীগত বিবেচনায় তাঁকে মনোনীত করা হয় না। দায়িত্ব গ্রহণের পর শাসনকর্তাকে এমন এক আইন অনুসরণ করতে হয়, যা তিনি নিজে রচনা করেন নি, যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা’আলা নাযিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা.)-এর একটি উক্তি উল্লেখ করতে পারি: “তোমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে আমি ততক্ষণই তোমাদের আনুগত্যের অধিকারী, যতক্ষণ আমি আল্লাহর অনুগত থাকি। যখন আমি আল্লাহ্ অবাধ্যতা করব, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো না।” শাসনকর্তা নিজের উপর বা অন্য কারো উপর আইন রচনার কোন বিশেষ অধিকার আরোপ করবে-ইসলামে এমন কোন বিধান নেই। এক শ্রেণীর বদলে আরেক শ্রেণীকে খাতির করা অথবা সম্পদশালী শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাবে অন্যান্যদের উপর শোষণ চালিয়ে সম্পদশালী লোকদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ক্ষমতা ইসলাম শাসনকর্তাকে দেয় না।
একথা স্পষ্টভাবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, যখন আমরা ইসলামী শাসনের কথা বলি তখন ইসলামী ইতিহাসের সেই যুগের কথাই বলে থাকি যখন ইসলামের নীতি ও শিক্ষাকে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যকরী করা হয়েছিল। কিছুতেই সে-সব আমলের কথা বলি না, যখন তাকে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত করা হয়। ইসলাম ওসব (রাজতন্ত্রী) সরকারকে স্বীকার করে না এবং ওসব শাসনের জন্যে ইসলামকে দায়ী করাও চলে না।
ইসলামী শাসন তার ইনসাফ ও আদর্শবাদ নিয়ে মাত্র সংক্ষিপ্ত কাল স্থায়ী হয়েছিল বলে এটাও মনে করবার কারণ নেই যে, এটা এমন একটি কাল্পনিক ব্যষস্থা যার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। যা একদ। সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছিল ত। পুনর্বার বাস্তবায়িত হতে পারে এবং সমস্ত মানুষের কর্তব্য সে ধরনের একটি আদর্শ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে অন্য যে-কোন যুগ অপেক্ষা বর্তমান যুগ সর্বাধিক উপযোগী।
ইসলামী শাসন-ব্যবস্থায় সম্পদশালী লোকগণ শুধুমাত্র তাদের স্বার্থে কোন আইন প্রণয়ন করতে সুযোগ পাবে না। ইসলামের বিধানমতে সমস্ত মানুষকে একই আইনের দ্বারা শাসন করা হবে, মানবীয় অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনরূপ তারতম্য করা হবে না। কোন আইনের বিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য উপস্থিত হলে-যা পৃথিবীর যে-কোন আইনের ব্যাপারেই হতে পারে আইনবিদগণ শেষ রায় দেবেন। একথা গৌরবের সাথে উল্লেখ করা যায় যে, খ্যাতনামা মুসলিম আইনবিদদের কেউই কখনই কোন আইনের এমন ব্যাখ্যা দেননি, যার দ্বারা দরিদ্রদের পরিবর্তে সম্পদশালী লোকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। তারা বরং শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক দাবী পূরণ ও তাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের উপর আগাগোড়া বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অনেক মুসলিম আইনবিদ (ফকীহ্) মালিকের মুনাফার শ্রমিকের শরীকানাও দাবী করেছেন।
অপরদিকে, ইসলাম মানব-প্রকৃতিকে কখনও এত জঘন্য মনে করে না যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেই সে বে-ইনসাফী ও জুলুমবাজি শুরু করে দেখে। মানব প্রকৃতিকে সংহত ও শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে ইসলাম অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। অনেক মুসলমান সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ‘তারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কোন বাসনা-কামনাই পোষণ করে নি, বরং অন্যদেরকে সেগুলো দান করে দিয়ে নিজেদের জন্যে সহজ সরল জীবন বেছে নেয়।” (কুরআন-৫৯:৭)। তাঁরা স্বেচ্ছায় অন্যকে তাদের সম্পত্তি দিয়ে দেন এবং এর জন্যে আল্লাহ্ মাগফিরাত ও রহমত ছাড়া আর কিছুই প্রতিদান চাননি। এসব সুমহান বিরল দৃষ্টান্তসমূহ সর্বদা সারণে রাখা আমাদের কর্তব্য। এগুলো সীমাহীন অন্ধকারে আলোকচ্ছট। বিশেষ-ভাবী দুনিয়ার মানবতার বিকাশে এসৰ মহৎ আদর্শ আলোকবর্তিকারূপে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে।
একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, ইসলাম আমাদের স্বপ্নের রাজ্যে বাস করতে বলে না-ইহা জনস্বার্থকে অনিশ্চিত ‘সদিচ্ছার’ উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে রাখে না। আত্মার শুদ্ধি ও উন্নয়নের উপর অত্যধিক নজর দেওয়। সত্ত্বেও ইসলাম কখনও বাস্তব বিবেচনা ভুলে যায় না। ইসলামী আইন সম্পদের সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা বিধান করে। শুধুমাত্র আত্মার শুদ্ধিকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ইনসাফসম্মত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলাম সুস্থ সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। তৃতীয় খলীফা উসমান বিন আফ্ফান নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে সম্ভবত সেকথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন: “কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ যা সংযত করেন না, শক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা নিয়ন্ত্রণ করেন।”
ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নে পুনরায় ফিরে আসা যাক। কোন কোন ৰূগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বে-ইনসাফী হয়নি। ইসলাম ভূমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু কখনও ইউরোপের ন্যায় একে সামন্তবাদে পরিণত হবার সুযোগ দেয়নি। ইসলাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এমন সব আইন প্রণয়ন করেছিল যার ফলে সামন্তবাদ গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি এবং বাদের ভূসম্পত্তি ছিল না। তাদের জন্যেও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা ছিল এসব আইনে। এ নিশ্চয়তাই সম্পদশালী লোকদের দ্বারা দরিদ্র শ্রেণীকে শোষণের পথ রুদ্ধ করে দেয়।
তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ইসলামে ধনবাদ ছিল, তবে বুঝতে হবে, ইসলাম সেই ধনবাদই স্বীকার করে, যা জনস্বার্থের জন্যে কল্যাণ- কর। মানব-প্রকৃতির শুদ্ধিকরণ ও উন্নয়ন সাধন এবং সাথে সাথে যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলাম যে ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাতে ধনবাদ তার অত্যাচার-মূলক ও শোষণ-মূলক পর্যায়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পায় না। ইসলাম বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্বের দূরবস্থার অবসান করতে পারত। তাছাড়া ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে অনুমতি দেওয়া হয় তা একাধিক বিধি-নিষেধের ফলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন এর বিধান মতে সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রূপে গণ্য হবে। ইনসাফের খাতিরে যেখানেই দরকার হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে এবং অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক গ্যারান্টি ছাড়া এর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না।
আমাদের বক্তব্যটি খোলাসা করবার উদ্দেশ্যে আমরা কতিপয় অনুসলিম দেশের (অর্থাৎ স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়ান রাষ্ট্রপুঞ্জ) দৃষ্টান্ত প্রদান করতে পারি। বর্ণগত ও জাতিগত বৈষম্যের প্রবক্তা ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসী জাতিত্রয় এ’কথা স্বীকার করে যে, স্ক্যাণ্ডিন্যাভীয় জাতি দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে সুসভ্য ও স্নেহপরায়ণ জাতি। এখানে স্মরণ করা দরকার যে, এসব দেশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করে নি-তার। সম্পদের সুষম বন্টনের জন্যে প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা বিধান করেছে মাত্র। এসব গ্যারান্টির ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে এবং কাজ অনুপাতে মজুরী ধার্যের ব্যবস্থা হয়েছে। একথা বলা চলে যে, এতে করে ইসলামের কতিপয় দিকের বাস্তবায়নে স্ক্যান্ডিন্যাভীয় দেশসমূহ পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশ থেকে ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে।
কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই তার অন্তনিহিত সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন থেকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। আজকের বিশ্বের পুঁজিবাদ, কম্যুনিজম ও ইসলাম-এই তিনটি মতবাদ আমরা যদি পর্যালোচনা করে দেখি, আমরা বুঝতে পারব প্রতিটি মতবাদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মালিকানা-তত্ত্ব তার সামাজিক দর্শনের সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে জড়িত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যক্তিসত্তা অলঙ্ঘনীয় এবং কোনরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধের দ্বারাই তার স্বাধীনতা খর্ব করা চলবে না-এই ধারণার উপর পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই পুঁজিবাদ অবাধ ব্যক্তি-মালিকানার অনুমতি দেয়।
অন্যদিকে কম্যুনিজম এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সমাজই মূল বুনিয়াদ এবং ব্যক্তির কোন পৃথক সত্তা থাকতে পারে না। সুতরাং কম্যুনিজম (সমাজের প্রতিভুরূপী) রাষ্ট্রের হস্তে সমস্ত প্রকার সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা অর্পণ করে এবং সমস্ত ব্যক্তিকেই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।
ইসলাম একটি স্বতন্ত্র সামাজিক দর্শনে বিশ্বাসী। তাই তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের ধারণা এই যে, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে দুটি সত্তা বিদ্যমান-একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিরূপে অপরটি সমাজের সদস্যরূপে। কোন এক বিশেষ পর্যায়ে কোন একটি সত্তার আবেদন অপর সত্তা থেকে বৃহত্তর হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে উভয়ের সম্মিলন ও সমন্বয় সাধনই স্বাভাবিক।
এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে সামাজিক ধারণা গড়ে ওঠে তা যেমন কোন ব্যক্তিকে তার সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখে না, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজকে দ্বন্দ্বরত দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তিরূপেও বিবেচনা করে না। ব্যক্তির যেমন;একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তেমনি সমাজের সদস্য হিসাবেও তার সত্ত। বিদ্যমান। সুতরাং এমন আইন প্রণয়ন প্রয়োজন, যা ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে এবং ব্যক্তির স্বার্থ ও অন্যান্যদের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে। একের খাতিরে অপবের স্বার্থ বিপন্ন না করেই সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। সমাজের নামে যেমন ব্যক্তিকে খতম করে দেওয়। আইন রচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়-তেমান এক বা একাধিক ব্যক্তির কারণে সমাজে বিশৃঙ্খল। ঘটতে দেওয়াও চলবে না।
ইসলামের অর্থ-ব্যবস্থা উপরোল্লিখিত সামঞ্জস্য-তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে- এক দিক দিয়ে এটা পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যবর্তী সুস্থ পন্থা। উভর মতবাদের ক্ষতিকর দিক বাদ দিয়ে উৎকৃষ্ট দিকগুলোর সমন্বয় এখানে সাধিত হয়েছে। নীতিগতভাবে ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দিলেও তার উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে যে, তার ফলে ইহা সম্পূর্ণ নির্দোষ জিনিসে পরিণত হয়। সমাজ ও তার প্রতিনিধিরূপে শাসককে ইসলাম মালিকানা সংগঠন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনবোধে জনস্বার্থের খাতিরে চলতি আইন সংশোধনের ক্ষমতা দেয়।
ইসলাম ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দেয়, কারণ এর থেকে উৎসারিত অকল্যাণ দূর করার ক্ষমতাও তার আছে। মনে রাখা দরকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বাভাবিক প্রবণতা-প্রসূতও নয়, মানবিক প্রয়োজনও নয়-এ ধরনের অনুমানের ভিত্তিতে তাকে সরাসরি উচ্ছেদ করার চাইতে নীতিগতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দিয়ে সমাজের উপর তার সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্পণ করা অধিকতর কল্যাণকর ব্যবস্থা। সোভিয়েত রাশিয়াও (ক্ষুদ্রাকারে) কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত মালিকানার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। এর থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি ও সমাজ-উভয়ের স্বার্থে মানব-প্রকৃতির চাহিদা পূরণ করাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা।
আমরা কেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করব? ইসলামকে যে আমরা তা উচ্ছেদ করতে আহ্বান জানাব তাতে কোন্ মহান লক্ষ্য অর্জিত হবে?
কম্যুনিজম বলতে চায়-মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আধিপত্য ও ক্ষমতা। বিস্তারের অন্তনিহিত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করবার জন্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ একমাত্র পন্থা। রাশিয়া উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা উচ্ছেদ করেছে; কিন্তু সে কি এই উচ্ছেদের উদ্দষ্ট লক্ষ্য হাসিল করতে পেরেছে? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়ায় যাদের শক্তি আছে তাদের জন্য অতিরিক্ত মজুরীর বদলে অতিরিক্ত সময় শ্রমদানের (overtime work) একটি স্বেচ্ছামূলক প্রথ। প্রবর্তিত হয়। এর মাধ্যমে রাশিয়া শ্রমিকের মজুরীতে পার্থক্য সৃষ্টি করে।
রাশিয়ায় সমস্ত লোকই কি একই রূপ মজুরী পায়? ডাক্তার ও নার্সরা কি সমান বেতন পায়? কম্যুনিস্ট প্রচারবিদরা প্রায়ই বলে বেড়ায়, রাশিয়ায় ইঞ্জি- নিয়াররা সর্বাধিক বেতন পায় এবং শিল্পীদের আয় সর্বোচ্চ। এসব কথার মাধ্যমে তারা অজান্তে স্বীকার করে বসেন যে, রাশিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরীতে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য শুধু যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তা নয়, একই শ্রেণীর বিভিন্ন লোকের মধ্যেও এই পার্থক্য বিদ্যমান।
কম্যুনিস্ট রাশিয়া কি মানুষের আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা বা ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা উচ্ছেদ করতে পেরেছে? তাই যদি হয়, তবে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, কারখানার ম্যানেজার, সিনিয়র কর্মকর্তা ও কমিশনার মনোনয়ন করা হয় কিভাবে? ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য বেছে বের করাই বা কিরূপে হয়?
ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ বা অনুমোদনের প্রশ্নের বাইরেও মানব-প্রকৃতিতে আধিপত্য লাভ ও ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের আকাঙ্খা। সুপ্ত রয়েছে-এ সত্য কি আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত নয়?
কম্যুনিজম যাকে বিরাট অভিশাপ বলে মনে করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের দ্বারাও মানুষ যখন তার হাত থেকে মুক্তি পায়নি-আমরা কেন তার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাতময় একটি পন্থা বেছে নেব এবং এক অসম্ভব লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করব?
কম্যুনিজম যদি বলতে চায় যে, রাশিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর ও ব্যক্তির মধ্য- কার পার্থক্য এত কম যে, তার ফলে বিলাসিতা বা বঞ্চনা কোনটাই সম্ভব নয়-তাহলে আমরাও বলব যে, কম্যুনিজমের জন্মের তের শত বৎসর পূর্বেই ইসলাম মানুষের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং এমন এক সমাজ কায়েম করেছিল, যেখানে বিলাসিতা ছিল নিষিদ্ধ আর দারিদ্র্যের করা হয়েছিল মূলোৎপাটন।