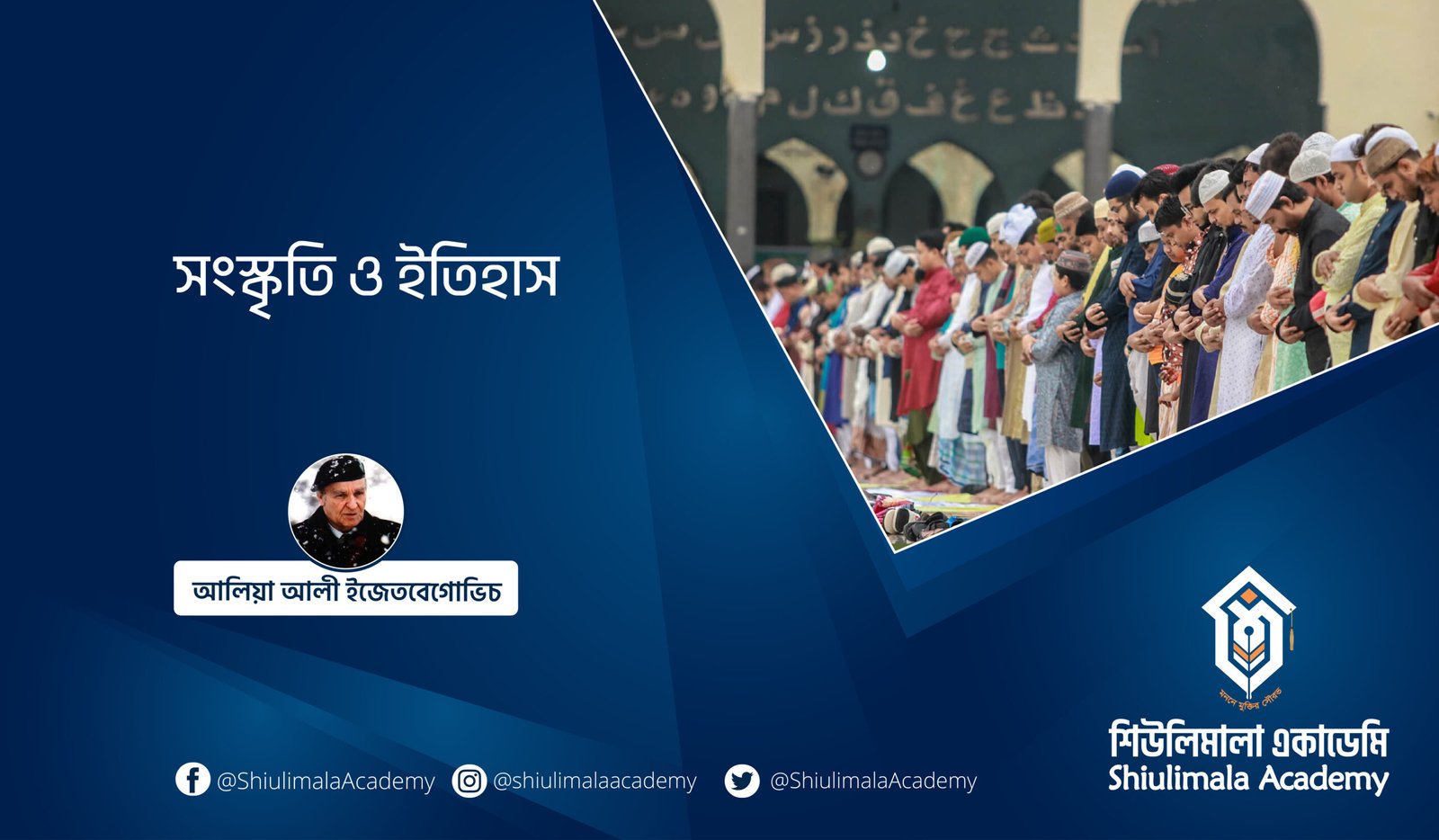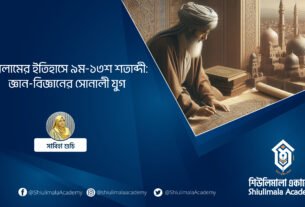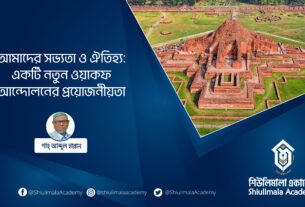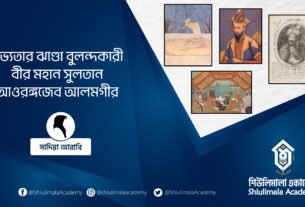বুদ্ধিবাদী ও বস্তুবাদী-উভয় দলই ইতিহাসের এই ব্যাখ্যায় থিতু হয়ে আছে যে, পৃথিবীর বিকাশ শুরু হয়েছে একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে থেকে এবং গুটিকয় অচলাবস্থা ও ব্যতিক্রম ব্যতীত ইতিহাস অনবরত এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। অন্যকথায় তুলনামূলকভাবে বর্তমান কালটি অতীত কাল থেকে উন্নত এবং ভবিষ্যত থেকে অবনত। এ নিয়মেই ইতিহাস চলছে তাদের মতে। বস্তুবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক কারণ তাদের নিকট ইতিহাস হল মানুষের বস্তুগত প্রগতি। তাদের চিন্তাধারা বস্তু ও সমাজকে ঘিরে, স্বয়ং মানুষকে ঘিরে নয়। ফলত এটা সংস্কৃতির ইতিহাস নয়, বরং সভ্যতার ইতিহাস।
মানুষ ও সংস্কৃতির ইতিহাস শূন্য থেকে শুরু হতে পারে না, তেমনি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা ক্রমঅগ্রগতির ধারাতেও একনিষ্ঠ হতে পারে না। মানুষ ইতিহাসে প্রবেশ করেছে প্রবল নৈতিকতাসহ যা সে তার ‘পশুত্বময় পূর্বসূরী’র নিকট থেকে পায়নি। প্রাগৈতিহাসিক কালে পশু ও আদিম মানুষের সহাবস্থানের সময় যে মানবিক গুণাবলী মানুষকে পশু থেকে আলাদা করেছিল বিজ্ঞান তা পর্যবেক্ষণ করেছে এবং স্বীকারও করেছে, কিন্তু কখনোই ব্যাখ্যা করেনি। গোড়াতেই (a prior) ধর্মীয় অনুধাবনাগুলো প্রত্যাখ্যান করার ফলে বিজ্ঞান এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ১
প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন লুইস মরগান তার Ancient Society বইয়ে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এ রকম: ২
-একটি গোত্রের সকলে মিলে তাদের নেতা পছন্দ করে, আবার সকলে মিলেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত নেতা পুনরায় গোত্রের অপরাপর সদস্য তথা সাধারণ যোদ্ধায় পরিণত হয়।
– একই গোত্রের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ও যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ থাকে।
– আত্মউৎসর্গের পর্যায় অতিক্রম করে।
– গোত্রের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা এতই প্রবল যে, অনেক ক্ষেত্রে তা আত্মউৎসর্গের পর্যায় অতিক্রম করে।
-বন্দীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হয়।
-গোত্রের সকল সদস্যই মুক্ত, স্বাধীন থাকে।
-গোত্রে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ধর্মীয় রীতিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নৃত্য ও নাটকের মধ্যে। প্রতিমার অস্তিত্ব নেই।
– সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক মনোভাব অস্তিত্বশীল থাকে।
প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই চিত্র দেখে এঙ্গেলস পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেন, “কী চমৎকার সংবিধান। কী শিশুসুলভ সরলতা। সেনাবাহিনী নেই, পুলিশ, পাদ্রী, রাজা, মন্ত্রী, বিচারক, আইন, জেল কিছুই নেই- অথচ সব কিছুই সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। নারী-পুরুষ সবাই স্বাধীন; কোনো দাসত্ব নেই, এক গোত্রের ওপর আরেক গোত্রের আধিপত্য নেই। ৩
মর্গান বর্ণিত সমাজচিত্র শৈল্পিকভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তারই দেশের ঔপন্যাসিক ফেনিমোর কুপার। সন্দেহ নেই, র্যালফ ওয়ালডো ইমারসনের মনেও একই প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে যখন তিনি আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে লেখেন, “আমি এদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দেখেছি এবং যত বেশি হিংস্রতা তাদের মধ্যে, তত বেশি মহত্ত্ব।”
টলস্টয় তার সামাজিক আদর্শের ভিত্তিভূমি খুঁজে পেয়েছেন আদিম রুশ কৃষকদের নিষ্কলুষ সরল জীবন ধারায়। এখানে এবং সর্বত্রই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলো নীচু স্তরের বস্তুগত ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত থেকেছে।
ইউনেস্কো প্রকাশিত General History of Africa বইয়ে আমরা আদিম আফ্রিকীয় মানুষের সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহোদ্দীপক চিত্র পাই। উদাহরণস্বরূপ জানা যাচ্ছে যে, প্রাচীন আফ্রিকীয় রাজ্যগুলোতে বিদেশী, সাদা কিংবা কালো, আগন্তুকদের আন্তরিক আতিথ্য দেওয়া হত এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মতই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তারা। অথচ একই সময়ে প্রাচীন গ্রীস কিংবা রোমে বিদেশী আগন্তুকদেরকে দাস হিসেবে গণ্য করা হত। এগুলো লক্ষ্য করে বিখ্যাত জার্মান জাতিতাত্ত্বিক লিও ফ্রবেনিয়াস বলছেন, The Africans are civilized upto their bones, and the idea of their being barbarians is a Europen fiction.
আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আফ্রিকা বা তাহিতির আদিবাসী কিংবা আদিম রুশ কৃষক বা ভারতের ব্রাত্য শ্রেণী-যাদের মধ্যে এই মানবিক মূল্যবোধগুলো জীবন্ত ছিল-এদের উৎপত্তি কোথায়? এবং কেন তারা ইতিহাসের প্রারম্ভে অস্তিত্বশীল থাকলেও ঐতিহাসিক প্রগতির সাথে সাথে সংখ্যালঘুতে পরিণত হল?
মর্গান তার সুপরিচিত বইটি শেষ করেন এই কথাগুলো বলে, “রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এবং সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সাধারণ শিক্ষা বয়ে থাকবে অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান। এবং সেটা হবে সেই আদিম মানুষের স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের নবতর পুনরাবৃত্তি।
” অর্থাৎ মর্গানের মতে ভবিষ্যতে সভ্য সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আসবে তিনটি ব্যবস্থাপনা দ্বারা : অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান। কিন্তু মজার ব্যাপার হল (১) আদিম সমাজে সাম্য-স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্ব অভিজ্ঞতা, মন ও বিজ্ঞান থেকে উৎসারিত হয়নি এবং (২) মর্গানের বইটি লিখিত হওয়ার (১৮৭৭) পরবর্তী সময় পর্যবেক্ষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি যে, তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে।
ইতিহাস তথাকথিত বর্বররা লিখছে না, ইতিহাস লিখছি আমরা। আমরা যত বেশি সভ্য হচ্ছি তাদের প্রতি আমাদের বোধ তত বেশি ঝাপসা হয়ে আসছে। কেউ যখন গণহত্যা চালায় কিংবা কোনো সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চায় তখন তাকে আমরা বর্বরতা বলি, অপরদিকে যখন সহমর্মিতা ও মানবিকতার দাবি জানাই তখন বলি, “সভ্য জাতির মত আচরণ কর”। অর্থাৎ সকল ভালত্বে অধিকার আমাদের, মন্দত্বে তাদের। অথচ ইতিহাসের ধারা কি সাক্ষ্য দেয়? সুসভ্য স্প্যানিশরা কি নির্মম ও নির্লজ্জভাবে মায়া ও এ্যাজটেক এবং তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেনি? সভ্য ও সাদা চামড়ার বসতি স্থাপনকারীরা কি পরিকল্পনা মাফিক ইন্ডিয়ান উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেনি? মার্কিন সরকারের অনুদান কি তাদের সংস্কৃতির যৌবনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে? তিন শ’ বছর ধরে ইউরো-মার্কিন সভ্যতার ধারকেরা যে দাস ব্যবসা চালিয়ে এসেছে তা ইতিহাস থেকে মুছে যাবে কখনো? ঐ সময়ে তের থেকে পনের মিলিয়ন (সঠিক সংখ্যা কোনো কালেই জানা যাবে না) মানুষকে ধরা হয়েছিল নিতান্ত পশু শিকারের মতই।
এ প্রেক্ষিতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কথা আসে যেখানে পশ্চিমা এবং অনুন্নত, অল্প সভ্যমানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু উপায়টি হল ছল-চাতুরি, ভণ্ডামি ও অর্থনৈতিক দাসত্ব আরোপ এবং সে সাথে চলছে দুর্বলদের বস্তুগত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংসের চক্রান্ত।
মধ্যযুগের ব্যাপারে আমাদের সংস্কারও একই প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যাযোগ্য। মধ্যযুগ কি সত্যিই অন্ধকার ও অস্বস্তির যুগ? সভ্যতার বিচারে হয়ত তাই। ইওরোপীয় বস্তুবাদী দার্শনিক হেলভেটিয়াসের ভাষায় মধ্যযুগে মানুষ পশুত্বে পরিণত হয়েছিল এবং মানুষের আইন পরিণত হয়েছিল দুর্বোধ্যতার আখড়ায়। কিন্তু বলা বাহুল্য খ্রিস্টান দার্শনিক নিকোলাই বার্দায়েজেভ বা চিত্রকর জাঁ আরপ-এর নিকট মধ্যযুগ সেভাবে প্রতিভাত হবে না। সত্যি কথা হল, স্বচ্ছলতা ও আয়েশের ঘাটতি থাকলেও মধ্যযুগীয় সমাজ সব সময় অন্তর্নিষ্ঠ সারবত্তায় পরিপূর্ণ থেকেছে। সময়টি ছিল আধ্যাত্মিকতা ও মননমন্থনের স্বর্ণ যুগ যা ছাড়া পশ্চিমা মানুষের ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষাকে বোঝা যায় না। মধ্যযুগ জন্ম দিয়েছে চমকপ্রদ বিশাল শিল্পকর্ম এবং সুসমন্বয় ঘটিয়েছে একটি মহান ধর্ম (খ্রিস্ট) ও একটি মহৎ দর্শনের (গ্রীক) মধ্যে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সৃষ্টি প্রকৌশল হিসেবে গথিক রীতির জন্ম এই মধ্যযুগেই। এই যুগ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরিবর্তে যে অন্যতর উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তাকে এ এন হোয়াইটহেড বলছেন “qualitative progress.”
শিল্প ও ইতিহাস
একদিক থেকে বলতে গেলে, সংস্কৃতি কাল ও ইতিহাসের ঊর্ধ্বে। সংস্কৃতির উত্থান ও পতন আছে, কিন্তু সাধারণ অর্থে প্রগতি বলতে আমরা যা বুঝি তার সাথে এর কোনো আত্মীয়তা নেই। শিল্পে জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নেই, যেমনটি বিজ্ঞানে রয়েছে। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে আজ অবধি আমরা শিল্পে প্রকাশ ক্ষমতার কোনো বর্ধিত পর্যায় খুঁজে পাইনে প্রগতির সমান্তরালে। সেই আদিকালের শিল্পের যে অনুভাবনা ও বোধ, আজকের মহৎ শিল্পেরও তাই।
সভ্যতার যেমন প্রস্তর যুগ, ইস্পাত যুগ ইত্যাদি আছে, সংস্কৃতির সে ধরনের কোনো ঊর্ধ্বমুখী স্তর নেই। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে নব্য প্রস্তর যুগ প্রাচীন যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে এক ধাপ অগ্রসর, কিন্তু শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে বরং উল্টোটি। সে ব্যাখ্যা শিল্পের মধ্যেই রয়েছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগ থেকে কয়েক হাজার বছর পুরনো হলেও সে সময়ের শিল্প পরবর্তী সময়ের শিল্পের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়, খাঁটি। কবিতা সর্বত্রই শুরুতে ছিল খাঁটি ও সরল, শুধু পরবর্তীকালেই এর মধ্যে ব্যবহারিক বিকৃতি এসেছে। এ গদ্যের পূর্বসূরী, সঙ্গীত মানুষের ভাষ্য বর্ণনা রীতির পূর্বজ। প্রমাণ রয়েছে যে প্রতিটি ধর্মই পর্যায়ে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, সংস্কৃতির নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা একটি ধারণাগত বৈপরীত্য; এ ক্ষেত্রে যা সম্ভব তা হল শুধু সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ধারালিপিবদ্ধ করা।
জ্যাক রিসলার বলেছেন, “চার পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মিশরীয় ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই সত্যিকারের শৈল্পিক মূল্যমানতা অর্জন করে।” অনেক সমকালীন শিল্পী প্রাচীন মন্দিরগাত্রে খোদাই, কাদা, মার্বেল, সোনা বা আলাবেষ্টারের বিনম্র বিন্যাস থেকে স্বীয় শিল্পকর্মের অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন। এই প্রাচীন শিল্পকর্মগুলো কখনো কমনীয় ও সূক্ষ্ম (যেমন, থটমস ২য় ও থটমস ৩য়-এর সময়ে), কখনো কঠিন চেহারার স্মারকচিহ্নরূপে উৎকীর্ণ (যেমন চিওপস-এর সময়ে) এবং কখনো বাস্তবিকতাপূর্ণ ও অল্প প্রতীকী (যেমন আকেনীটেন এর সময়ে)।
সভ্যতার চোখে আবিষ্কারকালে আমেরিকা প্রাচীন পৃথিবীর চেয়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর পিছিয়ে ছিল, এমন কি এলাকাটি এর লৌহ যুগেও পৌছায়নি (এইচ. জি. ওয়েলস জানাচ্ছেন)। কিন্তু সময়ের এই মাপযোগ আমেরিকার শিল্পজগতে আরোপ করা যায় না। বোনামপাক মন্দিরে, যেখানে আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীনতম চিত্রকর্ম রক্ষিত আছে, আমরা অসাধারণ সৌন্দর্যময় দেয়ালচিত্র পাই। ১৯৬৬ সালে প্যারিসে প্রদর্শিত মায়া ভাস্কর্যও একই অনুভব জাগ্রত করে।
নীটশের নিকট গ্রীক ট্র্যাজেডি শিল্প জগতের সবচেয়ে বড় অর্জন। তার মতে মানব সংস্কৃতির সর্বোন্নত রূপ পাওয়া যেতে পারে গ্রীক সংস্কৃতিতেই। ১০ “কোনো আধুনিক কবি হোমার কিংবা ধ্রুপদী গ্রীক ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্বকে ছুঁতে পারেনি” বলছেন আঁদ্রে মরিস। রজার কৎ লিখছেন, “দর্শনের কথা ভাবতে ভাবতে কখনো আমার মনে হয়, প্লেটোর পর তা আর খুব বেশি অগ্রসর হয়নি।” সিসেরোর নীতি ভাবনানির্ভর লেখাগুলো এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে (যেমন ডি’ ফিনিবাস বলোনারাম এট মেলম’ কিংবা ‘ডি এ্যামিসিয়া’), কিন্তু তাঁর শ্রমসংঘ বা রাষ্ট্র পদ্ধতির ওপরে সভ্যতাভিত্তিক লেখা আজকের বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। একজন অজ্ঞাতনামা রোমান লেখকের বই ‘ডি রিবাস বেলেসিস’, যেখানে সামরিক সরঞ্জামাদির চিত্তাকর্ষক ড্রইং রয়েছে, সামরিক ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান শুধু। কিন্তু আমরা সেনেকার ‘সুখ’ বা ভার্জিলের কবিতাকে আমাদের জীবনের খণ্ডপটে বাঁধতে পারিনে- তা আমাদের জীবনকে আপ্লুত করে সব দিক দিয়ে। সপ্তম ও অষ্টম শতকের ম্যানিয়োসি নামক চার হাজারের বেশি জাপানি কবিতার সংকলনটি (প্রধানত গীতি কবিতা) আজও বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম মহৎ শৈল্পিক অর্জন বলে বিবেচিত। অ্যাঙ্কাইলাস বা সফোক্লিসের ট্র্যাজেডি সব সময়ই এক অনুপম সত্যের বাণীবাহক। ইউরিপিডেস লিখেছেন ‘ট্রোজান উইমেন’, দু’হাজার বছর পর সাত্রে একই নামে লিখছেন আরেক নাটক। সৃষ্টি ভাবনার প্লাটফর্মে ওদের মধ্যে আমরা কোনো বিরোধিতা খুঁজে পাইনে। কিন্তু বিজ্ঞান সূত্র বৃত্তাবদ্ধ। এ্যারিস্টটলের পদার্থবিদ্যা, টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যা বা গ্যালেনের চিকিৎসাশাস্ত্র আজকের বিজ্ঞানের সাথে কতটুকু অংশীদারিত্ব দাবি করতে পারে? এ্যারিস্টটলের দুটি বিজ্ঞান গ্রন্থ (Physics On Heaven) সম্পর্কে বাট্রান্ড রাসেল বলছেন, “আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে এই দুই বইয়ে লিখিত একটি বাক্যও আজ আর সময়োপযোগী নয়।”
শিল্প-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলে। অন্য কথায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কিন্তু বিজ্ঞানের চলাচল ঠিক বিপরীতক্রমে। অনিবার্য প্রভাবনাসহ প্রাচ্যের সঙ্গীত, হিন্দু লোকসঙ্গীত, আফ্রিকীয় নাচ ও গান, ওসানিয়ার শিল্প প্রবেশ করেছে পশ্চিমে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল বলে বিবেচিত ওসানিয়ার শিল্প স্থান পেয়েছে ইউরোপ আমেরিকায় গ্যালারীতে। আফ্রিকীয় শিল্পের অবগুণ্ঠনের পর তা ইউরোপ আমেরিকার শিল্পে নবতর ঢেউ আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। পশ্চিমা সভ্যতার অপরাপর জগতের মৌলিক শিল্পকর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি। শিল্পের এই সার্বজনীন অন্তর্যোগের কারণেই আইভরিকোস্টের আফ্রিকীয় মুখোশ এবং সিসটিন চ্যাপেলের ছাদচিত্র একই “sensory exitement” তৈরি করে।১১
১৯৬৬ সালে ডাকারে ঊনত্রিশটি দেশের অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত আফ্রিকীয় শিল্পের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্কৃতি জগতের একটি অসাধারণ ঘটনা। কিন্তু একই সাথে কোনো আফ্রিকীয় দেশে আয়োজিত আফ্রিকীয় দেশগুলোর বাণিজ্য মেলা হয়ত কোনো খবরেই আসবে না। শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে তা কখনোই অনুন্নত নয়। কারণ শিল্পে অনুন্নত বা উন্নত বলে কিছু নেই। কালো আফ্রিকা তাই শিল্পকলা, লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের জগতে এক সত্যিকার পরাশক্তি।
নীতি ও ইতিহাস
আমরা কেন এ বিশ্ব সংসারে জীবন যাপন করছি- এ প্রশ্ন সংস্কৃতির, আর কিভাবে জীবন যাপন করছি- এ প্রশ্ন সভ্যতার। একটি জীবনের অর্থ সম্পর্কিত, অপরটি জীবনের যাপন প্রণালী সম্পর্কিত। সভ্যতার নানা কীর্তি প্রতিভাত হচ্ছে সেই আগুন আবিষ্কার থেকে আরম্ভকরে জলকল, লোহা, লেখনী, ইঞ্জিন, আণবিক শক্তি, নভোচারণ ইত্যাদি ক্রমোৎকর্ষের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সংস্কৃতির ভিন্ন চরিত্র। সে ঠিকই নতুনতরভাবে আরম্ভ করছে অনেক কিছু, কিন্তু পেছনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মানুষের যে প্রতীকী ভালত্ব-মন্দত্ব, সদগুণ ও সংশয় তা তার মানবিক অস্তিত্বকেই সংহত করে।
আজকের সকল সংকট ও সমস্যা দু’হাজার বছর আগেই নীতি-ভাবনায় পরিচালিত ছিল। মানবতার সকল মহৎ শিক্ষক পয়গম্বর মুসা (আঃ), যীশু খ্রিস্ট, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অপয়গম্বার কনফুসিয়াস, গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস, কান্ট, টলস্টয়, মার্টিন বুবার (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে আজ অবধি) সকলে সারসত্য বিচারে বলতে গেলে একই নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন। সামাজিক শৃংখলা ও উৎপাদনের নিয়ম থেকে নৈতিক মতগুলো পৃথক এবং তা অবিচ্ছিন্নতার পরিচায়ক। কিন্তু বাস্তব জীবনে সবকিছু বিপরীত ক্রমিক, যেমন জন কেনথ গলব্রেইথ বলেছেন, পরিবর্তনশীলতাই অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ম। নৈতিক সত্যগুলোর অপরিবর্তনীয়তার বীজ রোপিত হয়েছে সেই সৃষ্টির সময়ে যখন মানবিক দ্বন্দুপ্রকরণ ও রহস্যকেও আমাদের জীবনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এ কাজটি মানবেতিহাস শুরু হওয়ার আগেই সম্পন্ন হয়েছিল স্বর্গে। বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারটি জানতে আমাদের সহায়তা করতে পারে না। যীশু খ্রিস্ট তার সত্য বার্তা উচ্চারণ করেন তার শৈশবে এবং তিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই তার মিশন সম্পন্ন করেন। খোদা ও মানুষ সম্পর্কে মহৎ সত্যগুলো উচ্চারণে জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতা কোনোটিই প্রয়োজন হয়নি তার। কারণ তা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অধিগম্য নয়। তা “জ্ঞানী ও বিদ্বানদের নিকট লুক্কায়িত এবং শুধু অল্পসংখ্যক মানুষের নিকট প্রত্যাদিষ্ট নয় কি!”১২
সারবত্ত নৈতিক নির্দেশনাগুলো স্থান-কাল ও সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। পৃথিবীব্যাপী মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ ও কর্মকাণ্ডের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা নৈতিক নীতিগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি।১৩ এপিকটেটাস ও মারকিউস-একজন দাস, অপরজন রাজা-একই নৈতিক শিক্ষা, এমনকি একই বাক্যমালা প্রচার করেন। সাধারণভাবে যে সমস্ত ভালো-মন্দ, নীতি-অনীতির ধারণা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় সেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সাথে জড়িত। নীতির মৌলিক চেতনায় আমরা সার্বজনীনতা লক্ষ্য করি। ব্যাপারটি কান্টের বিখ্যাত ‘শর্তহীন আদেশে’র নীতি (Categoric Imperative) দ্বারাও দৃঢ়ীকৃত হচ্ছে। এই নীতিটি, যা প্রাচীন চিন্তাবিদদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পাওয়া যায় তা প্রথম সংজ্ঞায়িত হয়েছে কান্টের “Foundation of the Metaphysics of Morals”-এ এইভাবে, “Work only according to the principle of which you may want to become a general law”, এবং এরপর তার Critique of Pure Reason’-এ বলছেন, “Work in such a way that the principle of your will can serve at any time as a principle of general legislation”.
কিভাবে সৎ জীবন যাপন করতে হয় সে প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন গ্রীসের সাত সাধুর এক সাধু খেলেস (জন্ম ৬২৪ খ্রিঃ পূঃ) বলেছিলেন, “যে কাজের জন্যে আমরা অন্যকে তিরস্কার করি, নিজেরা সেটা করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।” প্রাচীন রোমের সিসেরো বলেন, “অন্যের যা কিছুকে তুমি সমালোচনা কর নিজে সেটা করা থেকে দূরে থাকো। “১৪ যীশু খ্রিস্টের সমসাময়িক এবং প্যালেস্টাইনে বাসরত ইহুদী চিন্তাবিদ হিল্লেল নৈতিকতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “যা তুমি নিজের জন্যে চাও না তা তোমার প্রতিবেশীর জন্যে চেয়ো না। সমগ্র তওরাত এই নীতির সাথে সম্পৃক্ত। “১৫ বুদ্ধ ও পিথাগোরাসের সমসাময়িক কুনফুসিয়াসও একই শিক্ষা প্রচার করেন চীন দেশে: “আমি নিজে যা করতে চাইনে, তা অন্যের জন্যে করি না। “১৬ একই নীতি যীশু খ্রিস্ট প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত এই উক্তিতে: “Do unto others as you would have them unto you”১৭ Categoric Imperative-এর এই চিত্র প্রমাণ করে যে, সার্বজনীন নৈতিক নীতির কোনো প্রগতিশীল ইতিহাস নেই। আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য থাকতে পারে কিন্তু সারসত্যটি সর্বত্রই এক।
শিল্পী ও অভিজ্ঞতা
শিল্পের যেমন বিবর্তন নেই, শিল্পীর জীবনও তেমনি বিবর্তনহীন। প্রত্যেক শিল্পী শিল্প সৃষ্টিতে একেবারে আনকোরা, যেন তার পূর্বে আর কেউ কিছুই সৃষ্টি করেনি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কারও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন না। অন্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন ও সংগ্রহ বিজ্ঞানভিত্তিকতার নির্দেশ দেয়, কিন্তু শিল্পে অন্যের অভিজ্ঞতা ব্যবহারের অর্থ হল অনুকরণ, পুনরাবৃত্তি তথা এক কথায় শিল্পের অকাল মৃত্যু।
পিকাসো সত্তর বছর ধরে আঁকেন এবং এই সময়পর্বে তিনি কিউবিজম, নব্য কিউবিজম, অভিজ্ঞতাবাদ ও পরাবাস্তববাদের পর্যায় অতিক্রম করেন, কিন্তু ব্যাপারটি শিল্পীর মন্দ থেকে ভালোর দিকে কিংবা অপূর্ণাঙ্গতা থেকে পূর্ণাঙ্গতার দিকে গমনের নির্দেশ দেয় না। এটা কোনো বিবর্তন নয়, বরং আবহমান মানবিক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার প্রতি সাড়া দেওয়া। শিল্পের এই অভিজ্ঞতা-অনির্ভর ও ইতিহাসহীন চরিত্র বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বড়দের জন্যে এক ধরনের বিজ্ঞান ও ছোটদের জন্যে আরেক ধরনের বিজ্ঞান। বাচ্চাদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও বয়সের ওপরে তার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তু বোঝা নির্ভর করে। কিন্তু সে অর্থে এমন সঙ্গীত নেই যা উপভোগ করার জন্যে বাচ্চাদের বড় হয়ে উঠতে হয়। বাক, মোৎসার্ট, বেতোফেন, দেবুসী প্রমুখের সুরলহরী বুঝুক আর না বুঝুক, ছোট বড় সকলের মনেই তা সমান সাড়া জাগায়। বেতোফেনের বিখ্যাত বত্রিশ সনেটের সুরচক্র একদিকে তরুণ ছাত্রদের সাহিত্য শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার তা স্বনামখ্যাত পিয়ানো শিল্পীর পিয়ানোতে বাজানো হচ্ছে ক্লাসিক আবহে।
পিকাসো কথা বলতে শেখার আগেই মাত্র দু’বছর বয়সে ছবি এঁকেছেন। তার বয়সী শিশুরা সবে যখন শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছে, ওভিড তখন কথা বলতেন ষটপদীতে। মাত্র ছয় বছর বয়সে মোৎসার্টের প্রথম কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সুতরাং শিল্প জ্ঞান নয়, অন্তর্মস্থিত উপলব্ধি। দিনভর কাজ শেষে একজন কৃষক একখণ্ডও কাঠ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদাই করা শুরু করতে পারেন- দশ বছরের একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই তার। কাজেই বিশেষ প্রতিভাও শিল্পে সবকিছু নয়। স্মরণ করা যেতে পারে টলস্টয় ও তার প্রতিষ্ঠান “ইয়াসানীয়া পলিয়ান”-কে যেখানে তিনি গভীর ধর্মীয় ও নৈতিক আলোচনায় বসতেন শুধু শিশুদের সাথে। ১৮ কাজেই শিল্প, ধর্ম ও নীতিক ভাবনা বোঝার উপকরণ বুদ্ধি ও যুক্তি থেকে নয়, আসছে অন্তর্গত প্রদেশ থেকে। এখানে একটি যুক্তি আরেকটি যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে না; একটি হৃদয় আরেকটি হৃদয়ে একনিষ্ঠ হচ্ছে গভীর মমত্বসহকারে।
টীকা
১. এই সময়ের জীবন্ত স্মৃতি প্রায় সকল জাতির কিংবদন্তী ও রূপকথায় পাওয়া যায় স্বর্ণযুগের মীথ হিসেবে। বাইবেলের Age of the Patriarches এখানে উল্লেখ্য। এই সময়পর্ব যে ভালো ছিল না-সে বিবেচনা এসেছে শুধু বিবর্তনবাদের সাথে। Betrand Russell তার ‘History of Western Philosophy’ বইয়ে বলছেন, “The common belief that the past had been bad appeared only with the theory of evolution.”
২. Morgan তার উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন উত্তর আমেরিকার Iroquois কৌম থেকে যা এ জাতীয় আলোচনার মডেল হিসেবে গৃহীত।
৩. Engels: The Origin of The Family, Private Property and the state, New York. 1928, P. 86.
৪. UNESCO কর্তৃক সম্পাদিত। পরিকল্পিত ৮ খণ্ডের ২ খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত।
৫. বোঝাই যাচ্ছে, Frobenius এখানে Civilized শব্দটি ব্যবহার করেছেন Cultured-এর অর্থেই।
৬. Jean Arp: “I am against mechanized things and chemical formulas. I like the middle ages. Its tapestries and sculputers.”
৭. Whitehead: The Future of Religion.
৮. এখানে অব্যশ্যই আমরা ইউরোপের কথা বলছি। এ অর্থে মধ্যযুগ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিরাজ করছিল না। যেমন, ভারত থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ইসলামী সভ্যতা সে সময়ে উৎকর্ষ লাভকরছিল ক্রমাগত।
৯. Jacque Risler: La Civilization Arabe.
২০. able norms and models”, কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে মার্কস বুঝতে পারেননি যে, তারই একই ধরনের বিবতি মার্কস দিয়েছেন তার নিকট প্রাচীন শিল্পকর্ম উপস্থাপন করে “unreach. বিবৃতি তার দর্শনের বিরোধিতা করছে। সংস্কৃতি যদি সভ্যতা এবং এর উপকাঠামোর প্রতিফলন হয় তাহলে কেন unreachable হবে? আর কেন বা সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হওয়ার আগেই আদিম সমাজে এর অস্তিত্ব থাকবে?
১১. Faure: The Spirit of Forms.
১২. St. Luke 10. 21.
১৩. Tolstoy বলেছেন, “খোদা কি? এ ব্যাপারে যদিও বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন, কিন্তু খোদা তাদের নিকট কি চায় সে ব্যাপারটি যেন সকলেই সমানভাবে বুঝে থাকেন।”
১৪. Diogenes Laerritus 1. 36.
১৫. Babylonian Talmud. part-sabbath.
১৬. Lun-Yu: Thoughts and Talks of Confusious.
১৭. St. Matthew 7:2 and St. Luke 6:31.
১৮. Petrov: Tolstoy
সংস্কৃতি ও সভ্যতা
দ্বৈতবাদের স্রোত
আমরা প্রায়শ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এক করে দেখি, কিন্তু এই প্রত্যয় দুটি অভিন্ন নয় ।১ সংস্কৃতির শুরু সৃষ্টিযজ্ঞ “Prologue in heaven”-এর সাথে। সংস্কৃতি তার ধর্ম, নীতি ও দর্শন সহযোগে মানুষ ও মানুষের আদি উৎস পারমার্থিক জগতের পারস্পারিক সম্পর্ককে উচ্চকিত করে। সকল সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মানুষের স্বর্গীয় উৎপত্তির ধারণার প্রতি স্বীকারোক্তি কিংবা অস্বীকৃতি, সন্দেহ কিংবা স্মৃতিচারণ; সংস্কৃতি এই হেঁয়ালি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং এই হেঁয়ালিই যুগে যুগে নানাভাবে প্রকাশ করে চলছে সে।
বিপরীতক্রমে সভ্যতা হল প্রাণীবিদ্যক ও এক রৈখিক জীবনের ধারাবাহিকতা যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান-প্রদান চলে। এখানে মানব জীবনের সাথে পশু জীবনের পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু তা শুধু মাত্রা, স্তর ও সংগঠনের দিক থেকে, গুণগত প্রেক্ষাপটে নয়। এ পর্যায়ে মানুষ পরাজাগতিক রহস্য, হ্যামলেট কিংবা কারামাজোভের মত কালজয়ী চরিত্রের শাশ্বত অন্তর্দ্বন্দু দ্বারা আক্রান্ত নয়। সমাজের অসংখ্য বেনামী সদস্য এখানে প্রকৃতিপ্রদত্ত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করে এবং পৃথিবীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে থাকে।
সংস্কৃতি হল মানুষের ওপর ধর্মের কিংবা মানুষের ওপর স্বয়ং মানুষেরই (man’s influ-ence on himself) প্রভাবের ফলশ্রুতি, যেখানে সভ্যতা হল প্রকৃতি তথা বাহ্য পৃথিবীর ওপর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবের ফল। সংস্কৃতি হল “মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আর্ট” যেখানে সভ্যতার অর্থ হল শৃংখলা, ক্রিয়া ও যথার্থতা। সংস্কৃতি হল “অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা”, সভ্যতা হল পৃথিবীকে পরিবর্তন করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। এখানেই মানুষ ও বস্তু তথা humanism chosism³ এর মধ্যকার বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়।
ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধুলা, লোকজ সংস্কার, লোককথা, পুরাণগাঁথা, নৈতিক ও নন্দনতত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারী, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে- এগুলোই মানব সংস্কৃতির অখন্ড ধারাচিত্র, যার শুরু স্বর্গে, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যকার আদি যোগাযোগের সূত্রে। এ হল “এক প্রজ্বলিত আলোক শিখার সাহায্যে গাঢ় অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অনতিক্রম্য সেই পবিত্র পর্বতে মানুষের আরোহণ প্রচেষ্টার ছবি।”৩
সভ্যতা পারমার্থিক নয়, বরং কলাকৌশলগত প্রগতির ধারাবাহিকতা, ঠিক যেমনটি ডারউইনীয় বিবর্তন মানবিক নয়, জীববিদ্যক প্রগতির ধারাবাহিকতা। সভ্যতা হল আমাদের পূর্বপুরুষদের চারপাশে অস্তিত্বশীল অচেতন, অর্থহীন ও প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক উপাদানসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন। কাজেই সভ্যতা নিজে ভালোমন্দ নিরপেক্ষ। মানুষের নিশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণ যেমন সহজাত, তেমনি সভ্যতার সৃজনও স্বাভাবিক। সভ্যতা একাধারে আমাদের অন্তর্গত স্বাধীনতার অন্তরায়, আবার আমাদের জন্যে অপরিহার্যও বটে। বিপরীতক্রমে সংস্কৃতি হল মানবিক স্বাধীনতারই নির্বাচন ও প্রকাশন।
সভ্যতায় বস্তুর ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। এক হিসেব মতে প্রত্যেক মার্কিন প্রতি বছর অন্তত ৮ টন বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকে। প্রতিনিয়ত নতুন চাহিদার সৃষ্টি ও সেই চাহিদা পূরণের ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সভ্যতা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান-প্রদান ত্বরান্বিত ও ঘনট করে; সেখানে বাহ্যিক জীবন যাপন ছন্দ উচ্চকিত হয়, কিন্তু অন্তর্নিষ্ঠ জীবনের সুরটি চাপা পড়ে যায় সভ্যতার যান্ত্রিকতার তলে।
“Produce to gain, gain to squander”- সভ্যতায় এই ভাবনা সহজাত। অপরদিকে প্রতিটি সংস্কৃতি তার ধর্মীয় প্রকৃতির কারণে মানুষের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণকে হ্রাস করতে চায়। সে চায় মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার সুরকে জোরালো করতে। সকল সংস্কৃতিতে পাওয়া সন্ন্যাসবৃত্তি ও আত্মস্বীকৃতির ব্যাপারটি এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধর্মের “সংযত আকাঙ্ক্ষার” নীতির পরিবর্তে সভ্যতাকে এই ভিন্নধর্মী মন্ত্রকে লালন করতে হয়েছেঃ “প্রতিনিয়ত তৈরি কর নতুন আকাঙ্ক্ষা।”৪ কিন্তু এই দাবির অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য দুর্ঘটনাপ্রসূত নয়; এই দুই বিপরীতধর্মী দাবি মানব চরিত্রের দুই অপরিহার্য দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে।
সংস্কৃতির বাহক মানুষ, সভ্যতার বাহক সমাজ। সংস্কৃতির অর্থ সহজাতবোধের পরিচর্যার মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জন, সভ্যতার সংযোগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নগরী ও রাষ্ট্রের সাথে- এর মাধ্যম হল চিন্তা, ভাষা ও লেখনী। ৫ সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক স্বর্গজগত ও ইহজগতের বা Civitas Dei ও Civitas Solis-এর সম্পর্কের অনুরূপ। একটি নাটকীয়তার (drama) প্রতিনিধিত্ব করে, অপরটি প্রতিনিধিত্ব করে ইউটোপিয়ার।
ট্যাটিটাস বলছেন যে, রোমানদের চেয়ে বার্বাররা তাদের দাসদের সাথে তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো আচরণ করত। সাধারণভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যকার সীমারেখা বোঝার জন্যে প্রাচীন রোমকে উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। লুণ্ঠন, যুদ্ধ, অমানবিক শাসকশ্রেণী ও অসংখ্য নিরাবয়ব মানুষ, নিম্নতম প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, মিথ্যে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ছলচাতুরি, খৃষ্টান হত্যা, গ্লাডিতোরিয়া (রোমের শাসক ও সামন্ত শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্যে প্রদর্শিত দাসদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাণপণ খেলা), নীরো ও কালিগুলার আচরণ- এ সবই যে রোমান সভ্যতার সত্য চিত্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু সংস্কৃতির কতটা সেখানে ছিল কিংবা সংস্কৃতির অনুষঙ্গ আদৌ ছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয়। স্পেঙ্গলার তাই বলছেন, “Hellenic soul and Roman intel-lect that is the difference between culture and civilization”
একইভাবে মায়া সংস্কৃতি, প্রাচীন জার্মান ও স্লাভ এবং ভারতীয় আদিবাসীদের সংস্কৃতিও রোমানদের সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত।
ইউরোপীয় রেনেসাঁও এই প্রেক্ষিতে ভালো দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানবেতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই যুগটি এক ধরনের পতনোন্মুখতার যুগ। রেনেসাঁর আগের শতকে ইউরোপে এক সত্যিকার অর্থনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হয়, যা সম্ভব হয় বর্ধিত উৎপাদন ও ভোগের মাধ্যমে এবং জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির সাথে সাথে। কিন্তু রেনেসাঁর যুগ বলে পরিচিত পরবর্তী দু’শ’ বছরে (১৩৫০-১৫৫০) এই অর্থনৈতিক বিপ্লবের অনেকখানিই হারিয়ে যায়। পৃথিবীর পরিবর্তে শুধু মানুষ ও মানবমুখে একনিষ্ঠ থাকায় বাস্তবতার প্রতি এক অলস ঔদাসীন্য দেখা দেয় এ সময়ে। এই রেনেসাঁর যুগে একের পর এক যখন পশ্চিমা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্মগুলো সৃষ্টি হচ্ছে, তখন অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ স্থবিরতা ও পরিষ্কার অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছিল যার সাথে যোগ হয় জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৪ মিলিয়ন; একশ’ বছর পরে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২.১ মিলিয়নে। চতুর্দশ শতকে ফ্লোরেন্সের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ৭০ হাজারে হ্রাস পায়।
কাজেই দুই ধরনের প্রগতি রয়েছে যাদের মধ্যে মূলত কোনো আন্তঃসম্পর্ক নেই। অন্য কথায় ‘সংস্কৃতির প্রগতি’ ও ‘সভ্যতার প্রগতি’ সমান্তরালবর্তী নয়। ৭
শিক্ষা ও ধ্যান
সভ্যতা মানুষকে শিক্ষিত করে, সংস্কৃতি মানুষকে আলোকিত করে। একটির প্রয়োজন জ্ঞানার্জন, অপরটির প্রয়োজন ধ্যান।
ধ্যান নিজেকে জানার এবং পৃথিবীতে নিজের স্থানকে বুঝে নেয়ার অন্তর্নিষ্ঠ প্রচেষ্টা যা জ্ঞানার্জন, শিক্ষা কিংবা বাস্তব উপাত্তসমূহ সংগ্রহ প্রচেষ্টার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধ্যান এগিয়ে নিয়ে যায় বিচক্ষণতা, নমনীয়তা, প্রশান্তি বা অন্য কথায় Greek Catharsis – এর দিকে। এটা হল কতক ধর্মীয়, নৈতিক ও শৈল্পিক সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষ্যে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিবেদন ও নিমজ্জিত করা। অপরদিকে শিক্ষা হল প্রকৃতিকে জানা এবং স্বীয় অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রকৃতির দিকে ফেরা। বিজ্ঞান প্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, বিভাজন ও পরীক্ষণ পদ্ধতি যেখানে ধ্যানের অর্থ ‘খাঁটি উপলব্দি’ (নব্য প্লেটোবাদে ধ্যান উপলব্দির পরাবৌদ্ধিক মাধ্যম)। ধ্যানমূলক পর্যবেক্ষণ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত (সপেনহাওয়ার বলছেন); এই ধ্যান কোনো বৈজ্ঞানিকের পথ নয়, তা একজন কবি, একজন ভাবুক বা একজন শিল্পীর পথ। একজন বৈজ্ঞানিকেরও ধ্যানের রাজ্য অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশমাত্রই বিজ্ঞানী আর বিজ্ঞানী থাকেন না, তিনি হয়ে পড়েন অখণ্ডসত্তা এক শিল্পী। ধ্যানে নিজের ওপর আধিপত্য করা যায়, বিজ্ঞান সাহায্য করে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা আমাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সংস্কৃতিকে নয়।
আজকের দিনে মানুষ শেখে; অতীতে মানুষ ধ্যানমগ্ন হত। কিংবদন্তী বলে বোধিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে মহামতি বুদ্ধ তিন দিন তিন রাত্রি নদীর ধারে ধ্যানমগ্ন হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন সময়চেতনা বিস্মৃতি হয়ে। জেনোফেন সক্রেটিস সম্পর্কে একই রকম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন: একদিন সকালে সক্রেটিস একটি জটিল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন যার সহজ সুরাহা হচ্ছিল না; দুপুর গড়িয়ে গেল, তিনি ঠাঁই দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন কেই কেউ ঔৎসক্য সহকারে ঘটনাস্থলের অদূরে তাদের মাদুর এনে অবস্থান নেয় যাতে তারা তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে। সক্রেটিস দিনাবসানের পর সারা রাত্রিও একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, অতঃপর পরের দিন সূর্যোদয়ের পর তার ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি সূর্যের দিকে ফিরে প্রার্থনা করেন, তারপর নিজের পা বাড়ান। ৮ টলস্টয় তার সারা জীবন অতিবাহিত করেন মানুষ ও মানুষের নিয়তি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে, যেখানে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবাদপুরুষ গ্যালিলিও সারা জীবন নিজের চিন্তাকে বেঁধে রাখেন একটি শরীরের পতনজনিত সমস্যার সাথে। ধ্যান করা বা শিক্ষা লাভ সম্পূর্ণ দুই ধরনের কর্মকাণ্ড বা দুই ধরনের শক্তি যা দুই ভিন্ন লক্ষ্যে নিবেদিত। প্রথমটি বেতোফেনকে তাঁর “The Ninth Symphony’ সৃষ্টির দিকে এগিয়ে নেয়; দ্বিতীয়টি নিউটনকে এগিয়ে নেয় ‘The Law of Gravitation’ আবিষ্কারের দিকে। এভাবে ধ্যান ও শিক্ষার মধ্যকার বৈপরীত্য আরেকবার পুনরাবৃত্ত করে মানুষ ও পৃথিবী, আত্মা ও বুদ্ধিমত্তা কিংবা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যকার বৈপরীত্যকে।
ধ্যানের বিষয়বস্তু কি?
প্রকৃতিতে বহুবিদ বাস্তব উপকরণ সহজলভ্য যার যাহায্যে মানুষ পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে যে জিনিস অনুপস্থিত সেটি হল আত্মা (Self) বা ব্যক্তিত্ব যার মাধ্যমে মানুষের সাথে শাশ্বতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই আত্মা বা অহম বা ‘আমিত্ব’- এর মাধ্যমে মানুষ একই সাথে পৃথিবী ও পর জগতের বাসিন্দা হতে পারে। এরই মাধ্যমে সে পারমার্থিকতা ও অন্তর্গত স্বাধীনতার অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।
কাজেই ধ্যান হল আত্মসমুদ্রে অনবরত অবগাহন করা, নিজেকে নিজের মধ্যে স্থাপিত করা; ধ্যানের সাথে সামাজিক প্রশ্নমালার কোনো সম্পর্ক নেই।
ধ্যান বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড নয়। একজন বিজ্ঞানী নতুন মডেলের প্লেন তৈরি করতে গিয়ে ধ্যান করেন না; তিনি চিন্তা করেন, গবেষণা, অনুসন্ধান ও তুলনামূলক বিচার করেন। কিন্তু একজন সাধু, একজন কবি বা একজন শিল্পী ধ্যান করেন। তারা সত্যানুসন্ধান ও এক মহিমাময় রহস্যের উন্মোচনের পথে বিচরণ করেন। এই সত্যানুসন্ধ্যান সবকিছু, আবার কিছুই নয়; একটি আত্মার নিকট সবকিছু, বাদ বাকি পৃথিবীর নিকট কিছুই নয়।
কাজেই ধ্যান একটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড। এ্যারিস্টটলের নিকট যুক্তি ও অন্যুধ্যানের মধ্যে পার্থক্য মানবিক ও স্বর্গীয়-এর মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ।
বৌদ্ধ ধর্মে প্রার্থনার অর্থ ধ্যান। খৃষ্ট ধর্মের ‘Contemplative Order’ একই ব্যাপারে। স্পিনোজা অনুধ্যানকে নৈতিকতার চূড়ান্ত ফর্ম ও উদ্দেশ্যরূপে আখ্যায়িত করেছেন।
শিক্ষা মানুষকে অধিকতর ভালো, অধিকতর স্বাধীন বা অধিকতর মানবিক করে না। পরিবর্তে শিক্ষা মানুষকে অধিকতর দক্ষ, অধিকতর সমর্থ ও সমাজের জন্যে অধিকতর উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পশ্চাতপদ মানুষের চেয়ে শিক্ষিত মানুষেরা অকল্যাণকর কাজে বেশি পটু। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক অল্প শিক্ষিত ও অনগ্রসর মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়, অযৌক্তিক ও বশ্যতামূলক আগ্রাসনের ইতিহাস। শিক্ষার উচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী তৎপরতাকে মসৃণ করার জন্যেই সব রকমের সহায়তা করেছে।
গণসংস্কৃতি
সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয়। এখন প্রশ্ন হলঃ তথাকথিত গণসংস্কৃতি (mass culture) কি সংস্কৃতি নাকি সভ্যতারই একটি প্রকল্প বিশেষ?
যে কোনো সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ, ব্যক্তি বিশেষ, ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কিন্তু গণসংস্কৃতির বিষয় হল mass বা man-mass। একজন মানুষের আত্মা রয়েছে, কিন্তু একদঙ্গল জনতার চাহিদা ছাড়া কিছু নেই। সুতরাং সকল সংস্কৃতি মানুষেরই লালিত সন্তান, যেখানে গণসংস্কৃতি হল শুধু প্রয়োজন পূরণ বা চাহিদার যোগানদার। সংস্কৃতি ব্যক্তিসত্তা অভিমুখী, গণসংস্কৃতি পরিচালিত ঠিক বিপরীতক্রমেঃ সার্বিক সমরূপতা (uniformity) তথা নৈর্ব্যক্তিকরণের দিকে।
একটি সর্বব্যাপ্ত ভুল হল গণসংস্কৃতির (mass culture) সাথে লোকসংস্কৃতিকে (popular culture) এক করে দেখা। এটা লোকসংস্কৃতির জন্যে ক্ষতিকারক। কারণ তা গণসংস্কৃতির চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে স্বতন্ত্র, খাঁটি সক্রিয় ও জীবন্ত। এর মধ্যে কোনো চটকদারি নেই।
লোকসংস্কৃতি সৃজন ও অংশ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গণসংস্কৃতির মূল কথা হল নিপুণতার সাথে অন্যকে বশে আনা। নাচ, গান, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি একটি গ্রাম কিংবা উপজাতীয় জীবনের সাধারণ সম্পদ। এগুলো তারা পরিবেশন করে তারাই উপভোগ করে সকলে মিলে, অকৃত্রিম বন্ধন ও অনুভাবনা সহকারে। কিন্তু গণসংস্কৃতির উপভোগের ক্ষেত্রে মানুষ উৎপাদক ও ভোক্তা- এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ কি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালাকে প্রভাবিত করতে পারেন? তথাকথিত গণমাধ্যম-সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অন্যান্য সম্প্রচার মাধ্যম প্রকৃতপক্ষে গণবশীকরণেরই মাধ্যম। একদিকে গুটিকয়েক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদকীয় অফিস, অপরদিকে লক্ষ কোটি নিষ্ক্রিয় দর্শকশ্রোতা।
১৯৭১ সালে নেয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রায় সকল ইংরেজ সপ্তাহে ষোল থেকে আঠারো ঘন্টা ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। প্রতি তিনজন ফরাসির একজন কখনো বই পড়ে না; ফরাসি দেশের শতকরা ৮৭ ভাগেরও বেশি মানুষের সাংস্কৃতিক বিনোদনের প্রধান মাধ্যম টেলিভিশন। ব্যালে ও অপেরার স্থান অনুসন্ধান তালিকার একেবারে নীচে। ১৯৯৭ সালে জাপানে নেয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে একই চিত্র পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ ভাগ জাপানী কোনোরকম বই পড়ে না. তাদের প্রায় প্রত্যেকে প্রতিদিন ২.৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। সানফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Horkara দাবি করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গামী উঠতি প্রজন্মের জ্ঞান ধারণ ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ মান থেকে অনেক নীচে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, টেলিভিশন মানুষের সকল সমস্যার রেডিমেড সমাধান দিয়ে থাকে এবং অত্যন্ত সহজেই তা সাহিত্যের ও চিন্তনের স্থান দখল করে নিয়েছে; ফলত তা সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড অসম্ভব করে তুলেছে। আমরা দেখছি কিভাবে সরকারি আধিপত্যের মধ্যে রেডিও-টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমগুলো গণপ্রবঞ্ছনা করে যাচ্ছে। এখন আর মানুষকে শাসন করার জন্যে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এখন বৈধভাবেই মানুষের ইচ্ছাকে অবশ করে তাদের শাসন শোষণ ও ‘সত্য’র বটিকা সেবন করিয়ে তাদের স্বচিন্তা ও মতামত গঠনে প্রতিহত করা যাচ্ছে সহজেই এবং তা সম্ভব হচ্ছে এই গণ্যমাধ্যম দ্বারা।
গণমনস্তত্ত প্রমাণ করেছে যে, ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ১০ অবাস্তব কোনো মীথের ব্যাপারে মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব। গণমাধ্যম, বিশেষত টেলিভিশনকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তা মানুষের চৈতন্য ও আবেগ এবং অনুপ্রেরণাময় দিকটিকেই বশীভূত করেনি শুধু, বরং মানুষের মধ্যে এই অনুভূতিকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে, আরোপিত মতামতটি যেন তারই। ১১
সকল অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা তাদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে টেলিভিশনকে বেছে নিয়েছে। ফলত টেলিভিশন স্বাধীনতার শত্রু হবার পাশাপাশি পুলিশ, জেলখানা ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হয়েছে। অতীতে শাসকের দাপট হ্রাস করার জন্যে যদি সংবিধান প্রণীত হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে টেলিভিশনে ছদ্মবেশী ক্ষমতা নিবারণের জন্যেও নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
গণসংস্কৃতি মনের এমন একটি অবস্থা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যাকে Johan Huizinga বলেছেন ‘ছেলেমানুষি’। তিনি সমকালীন মানুষের আচরণে শিশুসুলভতা লক্ষ্য করছেন, যেমন হালকা বিনোদন ভক্তি, পরিপক্ক হিউমারের অভাব, গণশ্লোগান ও মিছিলের দিকে ঝোঁক, ঘৃণা কিংবা ভালোবাসা, প্রশংসা কিংবা নিন্দা প্রসঙ্গে অতি অভিব্যক্তি ইত্যাদি।
পরিশেষে আমরা যন্ত্রের প্রতি একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দৃকপাত করতে পারি। যন্ত্র ও প্রযুক্তির প্রতি সংস্কৃতির সহজাত ভীতি ও বিরাগ রয়েছে। Berdjajev বলছেন, “যন্ত্র সংস্কৃতির প্রথম পাপ।” এই ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আসছে এই কারণে যে, যন্ত্র প্রথম দিকে বিভিন্ন বস্তুর ওপর আধিপত্য করত আর এখন মানুষের ওপর আধিপত্য করতে শুরু করেছে। স্মরণ করুন ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ), টলস্টয়, হেইডেগার, নীজবাস্তনী, ফকনার প্রমুখের সতর্ক বাণী। অন্যদিকে মার্কসবাদী Henri Lefevre সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন: “স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জিত হবে শুধু সেই সমাজে যেখানে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সার্বিক স্ফুরণ ঘটবে এবং সেটা হল কমিউনিস্ট সমাজ”। আসলে যে সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউটোপিয়াকে আদর্শ মানে সে সমাজ যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু যন্ত্র মানুষকে ব্যবহার করে, তাকে নিরাপত্তা দেয় না; শিক্ষা ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তা একই কৌশলকেন্দ্রে সকলকে আনতে চায়, অতঃপর ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বকে ভোঁতা করে, তাঁর কর্ম, চিন্তা ও বক্তব্যকে পানসে করে তাকে একটি একক সমাজের (কর্তৃত্বের) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
মানবতাবিরোধী প্রগতি
আমেরিকার হাইড্রোজেন বোমার স্রষ্টা অপেনহেইমারের মতে প্রযুক্তি ও বস্তুগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে মানব জাতি গত চার শ’ বছরে যা করেছে, তার চেয়ে বেশি করেছে গত চল্লিশ বছরে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত মানুষে মানুষে মনোদূরত্ব বেড়েছে ১০২৬-১০৪০, তাপমাত্রা বেড়েছে ১০৫-১০১১, চাপ বেড়েছে ১০১০-১০১৬। আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে পুরনো পিস্টন ইঞ্জিনের পরিবর্তে আসবে পারমাণবিক শক্তিচালিত নৌকা। সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন রাস্তার নিচে শুয়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক যানবাহন চলাচল করবে।
জাঁ রসতান্দ বায়োলজির যাদুকরী সম্ভাবনার কথা কল্পনা করেছেন। তার মতে অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষ থেকে বিচ্ছিনকত বংশগত সারবস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে মানব জাতি নিজেকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞানীরা যদি কৃত্রিম ডিএনএ (DNA-ক্রোমোজমের মধ্যে পাওয়া বংশগত সারবস্তুর রাসায়নিক ভিত্তি) উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে নবতর সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। ইচ্ছেমত সন্তান পাওয়া সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, মানুষের মস্তিষ্কে যে দশ বিলিয়ন কোষ থাকে তার সাথে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত আরও কয়েক বিলিয়ন যোগ করে প্রতিভার ফুলঝুরি ঘটানো যাবে।
মৃতদেহ থেকে নেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন হবে একটি সাধারণ ঘটনা এবং মস্তিষ্কের অবসাদ ও ধ্বস (lag)-এর কারণ আবিষ্কৃত হলে জীবনকে দীর্ঘায়িত করার প্রাচীন মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কর্ম সময় কমিয়ে আনবে সপ্তায় ৩০ ঘন্টায়, কর্মবছর হ্রাস পাবে ৯ মাসে। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯ মিলিয়ন মটর, ৬০ মিলিয়ন টেলিভিশন সেট, ৭.৭ মিলিয়ন নৌকা ও ইয়ট ছিল। একই বছরে আমেরিকানরা শুধু ছুটি কাটনো বাবদ খচর করে ৩০ বিলিয়ন ডলার। সে দেশে ব্যক্তিগত ব্যবহার্যের দুই-তৃতীয়াংশ বিলাসদ্রব্য। এক হিসেব মতে ধনী দেশগুলো (মোট দেশের এক-তৃতীয়াংশ) বছরে শুধু কসমেটিকস-এ খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ সমস্ত দেশে জীবনযাত্রার মান ১৮০০ সালে যা ছিল তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত এখন। আগামী ৬০ বছরে আজ যা আছে তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত হবে। এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি, সে সময়ে কি প্রগতির পরাকাষ্ঠার পাশাপাশি মানব জীবন পাঁচ গুণ বেশি সুখি ও মানবিকতাপূর্ণ হবে? স্বতঃসিদ্ধরূপেই উত্তর আসবে না। পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সালে পাঁচ মিলিয়ন অপরাধকর্ম সংগঠিত হয়। সেখানে ভীতিকর অপরাধকর্ম বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে চৌদ্দ গুণ বেশি (অনুপাত ১৭৪:১৩)। একই দেশে প্রতি ১২ সেকেণ্ডে একটি অপরাধ, প্রতি ঘন্টায় একটি খুন, প্রতি ২৫ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি ৫ মিনিটে একটি ডাকাতি এবং প্রতি মিনিটে একটি করে গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটে। সে দেশে প্রতি এক লক্ষ জনে খুন হয় ১৯৫১ সালে ৩.১ জন, ১৯৬০ সালে ৫ জন, ১৯৬৭-তে ৯ জন। পশ্চিম জার্মানীতে ১৯৬৬ সালে ২ মিলিয়ন অপরাধ কর্মের খবর পাওয়া যায়। ১৯৭০-এ তা এসে দাঁড়ায় ২,৪১৩,০০০-এ। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্যতিক্রমহীনভাবে অপরাধ প্রবণতার উর্ধ্বগামী চিত্র সুস্পষ্ট।
বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত অপরাধ বিজ্ঞানীদের সপ্তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (১৯৭৩, সেপ্টেম্বর) সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করা হয় যে, বর্তমান সময় অপরাধের বিশ্বজনীন আগ্রাসন দ্বারা আক্রান্ত। মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানীরা হতাশভাবে বলেন: ‘আমাদের গ্রহ এক ‘স্খলনের সমুদ্র’ অর্থাৎ কম বেশি সকলেই অপরাধপ্রবণ এবং এখান থেকে মুক্তির কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। ‘বিশ্ব পরিস্থিতি ৭০’- জাতিসংঘের এই রিপোর্টে বলা হয় যে, একটি শিল্পোন্নত দেশে (নাম বলা হয়নি) কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ১ মিলিয়ন থেকে (১৯৫৫) দশ বছরে বেড়েছে ২.৪ মিলিয়ন (১৯৬৫)। জাতিসংঘ মহাসচিবের এক রিপোর্টে বলা হয়, “বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানব জীবন কখনোই এতটা নিরপত্তাহীনতায় ভোগেনি। বিভিন্ন প্রকৃতির
অপরাধ (ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ), চুরি, প্রতারণা, দুর্নীতি, ডাকাতি, আধুনিক জীবন ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করছে।”
রুশ মনস্তাত্ত্বিক হোজকভের গবেষণায় দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাদকাসক্তি তুমুলভাবে বেড়েছে, বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে। ১৯৪০ থেকে ১৯৬০-এ মাদক দ্রব্যের বিক্রয় দ্বিগুণ বেড়েছে: ১৯৬৫ সালে এসে তা বাড়ে ২.৮ গুণ বেশি, ১৯৭০-এ ৪.৩ গুণ এবং ১৯৭৩ সালে ৫.৫ গুণ। মাদক দ্রব্য সেবনজনিত মৃত্যুর হার বার্লিনে ১০০০০০ জনে ৪৪.৩ জন, ফ্রান্সে ৩৫ জন, অস্ট্রিয়ায় ৩০ জন। আমরা মাদকাসক্তিকে দারিদ্র ও পশ্চাদপদতার সাথে সম্পর্কিত ভাবতাম, সেক্ষেত্রে সমাধানের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু উন্নত দেশে মাদকাশক্তি কেন? প্রাচুর্যের সন্তানেরা কিসের থেকে পলায়ন করতে চায়? ইউরোপের অন্যতম ধনী দেশ সুইডেনে প্রতি দশজনে একজন মাতাল (নারী-পুরুষ)। মাদক দ্রব্যে সর্বোচ্চ হারে কর আরোপ করেও অবস্থা তথৈবচ। পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসনও সুস্পষ্ট। সকল ফরাসি প্রেক্ষাগৃহের অর্ধেক জুড়েই চলে পর্ণো ছায়াছবি। প্যারিসেই ২৫০টি সিনেমা হল শুধু পর্ণো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। সেই সাথে যোগ হয়েছে জুয়া। বৃহত্তম জুয়া নগরীগুলো সভ্যতম অঞ্চলে অবস্থিত দোভিলে, মন্টে কারলো, মাক্যাও, লাস ভেগাস। আটলান্টিক সিটির বিশাল নৃত্যশালার একটি ঘরে ৬০০০ জুয়াড়ীর ধারণ ক্ষমতা রয়েছে।
পরিসংখ্যান বলে যে, ১৯৬৫ সালে ফরাসিরা জুয়া খেলায় খরচ করে ১১৫ বিলিয়ন ফ্রাঁ,
মার্কিনীরা খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার।
সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে আত্মহত্যা ও মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ার সম্পর্ক কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? “মনস্তাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তার জীবনের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকর্ষের মধ্যে অতৃপ্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশি”- বলছেন একজন মার্কিন মনস্তাত্তিক। ক্লাসিক সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত উন্নততম সমাজের এই চিত্র প্রগতির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার জনে চারজন মানসিক হাসপাতালের বাসিন্দা, নিউইয়র্ক শহারে এই সংখ্যা হাজারে ৫.৫ জন। হলিউডে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানসিক চিকিৎসকের সমাগম। গণস্বাস্থ্য সার্ভিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক পাঁচজন মার্কিনীর একজনের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি।
১৯৬৮ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য বছরে যে সমস্ত দেশে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক তাদের তালিকায় প্রথম আটটি দেশ হল পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড। এ সমস্ত দেশে হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পরেই আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর স্থান (১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে)। একই সংস্থার ‘৭০ সালের রিপোর্টে এ ব্যাপারগুলোকে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পারিবারিক ভাঙনের সাথে যুগপৎ হিসেবে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন ও শিক্ষাকেও যুক্ত করা যায়। যুগোস্লাভিয়ার অতি উন্নত অঞ্চল
স্লোভেনিয়াতে (যেখানে সাক্ষরতার হার ৯৮%) প্রতি ১০০০০ জনে আত্মহত্যার সংখ্যা ২৫.৮ জন, কিন্তু অনুন্নত কসোভোতে (যেখানে সাক্ষরতার হার ৫৬%) মাত্র ৩.৪% ২০:১)। ড. এ্যান্থনি বেইলের গবেষণা মতে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা তাদের সমবয়স্ক অন্যদের তুলনায় ছয় গুণ বেশি। কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের বয়সী অন্যদের তুলনায় দশ গুণ বেশি। এটা উদ্বেগজনক কারণ, এখানে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীরা ধনাঢ্য পরিবার থেকে আগত, নয়ত সরকারী বৃত্তিধারী।
এটা ধরে নেয়া ভুল যে, উপরোক্ত চিত্রটি শুধু পশ্চিমা সভ্যতাতেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা মাত্রেই এর সংযোগ অনিবার্য। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইংল্যান্ড বা সুইডেন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, জাপান সম্পর্কেও তা-ই প্রযোজ্য। তবে জাপানের ক্ষেত্রে জাপানি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কাঠিন্য ও জাপানি পরিবারের ভূমিকা এ পরিস্থিতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে এসে বলা যেতে পারে যে, সভ্যতা ও স্বাচ্ছন্দ্য মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও বয়োলজি যে ‘বস্তু’ দিয়ে মানুষ সৃষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল মানুষতো তা দিয়ে সৃষ্ট নয়। মানুষ শুধু তার ইন্দ্রিয় সহযোগে বেঁচে থাকে না। “অবাস্তবায়িত আকাঙ্ক্ষা বেদনার জন্ম দেয়, বাস্তবায়িত আকাঙ্ক্ষা জন্ম দেয় তারল্যের”, বলছেন সোপেনহাওয়ার। প্রাচুর্য ও তার সাথে সংলগ্ন মানসিকতা যে কোনো মূল্যবোধক পদ্ধতির প্রতি ভক্তিকে হ্রাস, এমন কি নিশ্চিহ্ন করে দেয়।
সরল সহজ জীবন যাপনের প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা ধ্বংসের মাধ্যমেও সভ্যতার আগ্রাসী চেহারা বেরিয়ে আসছে। এখানে দ্বন্দ্বটি আসছে মানব জীবনের যান্ত্রিক ও জীবন্ত, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক নীতির মধ্যে। সভ্যতার আগ্রাসনের কারণেই ব্রাজিলে প্রতি বছর ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র আশি ভাগের বেশি পানি শিল্পবর্জ্য দ্বারা দূষিত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর কারখানার চিমনি ও মোটর গাড়ি থেকে নির্গত ২৩০ মিলিয়ন টন বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর উপাদান বাতাসে প্রবেশ করে। ফরাসি শক্তিকেন্দ্রগুলো ১৯৬০ সালে ১১৪ হাজার টন সালফার গ্যাস এবং ৮২ মিলিয়ন টন অঙ্গার উৎপাদন করে। অনেক প্রতিরোধক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। জার্মানীর রুর অঞ্চলের প্রতিটি শহরেই প্রতি বছর উৎপাদিত হয় ২৭০০০ টন বর্জ্য। ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের ফুসফুসে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে দশ গুণ বেড়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে গত কুড়ি বছরে পঞ্চাশ ভাগ। টোকিওর বিশাল ইয়ানাগা ক্রসওয়ে থেকে নেয়া অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় সেখান দিয়ে পার হওয়া ৪৯ জন যাত্রীর মধ্যে ১০ জন যাত্রীর রক্ত চলাচলের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৭ গুণ বেশি। প্রধান কারণ, যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস। শুধু তাই নয়, মোটর যান আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় যত মানুষ মারা গিয়েছে তা এই শতকের সমস্ত যুদ্ধজনিত মৃত্যুর সংখ্যাকেও হার মানায়।
সভ্যতার মধ্যে এমন কোনো ধনাত্মক শক্তি নেই সভ্যতার সকল আবিলতা ও অসামঞ্জস্য মোকাবেলা করতে পারে। আসলে সভ্যতার অসুখ সভ্যতার ভিতরকার কোনো ঔষধ দিয়ে চিকিৎসাযোগ্য নয়, একে সভ্যতার বাইরে থেকে চিকিৎসা করাতে হবে এবং এটা পারে একমাত্র সংস্কৃতি। কারণ সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান কখনো ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না কিংবা সভ্যতা পারে না ক্লাসিক্যাল কাঠামোতে ফিরে যেতে। The circle is closed.
মঞ্চে বিষাদবাদ
লাক্ষণিক অর্থে অমঙ্গলরোধের দর্শন আসছে শুধু বিশ্বের ধন্যাঢ্য ও উন্নত অঞ্চল থেকে। যেমন, ইবসেন, হেইডেগার, সেইলার, পিন্টার, বেকেট, ও’নীল, বার্জম্যান, কামু, আন্তনিনি প্রমুখ এরকম অঞ্চলের বাসিন্দা। বিজ্ঞানী, যারা বস্তুর বাহ্যিক চরিত্রে বিশ্লেষণ করেন, তারা সাধারণত আশাবাদী; কিন্তু চিন্তক ও শিল্পীরা, বিশেষত শিল্পীরা বড় বেশি দ্বিধাক্রান্ত।
কিন্তু সাদামাটাভাবে দেখলে একটি জাতির জীবনে বিমর্ষবাদ প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ সাক্ষরতা, সামাজিক নিরাপত্তা, মাথাপিছু আয় কয়েক হাজার ডলারে উন্নীত হবার পর। পরিহাস্য হলেও সত্য উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সবচেয়ে ভালো থাকলেও সেখানেই উৎপত্তি হয় চূড়ান্ত বিমর্ষবাদী দর্শনের। এ দর্শনে মানুষের ভাগ্য হতাশাপূর্ণ ও ট্র্যাজিক এবং সকল মানুষের চেষ্টা ও অস্তিত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অনর্থক বলে বিবেচিত। তাহলে কি বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য আধ্যাত্মিক নিরানন্দের জন্ম দেয়?
স্বাচ্ছন্দ্য বহির্নিষ্ঠ এবং অনর্থকতার বোধ জীবনের অন্তর্নিষ্ঠ অভিজ্ঞান-সভ্যতায়। দ্বান্দিকভাবে প্রকাশ করলে: যত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য, তত বেশি শূন্যতা ও নৈরাশ্যের অনুভূতি। বিপরীতভাবে আদিম সমাজগুলো দরিদ্র হতে পারে এবং সূক্ষ্ম সামাজিক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু তাদের জীবন জীবন্ত, সমৃদ্ধ ও বিচিত্র অনুভূতির ধারক। ফোকলোর প্রাচীন মানুষের জীবন যাপন ছন্দের অনন্য সাধারণ চিত্রটি উপহার দেয়। অসন্তোষ ও নৈরাশ্য তাদের দরিদ্র জীবনে অনুপস্থিত।
এই মঞ্চেই সভ্য পৃথিবী উন্মোচন করেছে তার মানবিক ‘ট্রাজেডি’। বিজ্ঞান কর্তৃক সভ্যতাকে উপহার দেয়া শৃংখলা ও নিশ্চয়তার মুকুটকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে থিয়েটার। বিজ্ঞান প্রদান করে থাকে উৎপাদন সামগ্রীর সমৃদ্ধ তালিকা, যান্ত্রিক শক্তির প্রদর্শন ইত্যাদি; আর শিল্প নির্দেশ করছে মানবিক গুণাবলীর পতনাবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস, পশুত্ব ও শূন্যতা। বস্তুগত সমৃদ্ধির মধ্যে থেকে থিয়েটার আবিষ্কার করছে আক্রমণাত্মক, অসহায় ও অপরাধপ্রবণ মানুষকে। এ্যাবসার্ড নাটকগুলো আজকের সবচেয়ে উন্নত সমাজের মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি।
কবিরা যদি মনুষ্য জাতির সংবেদী নিরীক্ষক হন তাহলে তাদের ভীতি ও সংশয় দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবী মানবতার দিকে এগুচ্ছে না, এগুচ্ছে উন্মুক্ত বিমানবিকীকরণ ও বিচ্ছন্নতার দিকে।
১৯৬৮ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা ১৯৭১ সালে আত্মহত্যা করেন। এর দু’বছর আগে ১৯৬৯ সালে আরেকজন জাপানি ঔপন্যাসিক তুকিয়ো মিশিমা একই ভাবে জীবনাবসান ঘটান। ১৯৮৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অন্তত তের জন জাপানি ঔপন্যাসিক ও লেখক আত্মহত্যা করেছেন। জাপানি সংস্কৃতির এই ‘অবিরাম ট্রাজেডি’ হল জাপানের প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃতিতে পশ্চিমা সভ্যতা ও বস্তুবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশের পরোক্ষ ফল। মৃত্যুর এক বছর আগে কাওয়াবাতা লেখেন, “মানুষ এক কংক্রিটের দেয়াল দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, যে দেয়াল ভালোবাসার সকল সঞ্চালনকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রগতির নামে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে প্রকৃতির।” ‘তুষার রাজ্য’ নামক উপন্যাসে কাওয়াবাতা মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গ চেতনাকে কেন্দ্রীয় আলোকে তুলে ধরেছেন।
সকল মহৎ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি একইভাবে সভ্যতায় মানুষের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের চিত্র খুঁজে পেয়েছেন। আঁন্দ্রে মার্লো উনবিংশ শতকীয় আশাবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন: “ইউরোপ ধ্বংসাক্রান্ত এবং রক্ত দ্বারা কলঙ্কিত মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিল, ইউরোপ তা করেছেও।” একই চিত্র দেখিয়েছেন পল ভেলরী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর।
নাস্তিবাদ বলছে’ পরিপ্রেক্ষিতহীন পৃথিবীর কথা, বলছে ‘ভীষণ নৈঃশব্দে’র কথা, বলছে ‘ভগ্ন ও ছিন্নভিন্ন ব্যক্তিত্বের’ কথা-কিন্তু নাস্তিবাদ কোনোক্রেমেই কোনো বিষাক্ত দর্শন নয়, যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন। বস্তুত এই দর্শন অত্যন্ত গভীর ও শিক্ষাপ্রদ। এটা সেই পৃথিবীর বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও অসমর্থনের প্রকাশ যে পৃথিবী তার (মানুষ) মৌলিক ভাবমর্যাদাকে আক্রান্ত করেছে। এটা সভ্যতার এক রৈখিক বিশ্ববিস্তারের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ। একই কারণে কেউ কেউ আধুনিক নাস্তিবাদকে এক ধরনের ধর্মরূপে দেখেছেন এবং ধারণাটি ভিত্তিহীন নয়।
আদিম উদ্বিগ্নতা, কবরপাড়ের চিত্রকল্প, এ পৃথিবী থেকে, যেখানে যে আগন্তুক মাত্র, মুক্তি লাভের পথ অনুসন্ধানের বেপরোয়া প্রচেষ্টা-এ সবকিছুই ধর্ম ও নাস্তিবাদে উপস্থিত। পার্থক্য শুধু এই যে, এ প্রচেষ্টায় নাস্তিবাদ কোনো পথ খুঁজে পায়নি, কিন্তু ধর্মে এ পথের সন্ধান মিলে গেছে।
বিজ্ঞান, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে মানবিক সুখ সমস্যার সমাধানে সভ্যতার নিদারুণ ব্যর্থতাকে যখন মানুষ উপলব্ধি ও স্বীকার করবে তখনই মনুষ্য জাতির ওপর সবচেয়ে কঠিন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবটি আসবে। তখন সময় হবে ইতোপূর্বে গৃহীত কতক চিন্তাধারার পুনর্বিবেচনার। প্রথম পুনর্বিবেচনার বিষয় হবে মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক ভুল ধারণা। কারণ সভ্যতা যদি মানুষের সুখ-শান্তি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে ধর্মীয় ধারণাটিই সত্য এবং বৈজ্ঞানিক ধারণাটি মিথ্যে। তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই।
নাস্তিবাদ
ধর্ম ও আধুনিক নাস্তিবাদের মধ্যে কিছু সাধারণ সাদৃশ্য থাকায় নাস্তিবাদকে সভ্যতার অন্তর্গত একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
নাস্তিবাদ স্রষ্টার অস্বীকৃতি নয়, বরং তার আপাত অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা যেমনটি বেকেট বলছেন, মানুষের অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে তথা এই সত্যের প্রতিবাদ যে মানুষের ধারণাটি অবাস্তবায়নযোগ্য ও অসম্ভাব্য এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে ধর্মীয় ভাবনাকে নির্দেশ করে, বৈজ্ঞানিকতা নয়। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষ সম্ভবপর ও বাস্তবায়নযোগ্য। কিন্তু চূড়ান্তরূপে গণ্য তা-ই অমানবিক এবং সাত্রের বিখ্যাত উক্তি “man is futile passion” শুনতেও যেমন, অন্তর্নিষ্ঠ অর্থেও তেমনি-ধর্মীয়। যেহেতু বস্তুবাদে আবেগ নেই, সেহেতু নিরর্থকতার বোধও নেই।
সংসারের উচ্চতর উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে বস্তুবাদ অনর্থকতা ও তুচ্ছতার বোধকে ধারণ করার ঝুঁকি থেকে মুক্ত। বস্তুবাদী পৃথিবী ও মানুষের একটি প্রায়োগিক লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু “man is futile passion” এই বক্তব্য নির্দেশ করে যে মানুষ ও পৃথিবী অভিন্ন নয়। পৃথিবীর প্রতি এই রকমের আমূল বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সকল ধর্মের সূত্রপাত। সাত্রের অনর্থকতার বোধ এবং কামুর এ্যাবসার্ড একই উদ্দেশ্যও বোধবেদন্ধ্যের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি ধর্মীয় চরিত্রের, কারণ তা জীবন যাপনের বৈশ্বিক উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করে।
স্রষ্টার অনুসন্ধান এক ধরনের ধর্ম। কিন্তু অনুসন্ধানে খোদা মেলে না। নাস্তিবাদী দর্শনে যে উদ্বিগ্নতার প্রকাশ তা সর্বতোভাবেই, শুধু উপসংহার ব্যতীত, ধর্মানুসারী। নাস্তিবাদী ও ধর্ম উভয় মতেই মানুষ এই পৃথিবীতে আগন্তুক মাত্র, কিন্তু নাস্তিবাদের আগন্তুক হতাশায় হারিয়ে যাবার গল্প শোনায়, আর ধর্মের আগন্তুক উচ্চারণ করে মুক্তির পয়গাম।
আলবেয়ার কামুর বক্তব্যকে বোঝা যেতে পারে শুধু একজন হতাশ বিশ্বাসীর চিন্তা-ভাবনা হিসেবেঃ “যে পৃথিবী থেকে হঠাৎ করে আলোর ঝলকানি তিরোহিত হয় সে পৃথিবীতে মানুষ নিজেকে আগন্তুক ভাবে, তার কাছে এটা মুক্তি সম্ভাবনাহীন নির্বাসন; যেহেতু হারানো মাতৃভূমির কোনো স্মৃতি কিংবা প্রতিশ্রুত রাজ্যে পৌঁছানোর কোনো বন্দোবস্তও তার কাছে নেই।” অথবা “আমি যদি গাছগুলোর মধ্যে একটি গাছ হতাম তাহলে জীবনের একটি বোধ থাকত কিংবা এই বোধের সমস্যা-ই-উদ্ভূত হত না। কারণ তাহলে আমি এই পৃথিবীরই একটি অংশ হতাম যে পৃথিবীকে এ মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে প্রতিরোধ করি।” অথবা ‘all is allowed since God doesn’t exist and man dies”. এই শেষের বাক্যটিতে বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদদের ঠুনকো নাস্তিকতার কোনো সমর্থন নেই, বরঞ্চ এটা হল সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়া এক আত্মার আহাজারী। এটা হল ‘ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত নাস্তিকতা।’
নৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে অস্তিত্ববাদও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। Simone de Bouviore লিখছেন, “শুরুতে মানুষ কিছুই নয়; ভালো বা মন্দ হওয়াটা নির্ভর করছে তারই ওপর, অন্য কথায় তার স্বাধীনতা গ্রহণ বা বর্জনের ওপর। নির্বাচিত স্বাধীনতা তার লক্ষ্যকে চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং কোনো বাহ্যিক শক্তি, এমন কি মৃত্যু এই স্বাধীনতার অনুদানকে ধ্বংস করতে পারে না। যদি এই খেলায় হেরে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলেও প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রতিটি মূহূর্তে ঝুঁকি নেয়া এবং সংগ্রাম করে যাওয়া।” এমন কি সাত্রের অস্তিত্বের দ্বৈততা, ‘অস্তিত্বের দ্বারা অস্তিত্ব’ (etre et soi) এবং ‘অস্তিত্বের জন্যে অস্তিত্ব’ (etre pour soi)- এটাও বস্তুবাদের পরিষ্কার অস্বীকৃতি। শুধু প্রতিশব্দগুলো নতুন, সারসত্যটি পুরনো ও সহজে সনাক্তযোগ্য।
টীকা
১. সংস্কৃতির ইংরেজি culture শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে cult’ (ল্যাটিন cultus) শব্দটির সাথে সম্পর্কিত। দুটো শব্দেরই উৎপত্তি ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ ‘কুল’ (Kwel) থেকে। অপরদিকে সভ্যতা বা Civilization সম্পর্কিত ‘Civis’ শব্দটির সাথে যার অর্থ নাগরিক।
२. Chosism-এর উৎপত্তি ফরাসি শব্দ ‘chose’ থেকে যার অর্থ বস্তু বা thing: শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ডুরখেইম, কোনো কিছুকে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরীক্ষা করার প্রেক্ষিতে।
৩. Malreaux: Antimemoirs. Serbocroatian translation, Zagreb. 1969 P. 276.
8. New York Times-এ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এই প্রস্তাবনাকে বলা হয়েছে ‘নবযুগের প্রথম সূচক’।
৫. Marshall McLuhan প্রমাণ করেছেন যে, লেখনী চিন্তন প্রক্রিয়ায় বিচিত্র পরিবর্তন আনে। তিনি বলেন, “The use of an alphabet produces and supports the habit of expressing in visual and space terms, especially in terms of uniform space and uniform time, continually and constantly.” M. McLuhan: The Gutenberg Galaxy, Serbocroatian translation Belgrade, 1973, P. 32.
৬. Oswald Spengler: The Decline of the West. Allen and Unwin Ltd. 1971. P. 32.
৭. একটি মজার দৃষ্টান্ত এই যে, রেনেসাঁর যুগেও মানব মন বিচিত্র কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল এবং তা শুধু সাধারণ মানুষ নয়, শিল্পী ও মানবতাবাদীদেরকেও আক্রান্ত করে। যেমন, “জ্যোতিষতত্ত্বকে বিশেষভাবে স্বাগত জানান উদারপন্থী চিন্তকরা এবং তা প্রাচীনকালের চেয়েও এ সময়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।” জানাচ্ছেন বার্ট্রান্ড রাসেল।
৮. Xenephon. Symposium, P. 220.
৯. এই প্রতিশব্দটি সাহিত্যে প্রথম চালু করেন Ortega Y. Gasset; এই ‘mass’ হল ব্যক্তিত্ব হারানো কতক বেনামী, নিরবয়ব মানব ইউনিটের সমষ্টি।
১০. ১৯৪৫ সাল পর্যন্তও জাপানিদেরকে শিক্ষা দেয়া হত যে, মিকাডো হল সূর্যদেবীর সন্তান এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে জাপানকে সৃষ্টি করা হয়। এমন কি এই ধারণা শিক্ষা দেয়া হত বিশ্ববিদ্যালয়েও। পরবর্তীতে আমরা দেখি নতুনতর মীথ। রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়ায় এই মীথ গড়ে ওঠে। স্টালিন, মাও সেতুং ও কিম সুং-কে ঘিরে গড়ে ওঠে এক ধরনের ‘Leader Cult’.
১১. এ ব্যাপারে চমৎকার আলোকপাত করা হয়েছে Djura Susnjic লিখিত ‘Fisherman For Human Souls’ বইয়ে। #
[লেখাটি আলিয়া আলি ইজেতবেগডিচ-এর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ Islam Between East and West থেকে সংকলিত। গ্রন্থটি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলাম শিরোনাম দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ইফতেখার ইকবাল।]